ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও
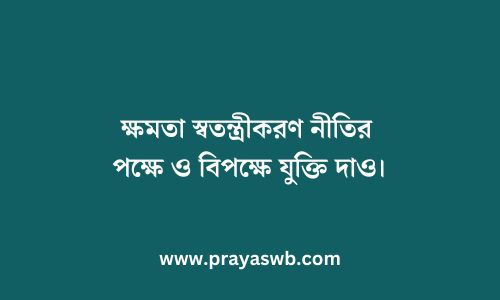
ভূমিকা
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম প্রবক্তা হলেন-মন্তেস্কু। তাঁর মতে, একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে না। তাই সরকারের তিন শ্রেণির ক্ষমতা তিনটি পৃথক বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি
মন্তেস্কু প্রদত্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে যুক্তি
(i) বিভাগীয় স্বাধীনতা: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সরকারের প্রতিটি বিভাগের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। কোনো বিভাগ অপর কোনো বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে না।
(ii) দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগের ফলে সরকারের প্রত্যেক বিভাগ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। প্রত্যেক বিভাগের কাজ সম্বন্ধে নাগরিকরা সচেতন থাকে বলেই বিভাগীয় দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়।
(iii) স্বৈরাচারিতা রোধ: এই নীতি প্রয়োগের ফলে কোনো বিভাগের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে না। ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কোনো বিভাগই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।
(iv) ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা: মস্তেস্কু এর মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে উপযোগী। এই কারণেই রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন কাজ পৃথকভাবে বিভিন্ন বিভাগের উপর অর্পণ করা উচিত।
(v) কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি: এই নীতিটি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা ও কাজকর্মের পৃথক্করণ করা হয়, যা বিভাগগুলিকে স্বাধীনভাবে কার্যসম্পাদনের সুযোগ প্রদান করে। তার ফলে সরকারি বিভাগগুলিতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
(vi) উৎকর্ষতা বৃদ্ধি: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সরকারের তিনটি বিভাগের গুণগত মানোন্নয়ন করা সম্ভব। এই নীতি প্রযুক্ত হলে ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত বিভাগে নিযুক্ত করা যায় ফলে সরকারি কার্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।
(vii) গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। এই নীতির ফলে গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করা যায়, ফলে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই এই নীতি মেনে চলে।
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিপক্ষে যুক্তি
(i) বাস্তব প্রয়োগ অসম্ভব: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়, কারণ পারস্পরিক সহযোগিতাই হল গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি। এখনও কোনো-না-কোনোভাবে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা অন্য বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
(ii) স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নয়: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকরী হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত হয়। তাই এই নীতিটি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে না।
(iii) দায়িত্বহীনতা: প্রতিটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করলে নিজেদের দায় অপর বিভাগের উপর চাপানোর চেষ্টা করতে পারে, তাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
(iv) জনকল্যাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি: আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারকে জনকল্যাণমুখী কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়, তাই নীতিটি প্রযুক্ত হলে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে জনস্বার্থ জড়িত কল্যাণমূলক কাজ ব্যাহত হয়।
(v) জৈব মতবাদীদের বক্তব্য: বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্টন্সি-র মতে, সরকার হল জীবদেহের মতো। দেহ থেকে মস্তিষ্ককে পৃথক করলে জীবদেহের মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তেমনি সরকারে প্রধান বিভাগগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সরকারের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।
(vi) অসমীচীন: অনেকে মনে করেন, সরকারি কাজকর্মের দক্ষতা ও সফলতা অর্জনের কারণেও পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সমীচীন নয়। কারণ সরকারের দক্ষতা ও সাফল্য প্রধান তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে তিনটি বিভাগ যদি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে তাহলে সরকারের কাজকর্ম কখনোই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।
মূল্যায়ন
পরিশেষে বলা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি থাকা সত্ত্বেও এই নীতির গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।
আরও পড়ুন – জাতি ও জাতীয়তাবাদ প্রশ্ন উত্তর