প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলনে প্রবল গতিবেগ দেখা দেয় এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রামমুখী চরিত্র ধারণ করে। এর পশ্চাতে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল।
তো চলুন আজকের মূল বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন পড়ে নেওয়া যাক।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন
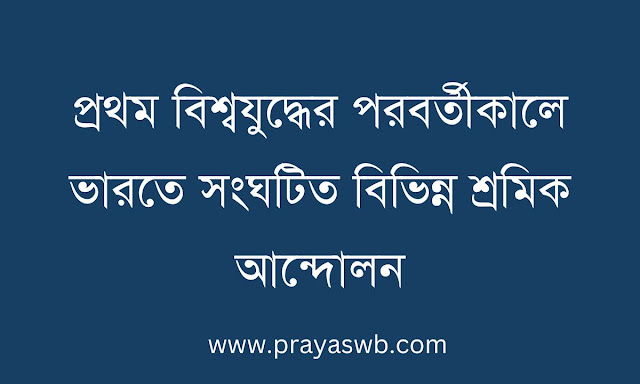 |
| প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন |
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলনে প্রবল গতিবেগ দেখা দেয় এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রামমুখী চরিত্র ধারণ করে। এর পশ্চাতে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল–
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও হোমরুল আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। ভারতীয় শ্রমিকরা মনে করতে থাকে যে, বুশ শ্রমিকরা যদি জার সরকারের পতন ঘটাতে পারে, তাহলে তারাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাতে পারবে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং এই কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকার ভারতীয় শিল্পপতিদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হন। এর ফলে ভারতীয় শিল্পপতিরা এতদিন তাঁদের অনধিগম্য বহু ক্ষেত্রে মূলধন লগ্নি করতে শুরু করেন। তাঁদের উদ্যোগে ভারতে বস্ত্র, চট, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, রসায়ন শিল্প, সিমেন্ট প্রভৃতির বহু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধান্তে মন্দার ফলে কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হলে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।
- এ ছাড়া, শ্রমিকদের নানা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অভাবনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বসবাস করতে হত। তাদের মজুরি ছিল অতি সামান্য এবং তাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ছিল না। এই সব কারণে যুদ্ধের পর শ্রমিকশ্রেণি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।
শ্রমিক ধর্মঘট (১৯১৭ খ্রিঃ)
১৯১৪ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ছোটো ছোটো কিছু ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণিকে ধর্মঘট থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়। কলকারখানা, রেল, ডক, ডাক, বস্ত্রশিল্প, চা-শিল্প, পাটশিল্প-সর্বত্র ব্যাপক ধর্মঘট চলতে থাকে এবং বহুক্ষেত্রে শ্রমিকরাই জয়যুক্ত হয়। এইসব ধর্মঘটে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, বি. পি. ওয়াদিয়া, বাংলার হেমন্ত সরকার, জে. এল. ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃত্ব দেন।
শ্রমিক সংগঠন, (১৯১৮-৪৬ খ্রিঃ)
১৯১৮ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা ভারতে অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের প্রায় ৭৫টি কারখানার প্রতিনিধিরা এতে যোগদান করে। এই বছরেই বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে।
শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কংগ্রেস তার প্রাদেশিক কমিটি ও অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলিকে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে সহায়তা করার নির্দেশ দেয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ অধিকার অর্জনের জন্য শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠন গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকলেও জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু কখনই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয় নি। চিত্তরঞ্জন দাশ ও লালা লাজপৎ রায় শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও, গান্ধীজি রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন।
শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি
ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের চারটি পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়।
- ওয়াদিয়া, ব্যাপ্তিস্তা, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ প্রমুখ শ্রমিকশ্রেণির দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তাদের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হন।
- নারায়ণ মালহর যোশী (এন. এম. যোশী) প্রমুখ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ আইন-সম্মতভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার বিরোধী ছিলেন।
- চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায়, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন।
- গান্ধীজি এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা করবে এবং রাজনীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।
‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’
সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ বা ‘All India Trade Union Congress’ (A.I.T.U.C.)। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বি. পি. ওয়াদিয়া, তিলক, যোসেফ, ব্যাপ্তিস্তা, লাজপৎ রায়, এন. এম. যোশী, দেওয়ান চমনলাল প্রমুখ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত এই সংগঠনের উদ্বোধনী সম্মেলনে লালা লাজপৎ রায় সভাপতিত্ব করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ৫ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসেবে ৮০৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করে। এ ছাড়া মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, ওয়াদিয়া, শ্রীমতী বেশান্ত, এন্ড্রুজ, সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী, নরিম্যান, ব্যাপ্তিস্তা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে লালা লাজপৎ রায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানান, ভারতীয় শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার কথা বলেন এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরামর্শ দেন- কিন্তু তিনি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা বলেননি। জাতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু এই সংগঠনকে স্বীকৃতি দেয়নি।
অসহযোগ আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণি
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নানা কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণিও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, গান্ধীজির গ্রেপ্তার, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন, প্রিন্স অফ ওয়েলস্-এর ভারতে আগমন প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, রেল, কয়লাখনি ও চা-বাগিচার শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে • ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়। ১৯১৯ সালের রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ভারতের শ্রমিক শ্রেণি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ১৯২১ সালে ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে যুবরাজ বোম্বাই-এ পৌঁছলে বোম্বাই শহরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সুতিকল শ্রমিক ধর্মঘটে নামে। আমেদাবাদ ও গুজরাটের বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয় এবং তা হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। আসামের চা বাগানের প্রায় ১২ হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক চা বাগান ত্যাগ করে বাসভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে চাঁদপুরের স্টিমার ঘাটে গোর্খা সেনা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ে এবং পদ্মার সব স্টিমার ঘাটে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। কলকাতার পাটকল, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প এবং রানিগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনি-সর্বত্র ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। কয়লাখনি অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী দর্শনানন্দ।
শ্রমিক সংগঠনে বামপন্থী প্রভাব
ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ (Communist Party of India) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬-২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে ‘শ্রমিক ও কৃষক পার্টি’ (‘Workers’ and Peasants’ Party’) প্রতিষ্ঠা করে তারা সক্রিয়ভাবে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, শ্রমিকদের সংগঠিত করা, জমিদারি প্রথা বিলোপ প্রভৃতি। এই দলের প্রধান সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মুজাফ্ফর আহমদ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, পি. সি. যোশী প্রমুখ বামপন্থী। কলকাতায় অবশ্য এই দলের নাম হয় ‘পেজ্যান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি’। মুজাফ্ফর আহমদ, কবি নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার এতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই সব বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলের মুখপত্র হিসেবে বাংলায় মুজাফ্ফর আহমদ সম্পাদিত ‘গণবাণী’ (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ), সন্তোষকুমারী গুপ্তা সম্পাদিত ‘শ্রমিক’, বোম্বাইয়ের ‘ক্রান্তি’ ও এস এ ডাঙ্গে সম্পাদিত ‘সোসালিস্ট’ (১৯২৪ খ্রিঃ), মাদ্রাজের সিঙ্গারাভেল্লু চেট্টিয়ার সম্পাদিত ‘লেবার-কিষাণ গেজেট’ এবং পাঞ্জাবের ‘কীর্তি’, ‘মেহনতাকাশ’ (মেহনতি মানুষ) ও ‘মজদুর-কিষাণ’ উল্লেখযোগ্য।
ধর্মঘট
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। এ সময় ধর্মঘটগুলি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র আকার ধারণ করে, যার সঙ্গে অতীতের ধর্মঘটগুলির কোনো তুলনাই চলে না। এই সব ধর্মঘটগুলিতে নবজাত কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।
- ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে খড়্গপুরের বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ২৫ হাজার শ্রমিক পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচার সত্ত্বেও ২৬ দিন ধরে ধর্মঘট চালায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লিলুয়ার ইস্ট ইন্ডিয়ান এবং সাউথ ইন্ডিয়ান রেলে ধর্মঘট হয়। এ সময় ধর্মঘটীদের ওপর গুলি চলে এবং এর ফলে পাঁচজন শ্রমিক প্রাণ হারায়।
- ১৯২৮ এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পর পর দুটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে দেড় লক্ষ শ্রমিকের ছয় মাসব্যাপী (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর) ধর্মঘট চলে এবং এই সময় বস্ত্রকল শ্রমিকদের জঙ্গি সংগঠন ‘গিরনি কামগার ইউনিয়ন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮-এ প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩২৪, কিন্তু এই বছরের শেষে এর সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয় ৫৪,০০০। ডাঙ্গে, মিরাজকর, যোগলেকর প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে, বাংলার চেঙ্গাইলে লাডকো জুট মিল এবং তারপর বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লাস্টার চটকল-এ ছয় মাস ধর্মঘট চলে। বঙ্কিম মুখার্জী, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘটগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ৬০ হাজার শ্রমিক-ছাঁটাই ও কাজের সময় বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ২ লক্ষ শ্রমিক পুলিশের অত্যাচার সত্ত্বেও ৩৭ দিন ধরে আন্দোলন চালায়। এই ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল ‘বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’, যার সভানেত্রী ছিলেন ড. প্রভাবতী দাশগুপ্তা। এছাড়া, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল মোমিন, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, কালী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলন শ্রমিকদের সংগঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখায়।
‘সাইমন কমিশন’ বিরোধী অভিযান
‘সাইমন কমিশন’ বিরোধী আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের উদ্যোগে শ্রমিকশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন বোম্বাই বন্দরে উপনীত হলে শ্রমিকশ্রেণি ধর্মঘট করে এবং ৩০ হাজার শ্রমিকের মিছিল বের করে। তাদের মুখে ধ্বনি ছিল- ‘ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক’।
‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজ্যান্টস পার্টি’
১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজ্যান্টস পার্টি’-গুলির সারা ভারত সম্মেলন ডাকা হয় এবং এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাদেশিক দলগুলিকে নিয়ে সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক দল গঠনের চেষ্টা হয়। এই সম্মেলনে শ্রেণি-সংগ্রাম, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি বিলোপ, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দান, বাক্-স্বাধীনতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সময় কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ত্রিশ হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মিছিল জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চের কাছে উপস্থিত হয়ে ‘পূর্ণ স্বাধীনতার’ দাবি জানিয়ে আসে। মূল কথা, এ সময় কমিউনিস্টদের উদ্যোগে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী রূপ ধারণ করে।
আপনি আমাদের একজন মূল্যবান পাঠক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন -এই বিষয়ে আমাদের লেখনী সম্পূর্ণ পড়ার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না।