মনসবদারি প্রথার দোষ-ত্রুটি বা কুফলগুলি উল্লেখ করো
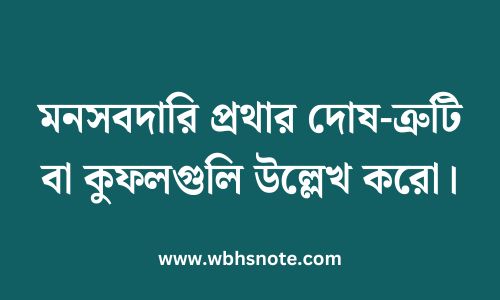
ভূমিকা
আকবর প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা যে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ভিত্তি ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাকে মজবুত করেছিল, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রথা একেবারে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ছিল না। সেগুলি হল-
(1) প্রথাগত ত্রুটি: প্রথম থেকেই এই মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু প্রথাগত ত্রুটি ছিল। এই প্রথায় মনসবদারদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক ও অসামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে দু-ধরনের দয়িত্ব পালন করার মতো যোগ্যতা সবার ছিল না।
(2) সৈন্যপোষণে কারচুপি : মনসবদারদের অধিকাংশই ছিলেন অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁদের বেশিরভাগ যে সংখ্যক সৈন্য বা অশ্ব রাখার কথা, তা রাখতেন না। অনেক সময় ভিখারি, ভবঘুরে লোকেদের সৈন্যবাহিনীর সদস্য সাজিয়ে সম্রাটের চোখে ধূলো দেওয়ার চেষ্টাও করতেন। আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন, আকবর মনসবদারদের এই কারচুপি রোধে ‘দাগ’ ও ‘চেহরা’ প্রথা চালু করেও এই দুর্নীতি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে পারেননি।
(3) সৈন্যদের আনুগত্য : সেনাদের সঙ্গে মোগল সম্রাটের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল মনসবদারদের সঙ্গে। কারণ তাদের নিয়োগ, বেতন, পদোন্নতি, পদচ্যুতি সব কিছুই নির্ভর করত মনসবদারদের ইচ্ছার ওপর। স্বভাবতই সম্রাটের প্রতি নয়, মনসবদারদের প্রতিই তাদের আনুগত্য ছিল।
(4) ভূমিরাজস্ব হ্রাস: সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনসবদারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাই তাঁদের বেতন মেটানোর জন্য সম্রাটরা বহু খালিসা জমি (রাজার খাস জমি)-কে জায়গির জমিতে পরিণত করতে বাধ্য হন। ফলে মোগল কোশাগারে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।
(5) সম্রাটদের আপসমূলক নীতি: মোগলবিরোধী কোনো জাতি বা গোষ্ঠী শক্তিশালী বা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সম্রাটরা তাঁদের উচ্চ মনসব দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁদের এই আপসমূলক নীতি সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল।
মূল্যায়ন
সবশেষে বলা যায় যে, মনসবদারি প্রথার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল অনেকটাই সম্রাটদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর। কিন্তু আকবর পরবর্তী সম্রাটদের আমলে এই প্রথার মধ্যে নানা জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মনসবদাররা মোগল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে ওঠে। ভালো জায়গির লাভের আশায় তাঁরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দেয়।
আরও পড়ুন – নুন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর