বিজ্ঞান বিপ্লব কী সত্যিই ‘বৈপ্লবিক’ ছিল
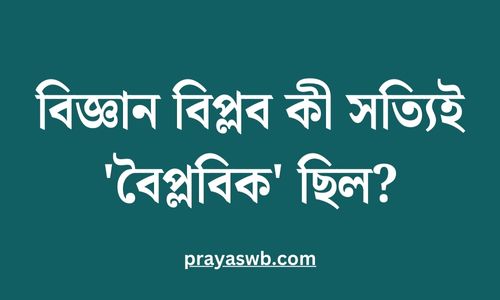
ভূমিকা
রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রভাবে ইউরোপে সাহিত্য-শিল্পের পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এই কালপর্বে ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যথা- জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, পদার্থ ও জীববিদ্যা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছিল, তা সাধারণভাবে বিজ্ঞান বিপ্লব নামে পরিচিত।
(1) বিজ্ঞান বিপ্লবের ক্ষেত্র: ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নব্যবিজ্ঞান চর্চা চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। এসময় মহাকাশ চর্চা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার প্রমুখরা যেমন মহাকাশ চর্চার ক্ষেত্রে এক নবপথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তেমনি ভেসেলিয়াস, ইউলিয়াম হার্ভে, লিউয়েন হুক, রবার্ট হুক প্রমুখরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকেও আলোকিত করেছিলেন।
(2) বিতর্ক: ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানচেতনার ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায় কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিভিন্ন মত বর্তমান। কারও মতে, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকালীন চর্চা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু একে ‘বিপ্লব’ বলা যায় না।
(3) পক্ষে যুক্তি: হারবার্ট বাটারফিল্ড (Herbert Butterfield) প্রথম বিজ্ঞান জগতের এই পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়া সিলভাইন বেইলি (Sylvain Bailly) সহ আধুনিক কালের অনেক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত এই মতের সমর্থক যে বিজ্ঞান বিপ্লব একটি আকস্মিক অভিনব ঘটনা। এটি পুরানো ‘গ্রিক-অ্যারিস্টট্লীয়-চার্চ’ কেন্দ্রিক বিশ্বচরাচরের মডেলকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আধুনিক পৃথিবীর দিকে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের মতে, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখারই যে উন্নতি ঘটেছিল, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। তাঁরা আরও মনে করেন, চিন্তার জগতের এই বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল বিজ্ঞানের হাতে। এখানে ধর্মীয় দর্শনের ভূমিকা বিন্দুমাত্র ছিল না।
(4) বিপক্ষে যুক্তি: সাম্প্রতিক কালে স্টিফেন শ্যাপিন, টমাস কুন প্রমুখ ঐতিহাসিক বিজ্ঞান বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বিজ্ঞান বিপ্লব আদৌ একটি ‘বিপ্লব’ নয় বা আকস্মিক যুগান্তর নয়; এটি একটি দীর্ঘকালীন চর্চার ধারাবাহিকতার ফসলমাত্র। তাই একে বিপ্লব না বলে অগ্রগতি বলাই যুক্তিযুক্ত। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে জ্ঞানচর্চার ধারার সূত্রপাত হয়েছিল, তারই দীর্ঘ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে নতুন মতবাদ কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে উঠে এসেছিল। এ ছাড়া বিজ্ঞান বিপ্লবের সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে খ্রিস্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ স্থির করা ছিল কোপারনিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। টলেমীয় পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের পরিবর্তে ‘সূর্যকেন্দ্রিক’ মহাবিশ্বের মডেল আবিষ্কার করেও তিনি নিজে তা প্রচার করেননি। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ‘De Revolutionibus’ প্রকাশ করেন যা উৎসর্গ করেন পোপ তৃতীয় পলকে।
মূল্যায়ন
পরিশেষে বলা যায় যে, তথাকথিত ‘বিজ্ঞান বিপ্লব’ মানবসভ্যতার প্রতিটি দিককেই আলোকিত করেছিল। এ যুগের সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা মধ্যযুগীয় পৃথিবীকেন্দ্রিক ধ্যানধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছিল বলা যায়। সর্বোপরি, বিজ্ঞান বিপ্লব সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তাভাবনা ও বিজ্ঞানচেতনার সঞ্চার করেছিল।
আরও পড়ুন – নুন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর