প্রার্থনা কবিতার প্রশ্ন উত্তর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার বাংলা | prarthona kobitar long question answer | HS 4th semester bengali
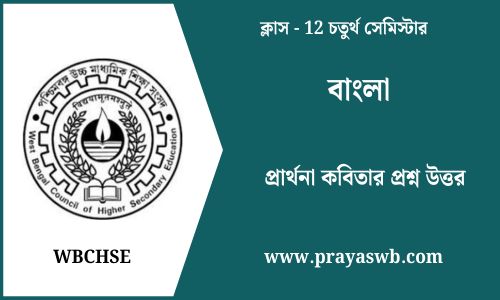
১। “চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির”-কোন্ প্রসঙ্গে কবি এ কথা বলেছেন? মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। ২+৩
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতায় এক নতুন স্বদেশের কল্পনা করেছেন। সেই মুক্ত স্বদেশে এবং আদর্শ সমাজব্যবস্থায় কবি একজন মানুষকে যেভাবে দেখতে চান, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
এমন এক ভারত কবি প্রত্যাশা করেছেন, যেখানে মানুষ তার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। নৈবেদ্য-র কবিতায় এই ভয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়- লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
ক্ষমতাবানদের ভয়, অস্তিত্ব হারানোর ভয়, অন্ধবিশ্বাসের অনুগত হওয়ার ভয়, মুক্তকন্ঠ বিসর্জনের ভয়-এরকম নানা ভয় ঘিরে থাকে এই সমাজে সাধারণ মানুষদের। আত্মশক্তির অভাবে যে মানুষ দাসত্বে অবনত হয়, শাসক বা ক্ষমতাবানদের কাছে নতজানু হয়ে আত্মবিক্রয় কিংবা আত্মসমর্পণ করে, তার কাছে ভয় হয়ে যায় এক স্থায়ী অনুভূতি। মাথা উঁচু করার মতো স্পর্ধা এই মানুষেরা দেখাতে পারে না। মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ভয়হীন মনের অধিকারী হবে এবং আর তখনই মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। একদিকে ব্যক্তিমানুষের আত্মিক পুনরুজ্জীবন, অন্যদিকে অনুকূল সমাজকাঠামোর মাধ্যমে কবি তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষিত ভারতকে পেতে চান-” চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির”।
২। “জ্ঞান যেথা মুক্ত”- কোন্ প্রসঙ্গে কবি এ কথা বলেছেন? কবির এ কথার তাৎপর্য কী? ২+৩
ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অবস্থান করে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতকে তাঁর আদর্শ স্বদেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, তার রূপকল্প তুলে ধরেছেন ‘প্রার্থনা’ কবিতায়। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশভূমিতে ব্যক্তি মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তার উল্লেখ প্রসঙ্গেই কবি উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের কাছে জ্ঞান ছিল সমস্ত সংস্কার, আচার-বিচার-এর ঊর্ধ্বে উঠে সত্যের ধারণা। আর ঠিক এর বিপরীত অনুশীলনেই তিনি লক্ষ করেছেন তার চারপাশের সমাজে। মানুষ সেখানে সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। মুক্তচিন্তার কোনো পরিসর নেই। ধর্মসাধনার নামে অজস্র আচার-আচরণ তাকে বেষ্টন করে আছে। স্বাধীন চিন্তার অনুমোদন নেই, অথবা তা আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে চেতনাগত অন্ধত্ব, যা সমাজকে ক্রমাগত পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষের জ্ঞান হবে মুক্ত, মুক্তজ্ঞান সত্যের সঙ্গে সমার্থক। নৈবেদ্য-র ৬১ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা, আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর।"
৩। “আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি” -‘আপন প্রাঙ্গণতলে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতায় ‘আপন প্রাঙ্গণতলে’ বলতে নিজের ক্ষুদ্র গৃহকোণ বা ব্যক্তিগত পরিসরকে বুঝিয়েছেন। মানুষ সেখানে আত্মসুখ এবং ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়।
রবীন্দ্রনাথের মতে, গৃহের প্রাচীর দিনরাত নিজের প্রাঙ্গণতলে বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করে রাখে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখ এবং স্বার্থের দিকে মানুষের পক্ষপাত বিশ্বজগৎ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ‘বহু’র দিকে মানুষের যে যাত্রা তা খণ্ডিত হতে বাধ্য যদি সে আত্মসুখসর্বস্ব হয়। বসুধার খন্ডরূপের অর্থ বিশ্বজনের সঙ্গে মিলতে না পারা, যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে।
আর ঠিক সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতে পারেননি সেই মানসিকতাকে; যা শুধু গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ রাখে এবং ব্যক্তিসুখের কথা ভাবে। ‘পূজা’ পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে, নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে।।"
রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে মানবজীবন ‘বহু’র সঙ্গে, সমষ্টির সঙ্গে মিলনের সাধনা। সে কারণেই তিনি ব্যক্তিগত চাওয়াকে অতিক্রম করে প্রয়োজনের সীমাকে ছিন্ন করতে চেয়েছেন। আত্মসুখসর্বস্বতা ‘বসুধা’-কে খণ্ড খণ্ড করে, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংযোগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।
৪। “বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি” -কীভাবে বসুধা খণ্ড ক্ষুদ্র হয়ে যায়? কেন কবির কাছে বসুধার সেই রূপ আকাঙ্ক্ষিত নয়? ২+৩
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতায় বলেছেন যে, গৃহের প্রাচীর দিনরাত নিজের প্রাঙ্গণতলে বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করে রাখে। অর্থাৎ মানুষ যত বেশি ব্যক্তিগত সুখ এবং স্বার্থের দিকে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, ততই বিশ্বজগত থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। গীতালি-র গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।"
এক থেকে ‘বহু’র দিকে মানুষের যে যাত্রা, তা খণ্ডিত হবে বা বাধাপ্রাপ্ত হবে; যদি সে আত্মসুখসর্বস্ব হয়। বিশ্বজনের সঙ্গে এই মিলতে না পারার অর্থ, তার বসুধার খণ্ডরূপে জীবনের ব্যর্থ নিমজ্জন।
রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে দুটো ‘আমি’-কে কল্পনা করেছিলেন-একটি হল তাঁর ‘ছোটো আমি’, অন্যটি ‘বড়ো আমি’। মানুষের যথার্থ যাত্রা এই ‘ছোটো আমি’ থেকে ‘বড়ো আমি’র দিকে। এর মধ্য দিয়েই মানুষ ব্যক্তিগত থেকে বিশ্বগত হয়ে ওঠে। আর ঠিক সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতে পারেননি সেই মানসিকতাকে, যে মানসিকতা শুধু গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ রাখে এবং ব্যক্তিসুখের কথা ভাবে। পূজা পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।”
বারবার তাঁর মনে হয়েছে মানবজীবন ‘বহু’র সঙ্গে, সমষ্টির সঙ্গে মিলনের সাধনা। সে কারণেই তিনি ব্যক্তিগতির সীমা ছিন্ন করতে চেয়েছেন। আত্মসুখসর্বস্বতার মধ্যে দিয়ে ‘বসুধা’র যে খন্ডীভবন ঘটে, তা কোনোভাবেই কবির কাছে প্রত্যাশিত নয়।
৫। “যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে/উচ্ছ্বসিয়া উঠে”-‘যেথা’ শব্দটির প্রয়োগে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
‘প্রার্থনা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন ভারতের কল্পনা করেছেন। যে ভারত হবে চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারায় সম্পূর্ণ মানবিক। ‘যেথা’ বলতে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুকূল সেই ভারতবর্ষের কথাই বলা হয়েছে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ তৈরি হয় যে ভাষা বন্ধনে, তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম এবং বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ। ফলে সেখানে সত্যের আত্মপ্রকাশের পথ অবরুদ্ধ থাকে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন-
"মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল; জ্ঞানের নিকট থেকে ধীরে দূরে থাকে।” (১৯৪৬-৪৭)।
রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে, মানবিক-সম্পর্কের বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য হৃদয়ের স্পর্শহীন এই ধরনের বাক্যে-সংলাপে। রবীন্দ্রনাথ সেই কবি, যিনি ছিলেন ‘হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল’। কথার সঙ্গে যদি হৃদয়ের সংযোগ থাকে, তাহলে মানবিক গুণাবলির প্রতিষ্ঠা ঘটে। তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের পথ সুগম হয়। একটি সুন্দর দেশ ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের গুরু নাটকে আচার্য বদ্ধ অচলায়তনে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ‘হৃদয়ের বাণী’, বলেছিলেন, “প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।” রবীন্দ্রনাথ মানবতার উদ্বোধনকেই ‘মানুষের ধর্ম’ বলে মনে করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রত্যাশা করেছেন যে, বাক্যের উচ্চারণ হবে হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে।
৬। ‘দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়’ -এখানে কোন কর্মধারার কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গটি উল্লেখের কারণ কী? ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতার অন্তর্গত উদ্ধৃত পঙ্ক্তিতে সাধারণ মানুষদের যে কর্মধারা পৃথিবীকে সচল ও গতিশীল করে রাখে, তার কথা বলেছেন।
যে উন্নত ও আদর্শ ভারতের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতায় দেখেছেন, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তি মানুষের চারিত্রিক উন্নতি। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে রবীন্দ্রনাথ কখনও চরম বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষার ভারতে মানুষ মানসিকভাবে হবে ভয়হীন, তার মেরুদণ্ড হবে সোজা এবং সে হবে মুক্তজ্ঞানের অধিকারী। ব্যক্তিমন সেখানে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত হবে অর্থাৎ বিশ্বমানবতাই হবে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন-“মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। সকল মানুষের মধ্যে তা বিদ্যমান।” ‘প্রবাসী’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।"
রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দেশ ও সমাজে আত্মসুখের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত রাখবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এরকম এক সমাজে মানুষের যে কর্মধারা, তা দুর্নিবার গতিতে প্রবাহিত হবে অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, অর্থাৎ তার লক্ষ্য সভ্যতার সমস্ত অভিমুখকে সঞ্জীবিত করা, তাকে গতিশীল করা।
৭। “বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি” কীসের কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রার্থনা’ কবিতার উদ্ধৃত অংশে কবি বলেছেন যে, তিনি যে আদর্শ ভারতের কল্পনা করেন, সেখানে তুচ্ছ আচার, মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং সংস্কার মূল্যায়ন কিংবা বিচারের যে গতিধারা তার পথকে অবরুদ্ধ করেনি।
আত্মপরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-“আত্মার ধর্ম কী তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ঘরে জানি এমন কথা বলিতে পারি নে-অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।” সমাজপ্রগতির পথে সব থেকে বড়ো বাধা হল মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার। যখনই মানুষ অন্ধআচারের উপরে নির্ভরশীল হয়, তখনই প্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগহীনতাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কার মুক্তচিন্তা এবং প্রাণের বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে। এক অদ্ভুত কূপমণ্ডুকতা গোটা সমাজকে গ্রাস করে। যে সমাজ মুক্তচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়, সেখানে অন্ধবিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই। সেখানে সমাজগত ও ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ভাবনাচিন্তা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার নতুন ভারতে এরকমই এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন-যেখানে অন্ধবিশ্বাস, স্বাধীন ভাবনা ও বিশ্লেষণের পথকে কখনও অবরুদ্ধ করে দেয়নি।
৮. “নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা” -এই ‘নেতা’-কে উদ্দেশ করে কবি কী প্রার্থনা করেছেন? এখানে কবির যে ঈশ্বরবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো। ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রার্থনা’ কবিতায় তাঁর আকাঙ্ক্ষার সুন্দর ভারত গড়ে তোলার পথে বাধা যে-সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলিকে দূর করার জন্য ‘সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা’-কে আহ্বান করেছেন। বলাবাহুল্য এখানে কবি ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করেছেন। সমস্ত স্বার্থপরতা, ভয়, বদ্ধতাকে দূর করে; আচার-সংস্কারকে দূরে সরিয়ে, পরাগতির সমস্ত চিহ্নগুলিকে আঘাত করে তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বর্গীয় মহিমা দান করেন-সেই প্রার্থনাই উল্লিখিত অংশে কবি করেছেন।
‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-“আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক’রে ‘সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ’। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।” সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে ‘সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা’ বলে উল্লেখ করেছেন। মানুষের মনের মধ্যেই তার অধিষ্ঠান।
"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে।"
সুতরাং কবি যখন ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে আঘাতের আহ্বান জানান তা আসলে সর্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষকে উদ্দেশ করেই আহ্বান। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানবমনের সংযুক্তি।
৯। “নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ” – এখানে ‘পিতঃ’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে? কাকে, কোথায় আঘাত করার কথা বলা হয়েছে? ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রার্থনা’ কবিতার উল্লিখিত অংশে যিনি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, সেই ঈশ্বরকেই পৃথক বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর মানুষের অন্তরে অবস্থান করা এক ‘সর্বজনীন সর্বকালীন মানব’। মানুষের ধর্মে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-“আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক’রে “সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ’। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।” সেকারণেই ঈশ্বরকে ‘সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাকে আঘাত করতে বলেছেন প্রাতিষ্ঠানিকতার অচল আয়তনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান হল আত্মপোলব্ধি। নৈবেদ্য-র সমসাময়িক কালে লেখা ‘ঔপনিষদিক ব্রহ্ম’ শীর্ষক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-“যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে, সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে। সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে-সেই ভোগে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না…।” সুতরাং কবি যখন ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পরাগতির সূচকগুলিতে আঘাতের আহ্বান জানান, সে আহ্বান আসলে তিনি করেন সর্ব মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষকে উদ্দেশ করেই। সে আঘাতের লক্ষ হবে সমস্ত আত্মগত সুখের অবসান, চিন্তাচেতনার বদ্ধতা থেকে মুক্তি এবং যে-সমস্ত আচার-বিচার-সংস্কার সভ্যতার গতিপথকে অবরুদ্ধ করতে পারে তার অবসান ঘটানো।
১০। “ভারতের এই সেই স্বর্গে করো জাগরিত” কাকে উদ্দেশ করে কবি এ কথা বলেছেন? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘প্রার্থনা’ কবিতার আলোচ্য পঙ্ক্তিতে সর্ব কর্ম-চির আনন্দের উৎস যে ঈশ্বর, তাঁকে উদ্দেশ করে মন্তব্যটি করেছেন।
কবি এখানে ‘স্বর্গ’ বলতে মানুষের জন্য বাসযোগ্য এমন এক স্বদেশের কল্পনা করতে চেয়েছেন, যা হবে স্বর্গের মতো। মানুষের মন সেখানে ভয়শূন্য হবে, মাথা উঁচু করে মানুষ বাঁচতে পারবে, মুক্ত জ্ঞানের চর্চা করতে পারবে। সেই আদর্শ স্বদেশভূমিতে আত্মসুখ বিশ্বমানবতার পথকে কখনও রুদ্ধ করবে না। মানুষের কর্মধারা সদর্থক লক্ষে পরিচালিত হবে এবং তুচ্ছ আচার কোনোভাবেই বিচার বা মূল্যায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সংস্কারমুক্ত মুক্তচেতনার অধিকারী হয়ে মানুষ পৌরুষদীপ্ত হয়ে উঠবে। আর স্বয়ং মানুষের ঈশ্বর এই পথে সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূর করে দেবেন। ‘মানুষের ধর্ম’ রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-“… মানুষের আর-একটা দিক আছে, যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে।… সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে।” কবির কাছে ব্যক্তির আত্মিক এবং সার্বিক সমুন্নতির আকাঙ্ক্ষিত মানববিশ্ব সেটাই, যা স্বর্গের সমতুল্য।
১১। ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কীভাবে ভারতবর্ষকে স্বর্গে জাগরিত করার কথা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি এক আদর্শবদ্ধ উন্নততর ভারতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। সেখানে প্রতিটি মানুষের মন থাকবে ভয়শূন্য, মাথা থাকবে উঁচু হয়ে। তারা মুক্তজ্ঞানচর্চার পথ অনুসরণ করবে। মানুষ পৃথিবী বলতে শুধু নিজের গৃহকে বুঝবে না, অর্থাৎ সে আত্মসুখসর্বস্ব হবে না, বিশ্বমানবতা হবে তার লক্ষ। তার প্রতিটা সংলাপ উঠে আসবে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। মানুষের যাবতীয় কর্মধারা পরিচালিত হবে সমষ্টির স্বার্থে।
কবি এমন এক ভারত চেয়েছেন, যেখানে জীর্ণ আচার কিংবা অন্ধ সংস্কার জীবনের চলার পথকে অবরুদ্ধ করবে না, ‘পৌরুষ’ অর্থাৎ চরিত্রের দৃঢ়তা এবং আদর্শবদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সমস্ত কর্ম-চিন্তা-আনন্দের পথপ্রদর্শক যিনি, সেই ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন যে, যা কিছু দেশকে পরাগতির দিকে নিয়ে যায় সেখানে আঘাত করে ভারতকে তিনি এক স্বর্গীয় মহিমা দান করুন। সর্বমানবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত এক উদার অথচ দৃঢ় আদর্শবদ্ধ স্বদেশকে কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নৈবেদ্য-র অন্য কবিতার ভাষায় বলা যেতে পারে-
"সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি, হে ভারত, সর্বদুঃখে রহো তুমি জাগি"