ভারত সরকারের বিভাগসমূহ : ভারতের বিচার বিভাগ প্রশ্ন উত্তর | ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান | Class 12 4th Semester Political Science fourth chapter question answer
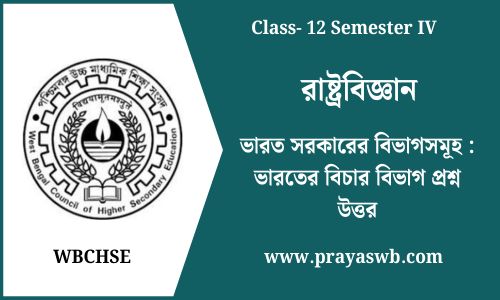
1. সুপ্রিমকোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions)
সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রকে মূলত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা- [১] মূল এলাকা (Original Jurisdiction), [২] আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction), [৩] পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction), এবং [৪] নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা (Jurisdiction to issue directions, orders and writs) |
(১) মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা: [1] আইনগত অধিকারের প্রশ্নে [a] কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য-সরকারের বিরোধ বাধলে, কিংবা [b] কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য-সরকারের সঙ্গে অন্য কয়েকটি বা একটি রাজ্য-সরকারের বিরোধ বাধলে, অথবা [c] দুই বা ততোধিক রাজ্য-সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে কেবল সুপ্রিমকোর্টই ওইসব বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে [১৩১ নং ধারা)। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ক’রে সুপ্রিমকোর্ট এইসব বিরোধের মীমাংসা করে। তাই সুপ্রিমকোর্টকে ‘ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা এবং রক্ষাকর্তা’ বলে অভিহিত করা হয়। আবার, [ii] রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন-সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্ন বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত [৭১ (১) নং ধারা)। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে ১৯৬৯ সালে শিবকৃপাল সিং, ফুল সিং প্রমুখ রাষ্ট্রপতিপদে ডি. ডি. গিরির এবং এইচ ভি. কামাথ উপরাষ্ট্রপতিপদে গোপালস্বরূপ পাঠকের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ ক’রে সুপ্রিমকোর্টের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রিমকোর্ট নির্বাচনকে সম্পূর্ণ বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল।
মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার ওপর আরোপিত বাধানিষেধসমূহ: সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা সীমাহীন নয়। সংবিধান এর ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করেছে। বলা হয়েছে যে, [১] সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে যেসব সন্ধি (treaty), চুক্তি (agreement), অঙ্গীকারপত্র (convenant), সনদ (charter) প্রভৃতি সম্পাদিত বা কার্যকর হয়েছিল এবং সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরেও যেগুলি কার্যকর রয়েছে, সেইসব বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি বা বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের নেই [১৩১ নং ধারা)। [২] তা ছাড়া, ওই ধরনের সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ প্রভৃতিতে যদি একথা বলা থাকে যে, সেই সংক্রান্ত কোনো বিবোধের ক্ষেত্র পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টের এক্তিয়ার সম্প্রসারিত হবে না, তাহলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের নেই [১৩১ নং ধারা)। তবে ওইসব বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পরামর্শ চাইলে সুপ্রিমকোর্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শদান করতে বাধ্য থাকে [১৪৩ (২) নং ধারা)। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য নন। [৩] আবার, বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে কিংবা একটি রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য একটি রাজ্যের অধিবাসীদের বিরোধের বিচার সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না।
(২) আপিল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা: সুপ্রিমকোর্ট হল দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এই আদালতের আপিল এলাকাকে প্রধানত যে-চার ভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলি হল-[1] সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আপিল, [ii] দেওয়ানি আপিল, [iii] ফৌজদারি আপিল এবং [iv] বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল।
[i] সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আপিল: কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য যে-কোনো মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে শংসাপত্র (certificate) দেয় যে, সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে সেই মামলার বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায় [১৩২ (১) নং ধারা)। কিন্তু বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এরূপ শংসাপত্র প্রদান করতে অস্বীকৃত হলে সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত এমন যে-কোনো মামলার বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্ট নিজেই আপিল করার ‘বিশেষ অনুমতি’ দিতে পারে [১৩৬ (১) নং ধারা]।
[ii] দেওয়ানি আপিল: বর্তমানে [a] কোনো দেওয়ানি মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন জড়িত আছে কিংবা [b] কোনো দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করলে সেই মামলা সম্বন্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায় [১৩৩ (১) নং ধারা]। ১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনের ফলে বর্তমানে আপিল বিষয়ে যাতে অযথা বিলম্ব না হয়, সেজন্য রায়দানের সময়েই হাইকোর্ট আপিলের অনুমতি দিতে কিংবা বিবদমান যে-কোনো পক্ষ মৌখিকভাবে আবেদন জানালেই সেই আবেদন তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করতে পারে।
[iii] ফৌজদারি আপিল: ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। এগুলি হল-[a] নিম্নতর আদালতের বিচারে নির্দোষ বলে প্রমাণিত কোনো ব্যক্তিকে হাইকোর্ট যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা [৮] নিম্ন আদালতে বিচার চলাকালীন কোনো মামলা নিজের হাতে তুলে নিয়ে হাইকোর্ট যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়, কিংবা [c] হাইকোর্ট যদি কোনো মামলাকে সুপ্রিমকোর্টের কাছে আপিলযোগ্য বলে শংসাপত্র দেয় [১৩৪ (১) নং ধারা।। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন ক’রে সুপ্রিমকোর্টকে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে আপিল গ্রহণ ও তার শুনানির জন্য অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করতে পারে (১৩৪ (২) নং ধারা)। সংবিধানের এই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্টের ফৌজদারি আপিল এলাকার সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত একটি বিল লোকসভায় গৃহীত হয়েছিল। ফলে বর্তমানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত যে-কোনো নাগরিক সুপ্রিমকোর্টে আপিল করতে পারেন।
[iv] বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল: পূর্বোক্ত তিন প্রকার ক্ষেত্র ছাড়াও ভারতের যে-কোনো আদালতের যে-কোনো রায়, আদেশ ও দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার ‘বিশেষ অনুমতি’ (‘Special Leave’) সুপ্রিমকোর্ট দিতে পারে [১৩৬ (১) নং ধারা)। সাধারণত ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট এরূপ আপিল করার অনুমতি দান করে। তবে কোনো সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট ‘বিশেষ অনুমতি’ দিতে পারে না।
(৩) পরামর্শদান-সংক্রান্ত এলাকাভুক্ত ক্ষমতা: কয়েকটি আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। [i] রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, আইন বা তথ্য-সংক্রান্ত কোনো সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে বা উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা আছে, তবে তিনি সে বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন [১৪৩ (১) নং ধারা)। অবশ্য এইসব প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টকে পরামর্শ প্রদান করতে বাধ্য করা যায় না। [ii] সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরেও বলবৎ রয়েছে, সেইসব বিষয়ে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন [১৪৩ (২) নং ধারা)। এক্ষেত্রে পরামর্শদান বাধ্যতামূলক। লক্ষণীয় বিষয় হল-দুটি ক্ষেত্রেই প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।
(৪) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারির ক্ষমতা: ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকারগুলি সংরক্ষণ করার জন্য বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপুচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার অধিকারী [৩২ নং ধারা)। তবে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি ক’রে ২০৪ ২১ নং ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া অন্য সব মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করার অধিকার খর্ব করতে পারেন (৩৫৯ (১) নং ধারা)।
(৫) অন্যান্য ক্ষমতা: উপরিউক্ত ক্ষমতাবলি ছাড়াও সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, যথা-[1] সংবিধান সুপ্রিমকোর্টকে অভিলেখ আদালত (Court of Records) হিসেবে কাজ করার অধিকার প্রদান করেছে। সুপ্রিমকোর্টে সংরক্ষিত নথিপত্র ভারতের যে-কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষ যথার্থ এবং প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। [ii] সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন মামলায় নিজের দেওয়া যে-কোনো রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। [iii] নিজের অবমাননার জন্য সুপ্রিমকোর্ট অবমাননাকারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। [iv] সুপ্রিমকোর্ট নিজ এলাকাভুক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে যে-কোনো বিষয়ে পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ডিক্রি বা আদেশ জারি করতে পারে। এরূপ ডিক্রি বা আদেশ ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডে কার্যকর হবে [১৪২ (১) নং ধারা)। তা ছাড়া, সুপ্রিমকোর্ট তার সামনে যে-কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত হওয়ার এবং যে-কোনো দলিল পেশ করার বা তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে পারে [১৪২ (২) নং ধারা)। [v] নিজ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনমতো কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের হাতে অর্পিত হয়েছে।
2. হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions)
ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, হাইকোর্টের ক্ষেত্রে কিন্তু সেইরূপ করা হয়নি। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে হাইকোর্টসমূহ যেসব ক্ষমতা ভোগ করত, সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরেও তারা অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই তাদের সংবিধান এবং যথাযোগ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে [২২৫ নং ধারা]। হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত সাতটি ভাগে ভাগ ক’রে আলোচনা করা যেতে পারে:
(১) মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা: [1] রাজস্ব-সংক্রান্ত সব বিষয়ই হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। তা ছাড়া, [ii] অনেক ক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাকেও মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। তবে কেবল কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই-এর হাইকোর্ট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতে পারত। কিন্তু ১৯৭৩ সালে ফৌজদারি দণ্ডবিধি (The Criminal Procedure Code, 1973) সংশোধিত হওয়ার ফলে হাইকোর্টের ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার বিলোপসাধন করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই শহরে ফৌজদারি মামলার বিচার নগর দায়রা আদালত (City Sessions Court)-এ সম্পাদিত হয়।
(২) আপিল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা: হাইকোর্ট হল রাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে (1) জেলা জজ এবং অধস্তন জেলা জজের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। আবার, [ii] কেবল আইন ও পদ্ধতিগত প্রশ্নে কোনো অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলায় কোনো ঊর্ধ্বতন আদালত যে-রায় দেয়, তার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে। তা ছাড়া, [iii] হাইকোর্টের কোনো বিচারকের একক রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যায়। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে [1] দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ কোনো ব্যক্তিকে ৭ বছরের অধিক কারাদণ্ডে দন্ডিত করলে কিংবা [ii] কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে সহকারী দায়রা জজ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্যান্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।
(৩) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারির ক্ষমতা: নিজ এলাকাভুক্ত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব হাইকোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। হাইকোর্ট এই অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ, নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারে [২২৬ (১) নং ধারা]। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ ছাড়াও ‘অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্যে’ (‘for any other purpose’) হাইকোর্ট লেখ, নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে সক্ষম। কিন্তু এই ক্ষমতা ভারতের সুপ্রিমকোর্টের হাতে অর্পিত হয়নি। তবে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে হাইকোর্টের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সংকুচিত হতে পারে। অবশ্য ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার সময়েও হাইকোর্টের ‘বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ’ ধরনের রিট বা লেখ জারির ক্ষমতাকে সাময়িকভাবেও খর্ব করা যাবে না।
(৪) আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা: মূল সংবিধানে হাইকোর্টের হাতে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য-আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৬) মাধ্যমে হাইকোর্টের হাত থেকে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলেও ১৯৭৮ সালে ৪৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তদানীন্তন দেশাই-সরকার সেই ব্যবস্থা বাতিল ক’রে দিয়ে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে এনেছে।
(৫) তত্ত্বাবধান-সংক্রান্ত ক্ষমতা: হাইকোর্ট নিজ এলাকার অন্তর্ভুক্ত সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ছাড়া অন্যান্য আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহের তত্ত্বাবধান করতে পারে। এই ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট যে-কোনো প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল করার জন্য অধস্তন আদালতসমূহকে নির্দেশ দিতে সক্ষম। অধস্তন আদালতের কর্মচারীবৃন্দ কীভাবে নথিপত্র এবং হিসাবপত্র রক্ষা করবে, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের অধিকার হাইকোর্টের রয়েছে।
(৬) মামলা অধিগ্রহণের ক্ষমতা: অধস্তন কোনো আদালতের বিচারাধীন কোনো মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে বলে মনে করলে সংশ্লিষ্ট মামলাটির বিচারের দায়িত্ব হাইকোর্ট স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারে।
(৭) নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ক্ষমতা: হাইকোর্ট অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জেলা জজের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে এবং অধস্তন আদালতসমূহের অন্যান্য বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ ক’রে থাকেন।
জেলা আদালত-সহ অন্যান্য অধস্তন আদালতের কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে হাইকোর্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(৮) অন্যান্য ক্ষমতা: উপরিউক্ত ক্ষমতাবলি ছাড়াও হাইকোর্ট অন্যান্য কয়েকটি কার্য সম্পাদন করে। [1] সুপ্রিমকোর্টের মতো হাইকোর্টকেও অভিলেখ আদালত (Court of Records) হিসেবে কাজ করতে হয়। [ii] হাইকোর্ট নিজ অবমাননার জন্য অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে। [iii] হাইকোর্ট বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি তৈরি করার অধিকারী।
3. জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা
জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা হল এক বিশেষ ধরনের মামলা, যার উদ্দেশ্য হল জনগণের সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে কৃতকর্মজনিত ক্ষয়ক্ষতি বা আঘাতের সুরাহা করা, জনস্বার্থ বিষয়ক কর্তব্য সম্পাদন সুনিশ্চিত করা এবং জনস্বার্থের দ্যোতক সামাজিক, সামগ্রিক ও বিক্ষিপ্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। জনস্বার্থের ধারক-বাহক যে-কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠন বা ব্যক্তি এরকম মামলা আদালতে বুলু করতে পারেন।
আদালতের বিচার্য বিষয়: জনস্বার্থ বিষয়ক আবেদন আদালতে পেশ করা হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি গ্রহণ করার। আগে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করে দেখে-
- [১] মামলাটি ব্যক্তিগত লাভালাভ বা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কি না। মামলাটি ওরকম বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত হলে তবেই সেটিকে গ্রহণ করা হয়।
- [২] মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিংবা অস্পষ্ট বিচারবিবেচনার বিষয় কি না। তেমনটা হলে সেই আবেদন গ্রহণ করা হয় না।
- [৩] মামলাটি সাধারণ কারণে সম্পর্কিত বা জনস্বার্থ হয়।
জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা দায়ের: স্কুল বা ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা দায়ের করতে পারে। এমনকী কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তরফে এই ধরনের মামলা দায়ের করতে পারে। ক্ষুথ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বা পক্ষের যন্ত্রণার নিরাময় বা অসুবিধার অবসান করাই হল জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার উদ্দেশ্য।
ভারতে ১৯৭৯ সালে প্রথম জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা দায়ের হয়। হুসেনারা খাতুন বনাম বিহার রাজ্য নামে পরিচিত ওই মামলাটি বিহারের হাজার হাজার জেলবন্দির তরফে রুজু করা হয়। কারাগারে অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। মামলা বুজু হওয়ার পর বিচারপতি পি এন ভগবতীর নেতৃত্বাধীন বেশ জেলবন্দিদের নিখরচায় আইনি সহায়তা প্রদান এবং মামলাটির দ্রুত শুনানির পক্ষে রায় দেন। শেষ পর্যন্ত মামলাকারিরা জেল থেকে মুক্তি পায়। তখন থেকে বিভিন্ন বিষয় জনস্বার্থে মামলা রুজু করার উপযুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে বন্ধুয়া মজদুরদের দাসত্বের অবসান ঘটানোর মতো আর্থসামাজিক বিষয়, খাদ্যের বা কর্মের অধিকারের মতো আইনি অধিকার সম্পর্কিত বিষয়, বায়ুদূষণ কিংবা জলদূষণের মতো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টন অথবা আইনসভার সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশের মতো রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়, সবকিছুই জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার উপযুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের অধিকার বিষয়ক সাবেকি ধারণার সঙ্গে জনস্বার্থ সম্পর্কিত মামলার ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাবেকি ধারণা অনুযায়ী, অপরপক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পক্ষ ব্যতিরেকে কেউ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার ভোগ করতে পারে না। কিন্তু জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায়, কোনো এক আবেদনকারী যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, কেবল এই কারণে আদালত আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দিতে পারে না বা ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।
মূল্যায়ন:
জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার বিষয়টি যেমন অতিমাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনই এটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে।
প্রথমত, এই ধারণার মামলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে কেবল বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অথচ বাস্তবে নিহিত আছে অন্যান্য অনেক বিষয়, সেগুলি আইন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।
দ্বিতীয়ত, জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার সৌজন্যে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে। ফলে, তাঁদের দায়িত্ববোধ প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে এবং গঠনমূলক উদ্যোগ আয়োজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
পরিশেষে, জনস্বার্থ বিষয় মামলা বিচার বিভাগের অতিসক্রিয়াতে প্রশ্রয় দেয়।
এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার্য যে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার সুবাদে কারাগার, মানসিক চিকিৎসালয় বা পাগলাগারদ, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হওয়াটা নাগরিকদের পক্ষে সহজতর হয়েছে। বিচার বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই মানুষের অধিকার বোধের পরিধিও প্রসারিত হয়েছে।
4. ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
ক্রেতা আদালত [Consumer Court)
ক্রেতা বা উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রুততার সঙ্গে এবং স্বল্পব্যয়ে ক্রেতাদের অভাব-অভিযোগের সুরাহার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। সমগ্র দেশ এই আইনের আওতাভুক্ত যে-কোনো প্রকার ব্যাবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ, নির্মাণ, কারবারি লেনদেন, দ্রব্য বা পরিসেবার জোগান, এমনকি ই-কমার্স সংস্থাও এই সুরক্ষা আইনের আওতায়। পড়ে। এক অর্থে এই আইন ক্রেতা বা উপভোক্বাদের ক্ষমতায়ন ও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত।
ত্রিস্তরবিশিষ্ট ক্রেতা আদালতের গঠন (Structure of Three-tier Consumer Courts)
১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ত্রিস্তরবিশিষ্ট ক্রেতা আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই আদালতগুলিকে ‘বিশেষ আদালত’ (special courts’) বা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আদালত’ (‘special purpose court’) বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, ক্রেতা বা উপভোক্তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার বিধানের উদ্দেশ্যে এই ধরনের আদালত গঠন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ত্রিস্তরীয় ক্রেতা আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। যে-তিনটি স্তর নিয়ে এরূপ বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল- [১] জেলা-স্তর (District Level), [২] রাজ্য-স্তর (State Level) এবং [৩] জাতীয় স্তর (Nationa Level)
জেলা-স্তর-জেলা আদালত [District Level-District Forum
ক্রেতা আদালতের গঠন একটি পিরামিডের মতো। এর সর্বনিম্ন স্তরে, অর্থাৎ প্রতিটি জেলায় রয়েছে একটি (কখনও বা একাধিক) ক’রে ‘কেতা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ আদালত’ (Consumer Disputes Redressal Forum’), যা ‘জেলা আদালত’ (‘District Forum’) নামে পরিচিত।
জেলা আদালতের এক্তিয়ার: ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যবিশিষ্ট দ্রব্য বা পরিসেবা সংক্রান্ত অভিযোগ মীমাংসার এক্তিয়ার জেলা কমিশনের। প্রথম শুনানি কিংবা তত্পরবর্তী যে-কোনো পর্যায়ে জেলা কমিশনের মনে হতে পারে বিষয়টির আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা সম্ভব এবং সেই মীমাংসা এমন হবে যা বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। জেলা কমিশন মধ্যস্থতা করে পাঁচ দিনের মধ্যে মামলাকারীদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ করতে পারে। যদি বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষই লিখিতভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসায় সম্মত হয়, তবে জেলা কমিশন বিষয়টিকে আদালত-বহির্ভুত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করে। তবে শেষপর্যন্ত এভাবে মীমাংসা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আইনি কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। যদি বিশ্লেষণ না-করে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ত্রুটি নিঃসন্দেহে নিরুপিত না হয়, তবে জেলা কমিশন দ্রব্যটির নমুনা সংগ্রহ করে সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠায়। পরিসেবার ক্ষেত্রে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা হয়। অভিযোগকারী যাদের সাক্ষ্যের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জেলা কমিশন তাদেরই সাক্ষ্যদানের জন্য সমন পাঠায়। এক্ষেত্রেও নথি ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। আদালতের বাইরে মীমাংসার জন্য কমিশন পদক্ষেপ করতে পারে। জেলা কমিশনের রায়ে বাদী কিংবা বিবাদী পক্ষ সন্তুষ্ট নাহলে সে রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য কমিশনের কাছে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাতে পারে। রায়দানের ৪৫ দিনের মধ্যে, এই ধরনের আবেদন করা যায়।
রাজ্য-স্তর-রাজ্য-কমিশন Commission] [State Level-State
ত্রিস্তরবিশিষ্ট ক্রেতা আদালতের মধ্যবর্তী স্তরটি হল রাজ্য-স্তর। এই স্তরের আদালতের নাম হল ‘রাজ্য ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন’ (State Consumer Disputes Redressal Commission), যা রাজ্য-কমিশন (State Commission) নামে পরিচিত।
রাজ্য-কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের বেতন, ভাতা, চাকুরির শর্তাবলি প্রভৃতি রাজ্য-সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়।
রাজ্য-কমিশনের এক্তিয়ার: সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার রাজা কমিশন রাজ্যের রাজধানীতে সাধারণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। ৫০ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ২ কোটি টাকার কম মূল্যবিশিষ্ট দ্রব্য বা পরিসেবা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা রাজ্য কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত। রাজ্য কমিশনের রায়ে সন্তুষ্ট নাহলে বাদী বা বিবাদী পক্ষ রায় দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় কমিশনে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারে।
জাতীয় স্তর-জাতীয় কমিশন (National Level-National Commission]
ত্রিস্তরবিশিষ্ট ক্রেতা আদালতের সর্বোচ্চ স্তরটি হল জাতীয় (national level) স্তর। এই স্তরের আদালতের নাম হল জাতীয় ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন’ (‘National | Consumer Disputes Redressal Commission’), যা ‘জাতীয় কমিশন’ (‘National Commission’) নামে পরিচিত।
জাতীয় কমিশনের এক্তিয়ার: সমগ্র দেশ জাতীয় কমিশনের আওতাধীন। ২ কোটি টাকা মূল্যের অধিক দ্রব্য বা পরিসেবা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি জাতীয় কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। জাতীয় কমিশনের দেওয়া রায়ে সন্তুষ্ট নাহলে বাদী কিংবা বিবাদী পক্ষ রায়দানের ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাতে পারে। ক্রেতা আদালতে যেসকল বিষয়ের সুরাহা হয় (Relief Available in Consumer Court): যদি জেলা, রাজ্য বা জাতীয় কমিশন সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি ত্রুটিযুক্ত ছিল বা সংশ্লিষ্ট পরিসেবায় কোনো খামতি ছিল কিংবা সংশ্লিষ্ট লেনদেনে অন্যায় কিছু ঘটেছে অথবা দ্রব্যটি প্রদানকারী সংস্থা নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণের দাবি মেটাতে দায়বদ্ধ এরকম কোনো বিষয়ে নিঃসংশয় হয়, তবে তারা এই মর্মে আদেশ দিতে পারে যে-
- [১] সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির ত্রুটি সারিয়ে দিতে হবে বা সংশ্লিষ্ট সেবায় ত্রুটি পরিমার্জনার ব্যবস্থা নিতে হবে। [
- ২] সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি বদলে নতুন ত্রুটিমুক্ত দ্রব্য প্রদান করতে হবে।
- [৩] দ্রব্য বা পরিসেবাটির জন্য প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিতে হবে।
- [৪] উপভোক্তা বা ক্রেতা যে ক্ষতির শিকার হয়েছেন সেজন্য। উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- [৫] যথাবিহিত শাস্তিমূলক আর্থিক জরিমানা ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে।
- [৬] অভিযুক্ত সংস্থার সঙ্গে ব্যাবসায়িক কারবারে ভবিষ্যতে ছেদ টানতে হবে।
- [৭] বিপজ্জনক দ্রব্যটি বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- [৮] বিপজ্জনক দ্রব্যটিকে বাজার থেকে তুলে নিতে হবে।
- [৯] বিপজ্জনক দ্রব্যটির প্রস্তুতকারী উপাদানসমূহ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং ক্ষতিকারক পরিসেবা প্রদানে বিরত থাকতে হবে।
- [১০] দ্রব্য বা পরিসেবাটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা বা উপভোক্তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
বিবাদের সঙ্গে যুক্ত কোনো পক্ষ যদি জেলা, রাজ্য বা জাতীয় কমিশনের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো আর্জি না জানায়, তবে সেটি চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।
উপসংহার: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ক্রেতাদের শোষণ, ওজন ও মাপ কম দেওয়া, জিনিসপত্রে ভেজাল দেওয়া প্রভৃতির হাত থেকে ক্রেতাদের সুরক্ষার জন্য অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ-ভারতে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার কথা প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বলা হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আইনও প্রণীত হয়েছে। এইসব আইনের মধ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ এবং তার বিভিন্ন সংশোধনীর ভিত্তিতে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারত সরকার কিংবা রাজ্য-সরকারগুলি ক্রেতা ও পরিসেবা লাভকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সরকারের ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজা-সরকারও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ‘জাগো গ্রাহক জাগো’ প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু করেছে। এতদসত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা ও পরিসেবা লাভকারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষত, গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমতাবস্থায় ক্রেতা-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারকে যেমন আরও বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, তেমনি সমাজ-সচেতন অগ্রণী মানুষদেরও অনেক বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত করতে না-পারলে সাধারণ ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে না।
ভারত সরকারের বিভাগসমূহ : ভারতের বিচার বিভাগ প্রশ্ন উত্তর (Marks : 2)
1. ভারতের সুপ্রিমকোর্ট কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: 2011 খ্রিস্টাব্দের প্রণীত একটি আইন অনুসারে ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং সর্বাধিক 30 জন অন্যান্য বিচারপতি অর্থাৎ সর্বমোট 31 জন বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হয়।
2. ভারতের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য বিচারপতিরা কীভাবে নিযুক্ত হন?
উত্তর: ভারতের সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। তত্ত্বগতভাবে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী তিনি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।
3. সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রকে কটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং কী কী?
উত্তর: সুপ্রিমকোর্টের কার্যক্ষেত্রকে মূলত চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা- [১] মূল এলাকা, [২] আপিল এলাকা, [৩] পরামর্শদান এলাকা, [৪] নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা।
4. সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত যে-কোনো একটি ক্ষমতা উল্লেখ করো।
উত্তর: রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্ন বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
5. সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার ওপর আরোপিত বাধানিষেধগুলির মধ্যে যে-কোনো একটির উল্লেখ করো।
উত্তর: সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতার ওপর আরোপিত একটি বাধা হল-একটি রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য রাজ্যের অধিবাসীদের বিরোধের বিচার সুপ্রিমকোর্ট করতে পারে না।
6. সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকাকে ক-ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কী কী?
উত্তর: সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, সেগুলি হল-[১] সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল, [২] দেওয়ানি আপিল, [৩] ফৌজদারি আপিল এবং [৪] বিশেষ অনুমতির জন্য আপিল।
7. কোন ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট নিজেই আপিল করার অনুমতি দিতে পারে?
উত্তর: কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য যে-কোনো মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে শংসাপত্র (certificate) দেয় যে, সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে সেই মামলার বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায় [১৩২ (১) নং ধারা। কিন্তু বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এরূপ শংসাপত্র প্রদান করতে অস্বীকৃত হলে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত এমন যে-কোনো মামলার বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্ট নিজেই আপিল করার ‘বিশেষ অনুমতি’ দিতে পারে [১৩৬ (১) নং ধারা।
৪. ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে যে-তিনটি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়, সেগুলির মধ্যে যে-কোনো দুটির উল্লেখ করো।
উত্তর: ফৌজদারি মামলার তিনটি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের কাছে আপিল করা যায়। এর মধ্যে দুটি হল- [১] নিম্নতর আদালতের বিচারে নির্দোষ বলে প্রমাণিত কোনো ব্যক্তিকে হাইকোর্ট যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা [২] নিম্ন আদালতে বিচার চলাকালীন কোনো মামলা নিজের হাতে তুলে নিয়ে হাইকোর্ট যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়।
9. কোন্ অবস্থায় সুপ্রিমকোর্ট আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে?
উত্তর: ভারতের যে-কোনো আদালতের যে-কোনো রায়, আদেশ ও দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি সুপ্রিমকোর্ট দিতে পারে। তবে কোনো সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বিশেষ অনুমতি দিতে পারে না।
10. যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন, সেগুলির মধ্যে যে-কোনো দুটি উল্লেখ করো।
উত্তর: কয়েকটি আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শগ্রহণ করতে পারেন। এর মধ্যে দুটি হল- [১] রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, আইন বা তথ্য সংক্রান্ত কোনো সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে বা উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা আছে, তবে তিনি সে বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন [১৪৩ (১) নং ধারা)। অবশ্য এইসব প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টকে পরামর্শ প্রদান করতে বাধ্য করা যায় না। [২] সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকারপত্র, সনদ প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরেও বলবৎ রয়েছে, সেইসব বিষয়ে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন [১৪৩ (২) নং ধারা)। এক্ষেত্রে পরামর্শদান বাধ্যতামূলক। লক্ষণীয় বিষয় হল, দুটি ক্ষেত্রেই প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।
11. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিমকোর্ট কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে?
উত্তর: ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকারগুলি সংরক্ষণ করার জন্য বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার অধিকারী [৩২ নং ধারা)। তবে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে ২০ ও ২১ নং ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া অন্য সব মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করার অধিকার খর্ব করতে পারেন (৩৫৯ (১) নং ধারা)।
12. সুপ্রিমকোর্টের ‘বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা’ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুপ্রিমকোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের আদেশ প্রভৃতি সংবিধানবিরোধী কি না, তা বিচার করে। কোনো আইন, আদেশ বা নির্দেশ সংবিধানসম্মত না-হলে সর্বোচ্চ আদালত সেটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। বলা বাহুল্য, আদালত কর্তৃক অবৈধ বলে ঘোষিত কোনো আইন, আদেশ বা নির্দেশ কখনোই কার্যকর হতে পারে না; সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতাকে ‘বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা পুনর্বীক্ষণের ক্ষমতা’ (‘power of judicial review’) বলা হয়।
13. সুপ্রিমকোর্ট কীসের মাধ্যমে ‘অতি-সক্রিয়’ হয়ে উঠেছে?
উত্তর: ‘জনস্বার্থমূলক মামলা’ বা ‘পিল’ (Public Interest Litigation- PIL.) এবং ‘সামাজিক কার্যমূলক মামলা’ বা ‘সাল’ (Social Action Litigation-SaL)-এর মাধ্যমে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ‘অতি সক্রিয়’ হয়ে উঠেছে।
14. সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের ইতিবাচক ভূমিকার যে-কোনো দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের দুটি ইতিবাচক ভূমিকা হল-[১] ‘অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন’ বা মিসা’র ১৭(ক) অনুচ্ছেদটি বাতিল করা, বধুহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কম দন্ড দেওয়ার সপক্ষে রায় এবং [২] বেগার শ্রমিকদের মুক্তি ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া।
15. একটি রাজ্যের হাইকোর্ট কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি রাজ্যের হাইকোর্ট গঠিত হয়। রাজ্যের বিচার বিভাগের শীর্ষে হাইকোর্টের অবস্থান।
16. হাইকোর্টের আপিল এলাকাভুক্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে যে-কোনো দুটির উল্লেখ করো।
উত্তর: হাইকোর্ট হল রাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে (১) জেলা জজ এবং অধস্তন জেলা জজের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। আবার, [২] কেবল আইন ও পদ্ধতিগত প্রশ্নে কোনো অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলায় কোনো ঊর্ধ্বতন আদালত যে-রায় দেয়, তার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে।
17. কোন্ ক্ষমতাটি ভারতের সুপ্রিমকোর্টের হাতে অর্পিত হয়নি, কিন্তু হাইকোর্টের হাতে অর্পিত হয়েছে?
উত্তর: নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ ছাড়াও ‘অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্যে’ হাইকোর্ট লেখ নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে সক্ষম। এই ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের হাতে অর্পিত হয়নি
18. বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে কি না, তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর: মূল সংবিধানে হাইকোর্টের হাতে কেন্দ্রীয় আইন ও বাজ্য-আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৬) মাধ্যমে হাইকোর্টের হাত থেকে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলেও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তদানীন্তন দেশাই সরকার সেই ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে এনেছে।
19. ভারতে অধস্তন আদালতগুলিকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
উত্তর: ভারতে অধস্তন আদালতগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায় [১] জেলার অধস্তন আদালত এবং [২] মহানগরীয় অঞ্চলের অধস্তন আদালত।
20. জেলার দেওয়ানি আদালতগুলি ক-টি স্তরে অবস্থিত এবং কী কী?
উত্তর: জেলার দেওয়ানি আদালতগুলি চারটি স্তরে অবস্থিত- [১] জেলা বিচারকের আদালত, [২] অবর বিচারকের আদালত, [৩] মুন্সেফের আদালত এবং [৪] ন্যায়। পঞ্চায়েত।
21. জেলার ফৌজদারি আদালতগুলিকে ক-টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
উত্তর: জেলার ফৌজদারি আদালতগুলি তিনভাগে বিভক্ত-[১] দায়রা আদালত, [২] অবর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং [৩] পঞ্চায়েত আদালত।
22. ক্ষমতার গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের কটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং কী কী?
উত্তর: ক্ষমতার গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি।
23. মহানগরীয় অঞ্চলের ফৌজদারি মামলার বিচার কীভাবে হয়?
উত্তর: মহানাগরীয় অঞ্চলে ফৌজদারি মামলার বিচার করে নগর দায়রা আদালত। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহানগরীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আপিল করা যেতে পারে।
24. কী ধরনের মামলার নিষ্পত্তি লোক আদালত করে থাকে?
উত্তর: যেসব বিষয় অত্যন্ত জটিল প্রকৃতি সম্পন্ন নয় সেই সব বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি লোক আদালতে হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ক্ষতিপূরণের দাবি, বণ্টন সংক্রান্ত মামলা, বিমা কোম্পানির কাছে অর্থ দাবি, বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি লোক আদালতে হয়ে থাকে।
25. ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি কবে প্রণীত হয় এবং কখন থেকে তা কার্যকর হয়েছে?
উত্তর: ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ‘ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি প্রণীত হয় এবং ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল থেকে আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমগ্র ভারতে কার্যকর হয়।
26. ভারতে ক্রেতা আদালতগুলিকে ‘বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আদালত’ বলে কেন চিহ্নিত করা হয়?
উত্তর: ভারতে ক্রেতা ও উপভোক্তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার বিধানের উদ্দেশ্যে ক্রেতা আদালতগুলি গঠিত হয়েছে। তাই এই আদালতগুলিকে ‘বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আদালত’ বলে চিহ্নিত করা হয়।
27. জেলা আদালত কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
উত্তর: প্রতিটি জেলা আদালত নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়-[১] একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক (District Judge) কিংবা এরূপ বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি, যিনি সংশ্লিষ্ট আদালতের সভাপতি (President) হিসেবে কার্য সম্পাদন করেন এবং [২] অন্য দুজন সদস্য, যাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হবেন।
আরো পড়ুন : উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্ন উত্তর