ভারত সরকারের বিভাগসমূহ : ভারতের শাসন বিভাগ প্রশ্ন উত্তর | ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান | Class 12 4th Semester Political Science forth chapter Short question answer
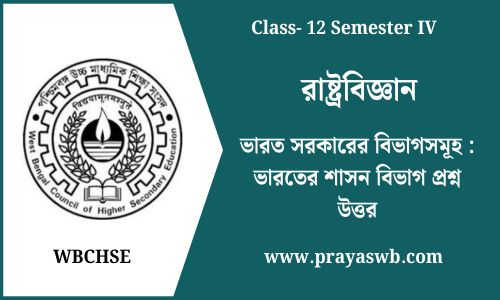
1. ভারতে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্য নির্বাচক সংস্থাটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
উত্তর: একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional representation by means of the single transferable vote)-এর নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College) কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। [১] ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের এবং [২] জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-সহ রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের, অর্থাৎ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়।
2. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার একজন সদস্যের ভোটসংখ্যা কীভাবে নির্ধারিত হয়?
উত্তর: রাজ্য-বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয়: প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। তারপর ভাগফলকে ১,০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয়, তবে দ্বিতীয় ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ ক’রে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভোটদানের সময় বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য একটি ক’রে ভোট দিলেও ভোটগণনার সময় সেই একটি ভোটের মূল্য হিসেবে পূর্বোক্ত ভোটসংখ্যাকেই ধরা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২৮টি অঙ্গরাজ্য ছাড়াও জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি এবং পুদুচেরি (এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। কোনো রাজ্যের ‘জনসংখ্যা’ বলতে সর্বশেষ ‘জনগণনা প্রতিবেদন’ (Census Report)-এ প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বোঝায়। কিন্তু ৮৪তম সংবিধান (সংশোধন) আইন, ২০০১ অনুযায়ী ২০২৬ সালের পরবর্তী সময়ে প্রথম ‘জনগণনা প্রতিবেদন’ প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ‘জনগণনা প্রতিবেদন’-এ উল্লিখিত জনসংখ্যাকেই প্রতিটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হবে।
3. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্টের একজন সদস্যের ভোটসংখ্যা কীভাবে নির্ধারিত হয়?
উত্তর: পার্লামেন্টের সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয়: রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় হল-পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য রাজ্য-বিধানসভাসমূহের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হয়, তবে পূর্বোক্ত ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ ক’রে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য।
4. ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারিত করা যায়?
উত্তর: সংবিধানের ৫৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানভঙ্গের অপরাধে ৬১ নং ধারায় বর্ণিত ‘ইমপিচমেন্ট’ (inpeachment) পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করা যায়। পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব আকারে সংবিধানভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারে। যে-কক্ষে এরূপ অভিযোগ-প্রস্তাব আনীত হবে, সেই কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরিত লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার অন্তত ১৪ দিন পরে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কক্ষে উত্থাপন করা যায়। প্রস্তাবটি সেই কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক ভোটে গৃহীত হলে অপর কক্ষ অভিযোগটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এর পর সেই কক্ষেও প্রস্তাবটি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়।
5. পার্লামেন্টে বিল পাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কী?
উত্তর: পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে হয়। তিনি অর্থবিল ছাড়া অন্য বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন কিংবা না-ও পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পুনর্বিবেচনার পর তাঁর সম্মতির জন্য বিলটি প্রেরিত হলে তাতে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। তা ছাড়া, সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত কোনো বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য প্রেরিত হলে তিনি সেই বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না।
6. রাষ্ট্রপতির ‘ভিটো’ ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: রাজ্য-বিধানসভায় গৃহীত হওয়ার পর যেসব বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে রাজ্যপাল প্রেরণ করেন, সেইসব বিলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন অথবা না-ও পারেন। রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতাকে ‘ভিটো’ ক্ষমতা (‘veto’ power) বলা হয়।
7. ভারতের রাষ্ট্রপতি ক-ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এবং কী কী?
উত্তর: ভারতীয় সংবিধানের অষ্টাদশ অংশ (Part XVIII)-এ রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা-সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত তিন প্রকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন, যথা- [i] জাতীয় জরুরি অবস্থা, [ii] রাজ্যসমূহে সাংবিধানিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা এবং [iii] আর্থিক জরুরি অবস্থা।
8. ভারতের রাষ্ট্রপতি কোন্ অবস্থায় জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন?
উত্তর: সংবিধানের ৩৫২ নং ধারায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরূপ জরুরি অবস্থাকে সাধারণভাবে জাতীয় জরুরি অবস্থা বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ কিংবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র ভারত কিংবা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে কিংবা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি ‘সন্তুষ্ট’ হলে তিনি সমগ্র দেশে কিংবা তার যে-কোনো অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন [৩৫২ (১) ধারা]। তবে বর্তমানে ক্যাবিনেটের লিখিত সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন না [৩৫২ (৩) নং ধারা]। এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণার।
9. ভারতীয় সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে কীভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে?
উত্তর: ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার সময়েও রাষ্ট্রপতি নির্দেশদানের মাধ্যমে সংবিধানের ২০ ও ২১ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করতে পারবেন না।
10. রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলার সপক্ষে দুটি যুক্তি দেখাও।
উত্তর: সংবিধান কর্তৃক শাসনক্ষমতা অর্জন: সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হয়েছে। তিনি ‘নিজে’ কিংবা ‘তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে’ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন [৫৩ (১) নং ধারা]। এর অর্থ, সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে প্রত্যক্ষভাবে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছে, মন্ত্রীসভার হাতে নয়।
মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি তাঁর ইচ্ছাধীন: প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং তাঁর ‘সন্তুষ্টির’ ওপর মন্ত্রীদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে।
11. রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব শাসক বলার সপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
উত্তর: পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা: রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা একথাই প্রমাণ করে যে, সংবিধান-রচয়িতারা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভাকেই প্রকৃত শাসক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
তাত্ত্বিক ক্ষমতা: তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকেই প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করতে বাধ্য। সুতরাং, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই।
12. সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কী কী কার্য সম্পাদন করেন?
উত্তর: লোকসভার নেতা বা নেত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভার অধিবেশন কখন আহূত হবে, কতদিন চলবে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর আলোচনা হবে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তিনি লোকসভায় সরকারি নীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সভায় বিতর্ক চলাকালে কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীই এগিয়ে আসেন। গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো বিল পাস করানোর দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে সভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কেবল লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী হিসেবেই নয়, সমগ্র সভার নেতা বা নেত্রী হিসেবেই তাঁকে কাজ করতে হয়।
13. ক্যাবিনেটের নেতা হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যেসব কার্য সম্পাদন করতে হয়, সেগুলির মধ্যে যে-কোনো দুটি সম্পর্কে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
উত্তর: [i] প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো মন্ত্রীর নীতিগতভাবে বা অন্য কোনো ন কারণে বিরোধ বাধলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। না উদাহরণ হিসেবে সি. ডি. দেশমুখ, এম. সি. চাগলা, মহাবীর ত্যাগী, অশোক মেহেতা, মোহন ধারিয়া প্রমুখের কথা বলা যায়। [ii] প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করেন।
14. ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ‘সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য’ বলার যে-কোনো একটি কারণ লেখো।
উত্তর: সাধারণ কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় মন্ত্রীসভা কিংবা ক্যাবিনেটে কোনোরূপ ভোটাভুটি হয় না। যদি কোনো ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে অন্যান্য মন্ত্রীর মতো প্রধানমন্ত্রীও একটি মাত্র ভোটদানের অধিকারী।
15. ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একনায়ক বলার যে-কোনো একটি কারণ লেখো।
উত্তর: যাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কেবল ‘সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য’ বলে মেনে নিতে সম্মত নন, তাঁদের প্রধানত দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক ও বহুমুখী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ ক’রে তাঁকে একনায়ক বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, [১] তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই তা ক’রে থাকেন।
16. রাজ্যপালের ‘স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সংবিধান রাজ্যপালের হাতে ‘স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা’ (‘Discretionary Powers’) প্রদান করেছে। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে এমন এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতাকে বোঝায়, যা প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ করতে বাধ্য নন। ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩ (১) নং ধারায় বলা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়, সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, সে সম্পর্কে সংবিধানে বিস্তারিতভাবে কোনোকিছু আলোচনা করা হয়নি।
17. রাজ্য-মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে ২০০৩ সালে প্রণীত ৯১-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে কী বলা হয়েছে?
উত্তর: ২০০৩ সালের ৯১-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, কোনো রাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা ওই রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যের ১৫ শতাংশের বেশি হবে না।
18. রাজ্য-বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হিসেবে মুখমন্ত্রীর যে-কোনো দুটি কার্যের উল্লেখ করো।
উত্তর: রাজ্য-বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, প্রয়োজন হলে ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বলা বাহুল্য, রাজ্যপাল সাধারণভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো ওইসব কার্য সম্পাদন করেন। রাজ্য-সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তিনি সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিধানসভায় বিতর্ক চলাকালে কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিল পাস করানোর দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। রাজ্য-মন্ত্রীসভা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য তিনি বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে আইনসভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাঁর কিংবা তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য-মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্য-আইনসভার বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল তাঁর ‘স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা’ প্রয়োগ ক’রে এই পরামর্শ অগ্রাহ্যও করতে পারেন।
19. আমলাতন্ত্রকে কেন স্থায়ী প্রশাসনের অংশ বলা হয়?
উত্তর: রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা হলেন শাসনবিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ।
স্থায়িত্ব হল আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত আমলা বা সরকারি কর্মচারীরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারেন। সাধারণত দুর্নীতিপরায়ণতা, অযোগ্যতা কিংবা চাকরির শর্তাবলি ভঙ্গের প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়া তাঁদের পদচ্যুত করা যায় না।
20. রাজ্য-বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হিসেবে মুখমন্ত্রীর যে-কোনো দুটি কার্যের উল্লেখ করো।
উত্তর: রাজ্য-বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, প্রয়োজন হলে ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বলা বাহুল্য, রাজ্যপাল সাধারণভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো ওইসব কার্য সম্পাদন করেন। রাজ্য-সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তিনি সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিধানসভায় বিতর্ক চলাকালে কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিল পাস করানোর দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। রাজ্য-মন্ত্রীসভা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য তিনি বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে আইনসভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাঁর কিংবা তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য-মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্য-আইনসভার বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল তাঁর ‘স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা’ প্রয়োগ ক’রে এই পরামর্শ অগ্রাহ্যও করতে পারেন।
ভারত সরকারের বিভাগসমূহ : ভারতের শাসন বিভাগ প্রশ্ন উত্তর (Marks : 6)
1. ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির ওপর। একটি বিশ্লেষণমূলক টাকা লেখো।
ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions)
প্রথমে নির্বাচক সংস্থা গঠন ও পরে তিনটি পর্যায়ে ভারতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচক সংস্থা গঠন [Composition of Electoral College]
একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional representation by means of the single transferable vote)-এর নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College) কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। [১] ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের এবং [২] জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-সহ রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের, অর্থাৎ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়।
নির্বাচনের তিনটি পর্যায় [Three Phases of Election]
রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক’রে আলোচনা করা যেতে পারে-
(১) রাজ্য-বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয়: প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। তারপর ভাগফলকে ১,০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয়, তবে দ্বিতীয় ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ ক’রে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভোটদানের সময় বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য একটি ক’রে ভোট দিলেও ভোটগণনার সময় সেই একটি ভোটের মূল্য হিসেবে পূর্বোক্ত ভোটসংখ্যাকেই ধরা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২৮টি অঙ্গরাজ্য ছাড়াও জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি এবং পুদুচেরি (এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। কোনো রাজ্যের ‘জনসংখ্যা’ বলতে সর্বশেষ ‘জনগণনা প্রতিবেদন’ (Census Report)-এ প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বোঝায়। কিন্তু ৮৪তম সংবিধান (সংশোধন) আইন, ২০০১ অনুযায়ী ২০২৬ সালের পরবর্তী সময়ে প্রথম ‘জনগণনা প্রতিবেদন’ প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ‘জনগণনা প্রতিবেদন’-এ উল্লিখিত জনসংখ্যাকেই প্রতিটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হবে।
একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আলোচনা করা যেতে পারে। ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হল ৪,৪৩,১২,০১১ এবং বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ২৯৪। পূর্বোক্ত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটমূল্য যে-পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছিল, তা হল:
২৯৪ ৪,৪৩,১২,০১১ (মোট জনসংখ্যা) (বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা) = ১,৫০,৭২১।
এই ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে, অর্থাৎ যোগ করতে হবে। কারণ, ভাগশেষ ৫০০-র বেশি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভাগশেষ হয়েছে ৭২১। অতএব পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট-মূল্য হল ১৫১। ভোটদানের সময় সদস্যদের প্রত্যেকেই একটি ক’রে ভোট দিলেও ভোট-গণনার সময় সেই একটি ভোটের মূল্য ধরা হয়েছিল ১৫১। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের মোট ভোট-মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১৫১ × ২৯৪ = ৪৪,৩৯৪।
(২) পার্লামেন্টের সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয়: রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় হল-পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য রাজ্য-বিধানসভাসমূহের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হয়, তবে পূর্বোক্ত ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ ক’রে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য।
(৩) একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব: রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির তৃতীয় পর্যায় হল ভোটদান। ভোটদানের ক্ষেত্রে একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে যতজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, প্রত্যেক ভোটদাতা ততগুলি পছন্দ (preference) জানাতে পারবেন। এইভাবে প্রত্যেক ভোটদাতা প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা লিখে তাঁর পছন্দ প্রকাশ করতে পারেন। প্রত্যেক ভোটদাতাকে তাঁর প্রথম পছন্দ অবশ্যই জানাতে হবে; অন্যথায় তাঁর ভোটপত্র বাতিল হয়ে যাবে। এইভাবে ভোটগ্রহণের পর সব প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোটগুলি যোগ করা হয়। তারপর যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ ক’রে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে-সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ‘কোটা’ (‘Quota’) বলা হয়। রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হতে গেলে প্রার্থীকে ‘কোটা’-নির্দিষ্ট ভোট পেতেই হবে। যদি কোনো প্রার্থীই নির্দিষ্ট কোটায় পৌঁছোতে না পারেন, তবে যিনি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন, তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর ভোটপত্রগুলিকে পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট ‘কোটা’ লাভ করতে না-পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থী-বাতিল এবং ভোটপত্রের এরূপ হস্তান্তর চলতে থাকবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র ক’রে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হলে সুপ্রিমকোর্ট তার মীমাংসা করতে পারে।
উদাহরণ [Example]
একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, রাষ্ট্রপতিপদে ক, খ ও গ এই তিনজন প্রার্থী রয়েছেন। পার্লামেন্ট ও রাজ্য-বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের প্রদত্ত মোট বৈধ প্রথম পছন্দের ভোটের মূল্য হল ১০,০০০। এক্ষেত্রে ১০,০০০ ২১ ৫,০০১ হল ‘কোটা। ক, খ ও গ-এর মধ্যে যিনি ৫,০০১ মূল্যের ভোট পাবেন, তিনিই রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হবেন। কিন্তু ধরা যাক, ক পেয়েছেন ৪,৫০০, খ পেয়েছেন ৩,০০০ এবং গ পেয়েছেন ২,৫০০ মূলোর ভোট। এক্ষেত্রে কেউই ‘কোটা’-নির্দিষ্ট ভোট পাননি। তাই একক-হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী গ-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রাপ্ত ২,৫০০ ভোটকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী ক এবং খ-এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ধরা যাক, ২,৫০০ ভোটের মধ্যে ক এবং খ যথাক্রমে ৩০০ ও ২,২০০ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়েছেন। ওই ভোটসংখ্যা যুক্ত হওয়ার ফলে ক-এর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৫০০+ ৩০০ ৪,৮০০ এবং খ-এর দাঁড়াল ৩,০০০ ২,২০০ = ৫,২০০। এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দের ভোট ক বেশি পেলেও দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে খ নির্দিষ্ট ‘কোটা’য় পৌঁছোতে পেরেছেন। তাই খ রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হবে। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভি. ডি. গিরি, সঞ্জীব রেড্ডি ও সি. ডি. দেশমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনের পর দেখা যায় যে, গিরি, রেড্ডি এবং দেশমুখ যথাক্রমে প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন ৪,০১,৫১৫টি, ৩,১৩,৫৪৫টি ও ১,১২,৭৬৯টি। তিনজনের কেউই নির্দিষ্ট ‘কোটা’য় পৌঁছোতে পারেননি। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
আরো পড়ুন : উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্ন উত্তর