ডাকঘর নাটকের প্রশ্ন উত্তর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার বাংলা | Class 12 daakghor natoker long question answer | WBCHSE
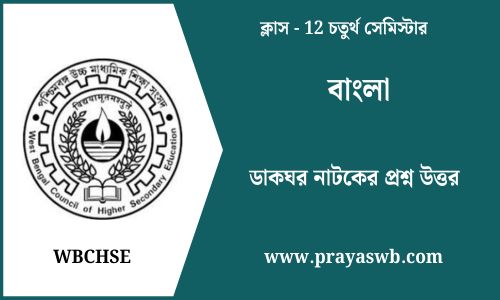
১। “আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক যায়।”- কোন্ প্রসঙ্গে বক্তার এমন উক্তি? এর দ্বারা বক্তার কোন্ অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে? ২+৩
প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ডাকঘর’ নাটকে দেখা যায় মাধব দত্তের পালিত পুত্র বালক অমল গুরুতর অসুস্থ। সে গৃহবন্দি। কবিরাজের নিদান অনুযায়ী ঘরের বাইরে যাওয়া তার বারণ। ওইটুকু ছেলে রোগের সমস্ত দুঃখ চুপ করে সহ্য করে। কারও প্রতি অভিযোগ-অনুযোগ করে না। কিন্তু কবিরাজের দেওয়া তেতো ওষুধ খাবার সময়ই তার যন্ত্রণা প্রকট হয়ে ওঠে। এই কষ্ট স্নেহশীল মাধবের পক্ষে সহ্য করা পীড়াদায়ক। এই প্রসঙ্গেই বক্তা মাধব দত্ত কবিরাজমশাইয়ের প্রতি এমন উক্তি করেছে।
বক্তার অনুভূতি: নিঃসন্তান মাধব দত্ত তার স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কিত ভাইপো অমলকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছে। অমল তাকে ‘পিসেমশায়’ বলে ডাকে। পুত্রতুল্য অমলের কঠিন অসুখে মাধব খুবই বিচলিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অকৃত্রিম বাৎসল্যে, অসীম মায়ায় মাধব বালক অমলকে আগলে রাখে। কিন্তু কবিরাজের আশঙ্কা তাকে আরও দুর্বল করে দেয়। কবিরাজের কড়া বিধান- বালককে কোনোমতেই বাইরে বেরোতে দেওয়া যাবে না। কবিরাজের উপদেশ মেনে মাধব দত্ত কষ্ট বুকে চেপে অমলকে ঘরবন্দি করে রাখে। অন্যান্য ছেলের মতো সে প্রকৃতির সান্নিধ্যে হেসে-খেলে বেড়াতে পারে না এবং পিসেমশায়ের মুখ চেয়ে সবই নীরবে মেনে নেয়। অমল। কিন্তু কবিরাজের দেওয়া কড়া কড়া তেতো ওষুধ খাওয়ার সময় অমলের কষ্ট চোখে দেখা যায় না আর তা প্রত্যক্ষ করেই মাধবের পিতৃমন কেঁদে ওঠে। আলোচ্য অংশে মাধব দত্তের পিতৃহৃদয়ের স্নেহকোমল অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে।
২। “এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ”- এর কারণ হিসেবে বক্তা কী বলেছেন? এই উক্তির মাধ্যমে নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে কোন্ সংকেতের কথা বলতে চেয়েছেন? ২+৩
কারণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটক থেকে গৃহীত আলোচ্য অংশের বক্তা হলেন বালক অমলের চিকিৎসক কবিরাজমশায়। অমলের অসুস্থতা যাতে আরও বেড়ে না যায় সে জন্য তিনি তাকে ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে, শরৎকালের রোদ-হাওয়া গায়ে লাগলে বালকের আরও ক্ষতি হবে। এই বিধানের কারণ হিসেবে তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলেছেন- “অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে” অর্থাৎ এতে মৃগী, জ্বর, কাশি, জন্ডিস রোগের আশঙ্কা আছে। প্রকৃত সংকেত: শরতে বিশ্বস্রষ্টা সংকেত পাঠান উৎসবের-আনন্দের-মুক্তির। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে মাধুর্য। প্রকৃতি সেজে ওঠে অপরূপ সাজে- উজ্জ্বল নীল আকাশ, ভাসমান শুভ্র মেঘের ভেলা, দিগন্তব্যাপী কাশফুলের মেলা গৃহসীমায় আবদ্ধ মানবাত্মাকে এই উন্মুক্ত প্রকৃতি হাতছানি দেয়। সুদূরের পিয়াসিকে অসীমের পথে বেরিয়ে পড়ার ডাক পাঠায়। আর অমল সেই মানবাত্মার প্রতীক, সে সুদূরের পিয়াসি। অপরদিকে, পুথি-পড়া পণ্ডিত কবিরাজ হলেন সীমার প্রতীক। তিনি অমলকে শাস্ত্রের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে চান। তাই শরৎকালের উজ্জ্বল রৌদ্র আর নির্মল বায়ু রক্ষণশীল সীমাবদ্ধ মানুষের কাছে বিষতুল্য মনে হয়। কিন্তু ঋতুরাজ এই রৌদ্র-বাতাসের মাধ্যমে আদতে স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে পড়ার, মুক্তির চরৈবেতির সংকেত পাঠিয়েছেন মানবাত্মা অমলকে। এই নির্মল জল-হাওয়ায় সেজে ওঠা প্রকৃতির মাঝে এটিই অমলের প্রাণের মুক্তির আদর্শ সময়। নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে এই সংকেতের কথাই বলতে চেয়েছেন।
৩। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর।”- কোন্ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? তা বক্তার ‘কঠোর’ বলে মনে হয়েছে কেন? ২+৩
ব্যবস্থাটির পরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্তের পালিত, পুত্র অমল এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক মতে তার চিকিৎসা চলছে। কবিরাজের নির্দেশ হল অমলকে কিছুতেই বাইরে বেরোতে দেওয়া যাবে না কারণ- “এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ” বরং বিষবৎ কিছু কড়া ও তিক্ত ওষুধ তাকে খেতে হবে। কবিরাজ প্রদত্ত এইরূপ কঠোর চিকিৎসা ব্যবস্থার কথাই এখানে বলা হয়েছে। মাধব দত্ত-ই কবিরাজের এই ব্যবস্থাপনাকে ‘কঠোর’ বলে অভিহিত করেছেন।
কঠোর মনে হওয়ার কারণ: মাধব দত্ত নিঃসন্তান। সেই শূন্যতা দূর করতে সে তার স্ত্রীর গ্রামতুতো ভাইপো অমলকে ঘরে এনেছে। অমলের মা-বাবা জীবিত নেই। পিতৃতুল্য পিসেমশায়ের সংসার অনাথ বালকটি অসীম মায়ায় ভরিয়ে তোলে। অমলের অসুস্থতায় মাধব দত্ত তাই খুবই উদ্বিগ্ন। ছেলেটির প্রতি তার প্রবল স্নেহ তাই কবিরাজের বিধান মেনে অমলের ‘শুভানুধ্যায়ী’ পিসেমশায় তাকে ঘরবন্দি করে রাখে, কড়া-তেতো ওষুধ খেতে বাধ্য করে। এমনকি শরতের রোদে সেজে ওঠা প্রকৃতির উৎসবেও সামিল হতে পারে না অমল। অতএব এই পরিস্থিতিতে মাধব দত্তের মনে হয় চিকিৎসার নামে ছেলেটির উপর যেন এক প্রকার অত্যাচার চলছে। ‘চিকিৎসা’ সাধারণত মানুষের রোগের উপশম ঘটায়, কিন্তু কবিরাজের চিকিৎসায় অমলের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করে মাধব দত্তের তার চিকিৎসার ব্যবস্থাপনাকে ‘কঠোর’ বলে মনে হয়েছে।
৪। ‘ডাকঘর’ নাটকে অমলকে কবিরাজ বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছিলেন কেন? অমলের সঙ্গে ছেলের দলের কথোপকথন নিজের ভাষায় লেখো। ২+৩
অমলকে বেরোতে নিষেধ করার কারণ: ‘ডাকঘর’ নাটকে পুথিসর্বস্ব ‘পণ্ডিত’ কবিরাজ পুথি পড়ে জানতে পেরেছেন যে বাইরে বেরোলে অমলের অসুখ বাড়বে তাই তিনি অমলকে বাইরে বেরোতে নিষেধ করেন। শাস্ত্রের বিধানের বাইরে তিনি আর কিছুই বোঝেন না। শাস্ত্রে লেখা আছে পিত্ত-জ্বর-কফ-বায়ু সংক্রান্ত রোগে বাইরের জল-আলো-বাতাস বিষের মতো ক্ষতিকর তাই বাইরে তো দূর, ঘরের উঠোনে যাওয়াও অমলের মানা। অমলের এই বাইরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে আদতে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তা বোঝার ক্ষমতা কবিরাজের নেই। তাঁর কাছে মুক্তিচেতনা, চিরাচরিত নিয়মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে চাওয়া একপ্রকার মারণব্যাধি। তাই নিয়ম, শাস্ত্র, প্রথার রক্ষক কবিরাজ মুক্ত প্রাণের প্রতীক অমলকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন।
ছেলের দলের সঙ্গে কথোপকথন: বাইরে যাওয়ার জন্য অমলের মন উচাটন। সে জানালার ধারে বসে পথচারীদের ডেকে ডেকে গল্প করে। দূরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্যাখে। এইভাবে সে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। সেই পথ দিয়েই খেলতে যাচ্ছিল ছোটো ছোটো ছেলেরা। অমল সেই ছেলের দলকে ডেকে ভাব করে। ছেলেরা জানায় সারাদিন তারা ‘চাষ খেলা’ খেলবে। তারপর, সন্ধ্যায় তারা ঘরে ফিরবে। লাঠি তাদের লাঙল আর দুজন দুই গোরু হবে। অমলকে তারা বাইরে এসে তাদের সঙ্গে খেলতে বললে অমল কবিরাজের নিষেধের কথা তাদের জানায় এবং অনুরোধ করে রাস্তায় তার জানালার সামনেই যেন তারা কিছুক্ষণ খেলা করে। ঘর ভরতি খেলনা অমলের কিন্তু ঘরের মধ্যে একা-একা খেলতে তার ভালো লাগে না। বরং ছেলের দলের কাছে খেলার সামগ্রী না থাকলেও তাদের ‘মিছিমিছি’ চাষ খেলা অনেক বেশি উপভোগ্য, কারণ তাদের খেলার সঙ্গী আছে, উপযুক্ত পরিবেশ আছে। তাই অমল-জটাই বুড়ি, জাহাজ, সেপাই- তার সুন্দর সব খেলনা ছেলের দলকে দিয়ে দেয়। অমল তার দরজার সামনে রোজ সকালে কিছুক্ষণ ধরে খেলে যাওয়ার অনুরোধ করে ছেলের দলকে, অমলের এমন সুন্দর সব খেলনা দেখে বিস্মিত ছেলের দল রোজ তার জানালার কাছে এসে খেলার প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যায়। ছেলেরা সেপাইগুলোকে সাজিয়ে শরকাঠিকে বন্দুক বানিয়ে লড়াই-লড়াই খেলে। সমবয়সিদের খেলার আনন্দ-দৃশ্য দেখতে দেখতে শারীরিক ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে যায় অমলের।
৫। “তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।”- কে, কার প্রতি এমন মন্তব্য করেছে? এমন মন্তব্যের কারণ কী? ২+৩
যে, যাকে বলেছে: আলোচ্য নাটকে ঠাকুরদার প্রবেশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই অমলের পিসেমশায় মাধব দত্ত তাকে ‘ছেলে খেপাবার সদ্দার’ বলে অভিহিত করেছে।
কারণ: রাজার আগমনের বহুপূর্বেই ‘ডাকঘর’ নাটকে ‘ঠাকুরদা’-র প্রবেশ ঘটে। ঠাকুরদা প্রথমে আসে নিজ পরিচয়ে, পরে আসে ফকিরের বেশে- তবে দু’বারই সে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। ঠাকুরদা যেন রাজারই প্রেরিত মুক্তির দূত- ছেলেদের বন্ধনমুক্তি ঘটার পূর্বে তাদের মনে মুক্তির বীজ বপন করাই যেন তার কাজ। যে কাজ শরতের হাওয়া আর রোদ করতে পারে, ঠাকুরদাও যেন সেই কাজেই ব্রতী হয়েছে।
বিপরীতে, মাধব দত্তের কাছে মুক্তি, স্বাধীনতা এই সব কিছুই অমঙ্গলসূচক। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার ডাকে সারা দেওয়া তার কাছে ‘খ্যাপামি’। আর প্রকৃতির এই ডাককেই চিনতে শেখায় ঠাকুরদা। বন্ধ প্রাণকে মুক্ত করে সে। তাই অমলেরও মুক্তি ঘটে গেলে মানবিক মায়ার জাল দিয়ে মাধব দত্ত তাকে আর ছুঁতে পারবে না। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাবে অমল- সেই ভয় থেকেই পার্থিব বাধার স্বরূপ মাধব দত্ত, মুক্ত প্রাণের দূত ঠাকুরদাকে ‘ছেলে খেপাবার সদ্দার’ বলে ভর্ৎসনা করতে চেয়েছে।
৬। “তাই তোমাকে ভয় করি।”- বক্তা কাকে, কেন ভয় করে? তার ভয় পাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিচার করো। ২+৩
ভয়ের কারণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে ভয় করে। কারণ ঠাকুরদা যে ‘ছেলে খেপাবার সদ্দার’। ছোটো ছোটো ছেলেকে ঘরের বাইরে এনে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে খেলা করানোই তার কাজ। পুথিগত বিদ্যার বাইরে প্রকৃতির পাঠ দেওয়া, অনাবশ্যক শৃঙ্খলিত জীবনের বাইরে শিশু-কিশোর মনে মুক্তির আনন্দ জাগিয়ে তোলাই ঠাকুরদার কাজ। কিন্তু মাধবের পালিতপুত্র বালক অমল যে অসুস্থ, তার বাইরে বেরোনোয় কবিরাজের নিষেধাজ্ঞা আছে। ঠাকুরদা যদি অমলকেও খেপিয়ে তুলে বাইরে নিয়ে চলে যায়! তাই তাকে ভয় করে মাধব।
ভয় পাওয়ার যৌক্তিকতা: ঠাকুরদা আসলে মুক্তির দূত। বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধি। এই উদার সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে সে শিশুদের পরিচয় ঘটায়। সীমার বাঁধন থেকে বের করে বিশ্বনিখিলের অসীম মাধুর্যের আস্বাদ দিতে চায়। জীর্ণ সংসার পেরিয়ে প্রকৃত মুক্তির পথ বলে দেয়। কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তা বোঝে না, তাদের মন লাভক্ষতির হিসেবে আবদ্ধ। ছোটোদের মন সাংসারিক আবিলতা থেকে মুক্ত। তাই ঠাকুরদার কারবার ছোটো ছেলেদের নিয়েই। ছোটোরা ঈশ্বরের বন্ধু আর ঠাকুরদা যেন সেই রাজারূপী ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। ঈশ্বরের সংকেত নিষ্পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। তাই ছেলেরা তাকে ভয় না করলেও একজন বৈষয়িক সাধারণ গৃহস্থ হিসেবে, অসুস্থ পুত্রের পিতা হিসেবে সর্বোপরি, পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপী মাধব দত্তের ঠাকুরদাকে ভয় পাওয়া যুক্তিযুক্ত।
৭। “তাই তোমাকে ভয় করি।”- বক্তা কাকে, কী কারণে ভয় করে তা বিশদে বুঝিয়ে দাও। ৫
ব্যাখ্যা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকের প্রথম দৃশ্যে মাধব দত্ত, ঠাকুরদাকে একথা বলেছে। ঠাকুরদা হল ‘ছেলে’ খেপাবার সদ্দার।’ ছোটো ছেলেদের ঘরের বাইরে বের করে উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গী করতে চায় সে। চিরাচরিত প্রচলিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপনের বাইরে এনে ঠাকুরদা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করায়। তাদের প্রকৃতির পাঠ শেখায়। খেলাধুলা-আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনকে অন্যভাবে চিনতে সাহায্য করে এবং ছোটোদের কল্পনাকে উসকে দেয়। পুথিগত শিক্ষার বাইরে যে প্রকৃতির এক সীমাহীন পাঠশালা আছে তা সাধারণ গৃহস্থরা জানে না। তাই তারা শিশুদের ধরাবাঁধা জ্ঞানের সীমায় আটকে রাখতে চায়। ঠাকুরদা সমস্ত অনুশাসনের বেড়া ভেঙে শিশুদের মনে অনাবিল মুক্তির স্বাদ এনে দেয়।
নিঃসন্তান মাধব দত্তের একমাত্র পোষ্যপুত্র অমল অসুস্থ। বাইরে বের হলে তার অসুখ বেড়ে যাবে। কবিরাজ বলেছেন ‘তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যেরকম প্রকৃপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই।’ তাই তাকে শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে রক্ষা করার জন্য ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। ছেলে খ্যাপাবার সর্দার ঠাকুরদা যদি অমলকে বাইরে বের হওয়ার উৎসাহ দেয়- এই ভেবে মাধব ভয় পায়।
৮। “আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল।”- বক্তার স্ত্রী পোষ্যপুত্র নেবার জন্য খেপে উঠেছিল কেন? কী কারণে বক্তা প্রথমে পোষ্যপুত্র নিতে রাজি ছিল না? ২+৩
খেপে ওঠার বিবরণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটক থেকে উদ্ধৃত আলোচ্য উক্তিটির বক্তা মাধব দত্ত। দত্ত-দম্পতি ছিল নিঃসন্তান, সন্তানের অভাবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার ছিল অসম্পূর্ণ। মাধব তাও বাইরের কাজে-কর্মে সন্তানের অভাববোধ কিছুটা ভুলে থাকতে পারত। কিন্তু তার স্ত্রীকে সারাদিন ঘরের মধ্যে একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হত। সন্তানহীনতার বেদনা তাকে সর্বক্ষণ বিচলিত করত। তাই সন্তানপ্রাপ্তির সুখানুভূতি পেতেই মাধবের স্ত্রী পোষ্যপুত্র নেওয়ার জন্য খেপে উঠেছিল।
রাজি না হওয়ার কারণ: মাধব দত্ত বৈষয়িক মানুষ। তার জীবন হিসাবনিকাশ করে চলে। অনেক কষ্টে টাকা উপার্জন করে সে। বহু পরিশ্রম করে যে ধন উপার্জন করেছে সে, সেই ধন সঞ্চয় করতেও সে জানে। আর পোষ্যপুত্র নেওয়া মানে পরের ছেলেকে ঘরে আনা। সে ছেলে কেমন হবে তার জানা নেই। তাই মাধবের মনে ভয় ছিল, ‘কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে’। অর্থাৎ, এখান থেকেই বোঝা যায় নিঃসন্তান মাধব দত্তের সন্তান দত্তক নেওয়ার নেপথ্যে কাজ করেছিল সন্তানের সুখানুভূতি নয় বরং উত্তরাধিকার চিন্তাই। আর সেই উত্তরাধিকারী হিসেবে পোষ্যপুত্র উপযুক্ত হবে কি না এবং তা না হলে মাধব দত্তের সম্পত্তি অপাত্রে দান করা হবে, এই আশঙ্কা এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতাই তাকে পোষ্যপুত্র নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।
৯। “এর জন্যে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।”- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৫
ব্যাখ্যা: ‘ডাকঘর’ নাটক থেকে গৃহীত প্রশ্নোদ্ভূত উক্তিটি মাধব দত্তের কথার সাপেক্ষে তারই উদ্দেশে বলেছে, ঠাকুরদা। মাধব দত্ত বিষয়ী লোক, সে নিঃসন্তান। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার বিষয়ে নিমরাজি ছিল সে কারণ তার কষ্টে অর্জিত টাকা অসৎ হাতে পড়ে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল তার। কিন্তু অমল সবার থেকে আলাদা, সরল-মুক্তপ্রাণের আধার তাই তাকে ঘরে নিয়ে আসার পরেই মাধব দত্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আসে। সে অমলের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে, তাকে ভালোবেসে মাধব দত্তের অবদমিত পিতৃসত্তা জেগে ওঠে। তার জমাখরচের হিসাব তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে।
অমল অসুস্থ। তাকে সুস্থ করে তুলতে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে মাধব দত্ত সদা তৎপর। কবিরাজের নির্দেশ মেনে যা যা করণীয় সবই সে করে। নিত্য চিকিৎসার খরচও তার কাছে নগণ্য বলে মনে হয়। অমলকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারলেই যেন মাধব দত্তের শান্তি। আসলে মুক্ত মানবাত্মার সারল্যের স্পর্শে বিষয়ী মাধব দত্তের মনেও বন্ধনমুক্তির হাওয়া লেগেছিল। পার্থিব হিসাবনিকাশের ভার অমলের দ্বারা লাঘব করতে চেয়েছিল সেও। উপরন্তু, অপত্য স্নেহের বশবর্তী হয়ে অমলের জন্য ব্যয় করাকে ‘পরম সৌভাগ্য’ বলে মনে হয় তার। উপার্জন জমিয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি তাই নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন মনে হয় মাধব দত্তের বরং অমলের জন্য খরচ করলে সেই ব্যয় করা অর্থ প্রকৃত কাজে লাগে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে অমলকে নিজের কাছে রেখে দিতে চায় সে। মাধব দত্তের বৈষয়িক চিন্তাও, অমলকে ঘিরেই এরূপ প্রবর্তিত হতে দেখে ঠাকুরদা প্রশ্নোদ্ভূত মন্তব্যটি করে।
১০। “একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো” শরতের বোদ-হাওয়া কী অর্থে ভয়ানক? বক্তার এ কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি ব্যাখ্যা করো। ৩+২
প্রকৃত অর্থ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকে মাধব দত্ত, ঠাকুরদাকে বলে- “ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা- তাই তোমাকে ভয় করি।” এ কথার প্রেক্ষিতেই ঠাকুরদা প্রশ্নোদ্ভূত উক্তিটি করেছে। রুগ্ধ বালক অমলের বাইরে বেরোনোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কবিরাজ বলেছিলেন, “এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ”। এরই সূত্র ধরে কিছুটা কৌতুক ও কিছুটা শ্লেষ মিশিয়ে ঠাকুরদা কবিরাজের কথারই যেন পুনরাবৃত্তি করে। শাস্ত্র পড়ে পুথিগত জ্ঞান থেকে কবিরাজের মনে হয়েছে শরতের রোদ -হাওয়া অমলের স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে। কারণ শরতই হল প্রকৃতির উৎসবের আনন্দে সেজে ওঠার সময় আর এই সময়ই হল প্রাণের মুক্তির জন্য আদর্শ। কিন্তু মুক্তি, কবিরাজের কাছে ব্যাধির মতো। তাই তিনি শরতের রোদ-হাওয়াকে উপেক্ষা করে অমলকে ঘরে বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। অপরদিকে, ছোটোদের ঘরের বাইরে বার করাই ঠাকুরদার খেলা। তাই ছাপোষা গৃহস্থের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদাই ভয়ানক। কারণ সে ছোটোদের গণ্ডিবদ্ধ বাঁধাধরা জীবনপ্রবাহ বিঘ্নিত করে তাদের মুক্তির নেশায় খেপিয়ে তোলে।
অন্তর্নিহিত অর্থ: বড়োদের অনুশাসনে অত্যধিক ঘরকুনো হয়ে থাক শিশুরা, তা একেবারেই পছন্দ নয় ঠাকুরদার। চারদেয়ালে বন্দি থেকে কেবল রাশি রাশি পুথি পড়লেই জীবনকে, পৃথিবীকে চেনা যায় না। তাকে জানতে হলে বাইরে বেরোতে হয়, উদার প্রকৃতির ডাক শুনতে হয়। শরতের রৌদ্র-হাওয়া যেমন, তেমনি প্রকৃতির সমস্ত ঋতুর রঙ্গশালার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করতে হয়। প্রকৃতিপাঠের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত বহির্বিশ্বের সঙ্গে শিশুমনের সংযোগ ঘটানোই ঠাকুরদার কাজ। এভাবে যথার্থ জ্ঞানের ও মনের বিকাশ ঘটে। বেড়াভাঙার এই খেলাকে হিসাবি লোক ‘উচ্ছন্নে যাওয়া’ ভেবে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ঘরে ধরে রাখার খেলাও ঠাকুরদা জানে।
১১। “আমি যদি কাঠবেড়ালি হতুম তবে বেশ হত।”- কার, কখন এরকম মনে হয়েছে? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তার মনের কোন্ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে লেখো।
যার, যখন এরকম মনে হয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকের মুখ্য চরিত্র অমল। সে অল্পবয়সি একটি ছেলে। তার মা-বাবা গত হয়েছে। দূর সম্পর্কের পিসেমশায় মাধব দত্তের বাড়িতে তাদের পোষ্যপুত্ররূপে অমল প্রতিপালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ভারি অসুখ। তাই কবিরাজ তাকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করেছেন। ঘরের ভিতরটা আর ঘরের জানালাখানিই তাই ছোট্ট অমলের পৃথিবী। ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভিতরেও অন্যত্র কোথাও যাওয়ারও অনুমতি নেই অমলের। তাই ঘরের ভিতরে বসেই সে দ্যাখে, বাড়ির উঠোনে বসে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। সেখানে ভাঙা ডালের খুদ পড়ে থাকে। অমল দেখতে পায় ‘খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস-কুটুস করে খাচ্ছে’। সেই উঠোনটাতে সে যেতে চায়। কিন্তু পিসেমশায় তাকে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় অমলের মনে হয়েছে সে যদি কাঠবেড়ালি হত তবে ভালো হত।
মানসিক প্রবণতা: কাঠবেড়ালি প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা জীব, মুক্তির প্রতীক। অমলও যদি কাঠবেড়ালি হত তবে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারত। উঠোনে বসে পিসিমার ভাঙা ডালের খুদগুলি খেত। কোনো নিষেধ-বাধা থাকত না তার। অর্থাৎ আলোচ্য উক্তিতে অমলের সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। গৃহবন্দি জীবন থেকে বাইরে বেরিয়ে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সে মিশতে চায়। বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা, সুদূরের আহ্বান, প্রকৃতির বুকে মুক্ত জীবনের আনন্দ সে উপভোগ করতে চায় কাঠবেড়ালির মতোই। অমলের বিশেষ নয়, সাধারণ হতে হচ্ছে করে। যাতে সে সমস্ত এড়িয়ে চলে যেতে পারে প্রকৃতির কাছাকাছি। নিয়মের বেড়াজালে নয়, কাঠবেড়ালির মতো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকাতেই তার ইচ্ছেপূরণ হবে। অর্থাৎ অমলের কাঠবেড়ালি হতে চাওয়া তার মুক্ত মনের স্বাধীনতার প্রবণতাকেই প্রকাশ করে।
১২। “না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না”- কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? বক্তা পণ্ডিত হতে চায় না কেন? ২+৩
প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ডাকঘর’ নাটকে কবিরাজ, বালক অমলকে ঘরের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন। সে এমনিতেই রুগ্ধ, দুর্বল। বাইরে বেরোলে তার অসুখ বাড়বে। কিন্তু কবিরাজ সে কথা জানলেন কী করে- অমলের এমন প্রশ্নের উত্তরে পিসেমশায় বলেন, কবিরাজ অনেক পুথি পড়েছেন বলে তিনি পণ্ডিত, তাই তিনি সব জানেন। পন্ডিতরা বাইরে বের হয় না। তাঁরা ঘরে বসে রাতদিন পুথি পড়েই সব জানতে পারে। পিসেমশায় এই প্রসঙ্গে বলে- “অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে-বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়বে-সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।”- এই কথা শুনেই আঁতকে উঠে অমল উদ্ধৃত উক্তিটি করেছে।
পণ্ডিত হতে না চাওয়ার কারণ: অমল সংবেদনশীল কল্পনাপ্রবণ বালক। বন্দি জীবন তার পছন্দ নয়। পুথিগত জ্ঞানের চেয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যই তার ভালো লাগে। উন্মুক্ত প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব সে নিবিড়ভাবে পেতে চায়। পুথি-পড়া ‘পণ্ডিত’ কবিরাজ তাকে ঘরে বেঁধে রেখেছেন। বাইরে বেরোনোর জন্য সে ব্যাকুল। সে সুদূরের পিয়াসি।
অন্যদিকে, পন্ডিতেরা সবজান্তা। তারা ভাবে পুথি পড়েই সব জানা যায় তাই তাঁরা মুখ বুজে কেবল পুথি পড়ে, বাইরের দিকে তাকিয়েও দ্যাখে না কিন্তু অমল বিশ্বপ্রকৃতির কাছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়েই দাঁড়াতে চায়, প্রকৃতির মধ্যে নিরলস খোঁজ চালিয়েই পেতে চায় বিশ্বাত্মার সন্ধান। তাই ‘সবজান্তা’ পণ্ডিত হয়ে তার কাজ নেই বরং সাধারণ কিছু হওয়ার প্রতিই তার ঝোঁক বেশি। অমল তাই ছকভাঙা কিছু হতে চায়, যেমন-কাঠবেড়ালি বা দইওয়ালা। যা হলে প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা যাবে, মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো যাবে তাই-ই হবে সে। রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের ‘বাউল’ কবিতায় যেন অমলের এই চাহিদাই আরও খোলসা হয়-
“এ-সব পণ্ডিতেরই হাতে আমায় কেন সবাই মারো? ভুলিয়ে দিয়ে পড়া আমায় শেখাও সুরে-গড়া তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।”
– অমল তাই পণ্ডিত হবে না। চিরাচরিত পুথি-শাস্ত্রের আগল ভেঙে সে খুঁজে নেবে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশ, পালিয়ে যাওয়ার মাঠ, বদ্ধ জীবনের ওপারের মুক্তি।
১৩। “পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ”- প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। উক্তিটি ব্যাখ্যা করে বক্তার মানসিকতার পরিচয় দাও। ২+৩
প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ডাকঘর’ নাটকে অমলের পিসেমশায় মাধব দত্ত এই উক্তিটি করেছে। অসুস্থতার কারণে গৃহবন্দি অমল জানালার ধারে বসে থাকে। কবিরাজের নিদানে তার বাইরে বেরোনো মানা। জানালা দিয়ে দূরের পাহাড় দেখা যায়, অমলের মন চলে যায় সেদিক পানেই। পিসেমশায়কে সে বলে, “আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।”- তার এ কথা শুনেই পিসেমশায় মাধব দত্ত, অমলকে বাইরে যাওয়ার ভাবনা থেকে বিরত করতে আলোচ্য উক্তিটি করে।
ব্যাখ্যা: মাধব দত্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। অর্থ রোজগার, হিসাবনিকাশ, সঞ্চয় ইত্যাদি স্থূল সাংসারিক বিষয় নিয়েই সে থাকে। অমল তার পোষ্যপুত্র। বালকের মনের খবর মাধব রাখে না। প্রকৃতিকে সে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাভাবিক উপকরণ হিসেবেই দেখে। নিসর্গের অন্তরে নিহিত যে সূক্ষ্ম আহ্বান, তা উপলব্ধি করার শক্তি মাধবের নেই। তাই পাহাড়কে তার মনে হয় নিষেধের বেড়া। তবে অমলের ভাবুক মন তা মানতে চায় না। তার মনে হয় “পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে।” অর্থাৎ, অমলের কাছে পাহাড় কোনো বেড়াজাল নয়, তা হল প্রকৃতির হাতছানি। পৃথিবীর ভাষা যেন প্রকৃতির নানা উপকরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। অমলের সরল মন সে ডাক শুনতে পায় তাই সে পাহাড় পেরিয়ে চলে যেতে চায়।
কিন্তু, বক্তা মাধবের মন সংসার-সীমায় আবদ্ধ। তার স্থূল বিষয়বুদ্ধি। স্বাভাবিকভাবেই মনে করে পাহাড়ের বিশালতা যেন বলতে চায় ‘পেরিয়ে যাওয়া বারণ’। আলোচ্য উক্তি থেকে বক্তার এমনই সীমাবদ্ধ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।
১৪। “আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।” কোন্ প্রসঙ্গে বক্তার এই উক্তি? খ্যাপা লোকটি সম্পর্কে বক্তা যা বলেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো। ২+৩
প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকে কঠিন অসুখে গৃহবন্দি বালক অমল বাইরে বেরোতে চায়, পৃথিবীতে যা আছে সব দেখে বেড়াতে চায়। জানালা দিয়ে দূরে পাহাড় দেখে তার মনে হয় পৃথিবীটা কথা বলতে পারে না বলে অমনি করে আকাশে হাত তুলে তাকে ডাকছে। ঘরে বসে অনেকেই প্রকৃতির সেই ডাক শুনতে পায়, যেমন পায় অমল। তবে পণ্ডিতরা কি সে ডাক শুনতে পায়? পিসেমশায় মাধব দত্ত বলে, পণ্ডিতরা শুনতে চায় না, কারণ তারা অমলের মতো খ্যাপা নয়। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অমল উদ্ধৃত উক্তিটি করেছে।
খ্যাপা লোকটির বর্ণনা: অমলের ঘর ছেড়ে বেরোনোর ইচ্ছে মাধব দত্তের খ্যাপামি বলে মনে হয়, অমলকে তাই সে খ্যাপা বলে। অমল নিজেও তাই মনে করে- তবু তার সেই মুক্ত হওয়ার ‘খ্যাপামি’ পিছু ছাড়ে না। অমল দরজায় দাঁড়িয়ে একদিন দেখেছিল মাঠের পথ দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকে হেঁটে চলেছে একটি লোক। সে বুঝি অমলের মতোই বাহির-প্রিয়, কেবলই বেরিয়ে পড়তে চায়, দেখে বেড়াতে চায়। সেই পথিকের কাঁধে যে বাঁশের লাঠি ছিল তাতে পুঁটুলি বাঁধা আর বাঁ হাতে ছিল ঘটি। পায়ে পুরোনো নাগরা জুতো। পথিক জানে না সে কোথায় যাবে। সে কাজ খুঁজতে বেরিয়েছিল। অমলও বড়ো হয়ে অমনভাবে কাজ খুঁজতে বেরোতে চায়। পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া লোকটি ঝরনার কাছে দাঁড়ায়। ডুমুর গাছের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে ঝরনা, সেখানে পুঁটুলি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে পা ডোবায় সে। কিছুটা ছাতু মেখে খায়। তারপর ঝরনার জল পেরিয়ে চলে যায়। অমলের মনও লোকটির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পেরিয়ে চলে যায়। অমলের ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছারই এক কায়িক প্রতিফলন ঘটে এই খ্যাপা লোকটির দ্বারা, সে যেন অমলের মুক্তিরই প্রতিচ্ছবি।
আরো পড়ুন : হলুদ পোড়া গল্পের বড়ো প্রশ্ন উত্তর