গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও
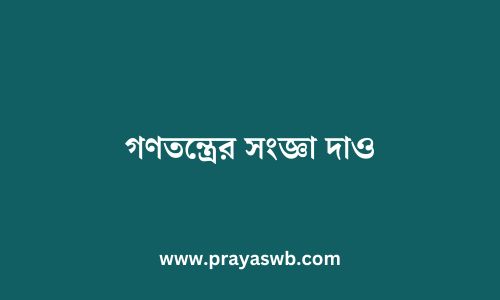
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মোবট (Mobott) মন্তব্য করেছিলেন যে, “…the most elusive and ambiguous of all political terms.” আবার ডেভিড হেল্ড (David Held)-এর মতে, গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণা আজও জটিল ও বিতর্কিত (The idea of Democracy remains complex and contested.)। গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) মনে করতেন, যেখানে গুণগত বিচারে সরকারি কর্মচারীরা নিযুক্ত হন এবং আইনগতভাবে সকলেই সমান, সেখানে প্রকৃত সরকার হল গণতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টট্ল সরকারের একটি বিকৃত রূপ হিসেবে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অন্যদিকে, চতুর্দশ লুই (Louis XIV) গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।
আবার ইতালির স্বৈরাচারী শাসক বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini) স্বৈরাচারিতার মধ্য দিয়েই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করতেন। অন্যদিকে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নার্ড ক্রিক (Barnard Crick) তাঁর ‘In Defence of Politics’ গ্রন্থে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, “সরকার সম্পর্কিত আলোচনার জগতে গণতন্ত্র সম্ভবত সবচেয়ে বাছবিচারহীন শব্দ” (“Democracy is perhaps the most promiscuous word in the world of public affairs”)। অধ্যাপক গিডিংস (Gidings)-এর মতে, “A democracy may either be a form of government, a form of state, a form of society or a combination of all the three.” গণতন্ত্রকে মোটামুটিপক্ষে দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা-ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে।
(1) ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র
বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের সঠিক স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলে। অর্থাৎ এটি এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, একটি বিশেষ শাসনতন্ত্র এবং একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান।
এ প্রসঙ্গে সি ডি বার্নস (CD Burns) মন্তব্য করেছিলেন, একটি আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র হল এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি মানুষ সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হলেও এক অর্থে তারা অভিন্ন সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তিই সমাজের অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ (“Democracy, as an ideal, is a society not of similar person but of equal, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole.”)
আবার, যে সমাজব্যবস্থা সাম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এরূপ রাষ্ট্রে জনগণ হল চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। যখন জাতি, বর্ণ, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন নির্বিশেষে সকলেই রাষ্ট্রপরিচালনার কার্যে অংশগ্রহণ করে, তখন তাকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা যায়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ-কে অনুসরণ করে বলা যায়, “গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে শ্রেণিই নেতৃত্ব করুক না কেন, জনগণই হল চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎসস্থল।”
বার্নস, উইলোবি, হবহাউস, হেনরি মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাম্য, ন্যায়, সত্য ও জনকল্যাণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ল্যাস্কি মন্তব্য করেছিলেন, যে সমাজব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ বা শোষণের কোনো স্থান নেই এবং যেখানে কোনোরূপ ধনবৈষম্য থাকে না, সেই সমাজই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ।
(2) সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র
সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে মূলত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার (Democratic Government)-কেই বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে অনেকেই জনগণের শাসনকে বুঝিয়েছেন। জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকেই এঁনারা গণতন্ত্র বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। তবে, প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্রায়তন ও স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট নগররাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হলেও বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
এর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর গেটিসবার্গ বক্তৃতায় গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ নির্দেশ করে যা বলেছিলেন, তা আজও গণতন্ত্রের সুপ্রচলিত সংজ্ঞা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তাঁর ভাষায়, “… জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে না… (“that Government of the people, by the people, for the people shall not perish from earth.”)। তাঁর এই উক্তিটিলিঙ্কন-এর সূত্র (Lincoln’s Formula) নামে পরিচিত। তবে লিঙ্কন প্রদত্ত গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান। সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-
- জনগণের শাসন: সরকারের প্রতি জনগণের নিঃশর্ত বা স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদর্শনকেই অনেকে ‘জনগণের শাসন’ (‘Government of the people’) বলে বোঝাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুইজি (Sweezy) জনগণের শাসন বলতে দুটি দিকের কথা নির্দেশ করেছেন- শাসনব্যবস্থার উৎসস্থল হল জনগণ এবং সরকার এবং জনগণ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।
- জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা: যখন কোনো রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন সেই শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Government by the people) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিলিও এমনটাই মনে করেছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, একটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক কখনই রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। নাবালক, মানসিক ভারসাম্যহীন, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি দেশবাসী শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। এ প্রসঙ্গে ডাইসি (Dicey) বলেছিলেন, যে শাসনব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে একটি গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে, তাকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)-এর মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা দেশের প্রতিটি নাগরিকের হাতে অর্পিত থাকলেও, বাস্তবে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয় (“A Government in which the will of the majority of qualified citizens rules…”)। আবার ডাইসিও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেছেন, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাসনপরিচালনায় অংশগ্রহণ করলে সেই শাসনতন্ত্রই হবে গণতন্ত্র (“A form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the nation”.) I রাষ্ট্রবিজ্ঞানী র্যাফেল (DD Raphael) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, “Democracy in practice has to mean following the view of the majority.”
- জনগণের জন্য শাসনব্যবস্থা: যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার জনগণের স্বার্থে কার্যপরিচালনা করে, তাকে ‘জনগণের জন্য শাসনব্যবস্থা’ বলা হয়। এরূপ সরকার মূলত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে না। সমাজস্থ সকল জনসাধারণের চূড়ান্ত কল্যাণসাধনই এই ধরনের সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।
(3) সাম্প্রতিক সংজ্ঞা
আধুনিককালে রবার্ট ডাল (Robert Dahl), জি সি ফিল্ড (G C Field), কার্ল পপার (Karl Popper), জোসেফ শ্যুমপিটার (Joseph Schumpeter) জন প্লামেনাজ (John Plamenatz) প্রমুখ রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ গণতন্ত্রের সর্বাধুনিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে রবার্ট ডাল গণতন্ত্রকে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর (Interest Groups) মধ্যেকার আপোস- মীমাংসার একটি পদ্ধতি বলে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ – শ্যুমপিটার মনে করেন, গণতন্ত্র হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক প্রতিনিধি নির্বাচনের এক ব্যবস্থা। আবার জি সি ফিল্ড-এর মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল সেই শাসনব্যবস্থা, যেখানে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।
জন – প্লামেনাজও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন, শাসিত শ্রেণিকর্তৃক – স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থাই হল গণতন্ত্র। অন্যদিকে, কার্ল পপার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শাসনকে গণতন্ত্র বলে মেনে নিতে চাননি। তিনি মনে করতেন গণতন্ত্র হল এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি, যার মাধ্যমে জনগণ শাসকশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতাচ্যুতা করতে পারে। তবে, সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় গণতন্ত্রের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ প্রসঙ্গে লিপসন (Lipson) বলেছিলেন, “When one considers how great has been the extent of democracy is space, time and culture it becomes obvious that no two look exactly alike.”।
আরও পড়ুন – নুন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর