একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মোট 40 নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। এই 40 নম্বরের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন রূপ অধ্যায় থেকে মোট 8 নম্বর আসবে। পরীক্ষায় এখান থেকে একটি বড়ো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। বড়ো প্রশ্নের ধরন হবে গোটা 6 নম্বরের এবং ছোটো প্রশ্নের ধরন হবে গোটা ২ নম্বরের। আজকের এই প্রশ্নোত্তর পর্বে একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমিষ্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায় থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরসহ তুলে ধরা হল।
সরকারের বিভিন্ন রূপ প্রশ্ন উত্তর Class 11 Second Semester
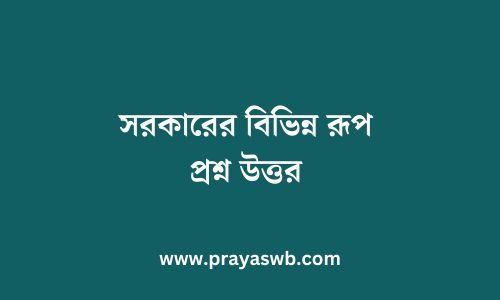
পরোক্ষ গণতন্ত্রের দোষসমূহ আলোচনা করো।
(1) পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সরকার
পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।
(2) জনস্বার্থের বিরোধী
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচকদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারে বলে মনে করা হয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে, তা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিফলিত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেছেন।
(3) জনগণের সীমিত নিয়ন্ত্রণ
নাগরিকরা সাধারণত বেশ কয়েক বছর অন্তর অন্তর কেবলমাত্র নির্বাচনের সময়টিতেই নিজেদের পছন্দ প্রকাশ করতে পারে। দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কীভাবে কাজ করে থাকে বা কী কাজ করে থাকে, তার উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণের পরিধি অত্যন্ত সীমিত।
(4) দুর্ণীতিগ্রস্ত প্রশাসন
অর্থ এবং তোষামোদের প্রভাব জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীগুলি প্রচারকার্য-সহ অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে প্রশাসনিক বা সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।
(5) আমলাতন্ত্রের উদ্ভব
প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা সাধারণত বৃহৎ ও জটিল আমলাতন্ত্র তৈরি করে। আমলাতন্ত্রের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থায় ব্যাপক বিতর্ক ও মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয় বলে, অনেকসময় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অকারণে কালবিলম্ব হয় এবং তা অকার্যকারী হওয়ারও সম্ভবনা থাকে।
(6) সংখ্যালঘুদের স্বার্থের পরিপন্থী
জনপ্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচনি এলাকায় বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্বের উপস্থাপনা করতে পারে না। এর ফলস্বরূপ, সংখ্যালঘু এবং ক্ষমতাহীন শ্রেণি বা গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত হতে পারে।
(7) সুষ্ঠু ভোটপদ্ধতির অনুপস্থিতি
অনেকসময় নির্দিষ্ট কোনো নির্বাচনি এলাকায় নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সমর্থন জানানোর জন্য জনগণকে বাধ্য করা হয় অথবা উক্ত দলটিকে ক্ষমতায় আসীন করার উদ্দেশ্যে, ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে কারচুপি বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাতে এবারের নির্বাচনেও একই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব বহাল থাকে।
(8) অস্থায়ী নীতি নির্ধারণ
জন প্রতিনিধিগণ সর্বদা পুনর্নির্বাচিত হওয়া উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক স্বার্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যপূরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তাদের এই ধরনের কার্যকলাপ এমন সব নীতি নির্ধারণের পথকে প্রশস্ত করে, যা সুস্থায়ী প্রকৃতির হয় না।
(9) রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি
প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রয়োজনে নির্বাচন প্রক্রিয়া চরম অবস্থান গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যাপক দলাদলিকে উৎসাহ প্রদান করতে পারে, যার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
(10) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বৈধতা হ্রাস
জনগণ যখন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ অনুভব করে বা এটা অনুভব করে যে, তাদের ভোটের কোনো রাজনৈতিক মূল্য নেই, তখনই তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি সীমিত হতে থাকে। আর জনসাধারণের এরূপ আচরণই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বৈধতাকে আরও দুর্বল করে।
(11) আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীনতা
পরোক্ষ গণতন্ত্রে দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে জাতীয় বা আঞ্চলিক জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও একথা কখনই অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিশেষ আঞ্চলিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার অথবা বোঝাপড়া বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না।
(12) দায়বদ্ধহীন সরকার
নির্বাচনক্রিয়া চলাকালীন প্রতিনিধিরা যেসকল কার্যকলাপ সম্পাদন করে থাকেন, তার জন্য তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নাও থাকতে পারেন। ফলত জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকার যে ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়, তা প্রায়শই দুর্বল হতে থাকে।
(13) আদর্শ গণতন্ত্র নয়
আবার অনেকে মনে করেন, পরোক্ষ গণতন্ত্র কখনোই আদর্শ গণতন্ত্র হতে পারে না। কারণ নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণের পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ নির্বাচিত হলেও কার্যকালের নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের নানা কারণে পদচ্যুত করা যায়। ফলে, জনগণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর আঘাত হেনে গণতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা সম্ভব বলে, এরূপ শাসনব্যবস্থাকে অনেকে আদর্শ গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে মনে করেন।
(14) জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে কার্যকর নয়
পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব থাকায় যে-কোনো বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণে কালবিলম্ব হয়। তার ফলে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
(15) তৃণমূল স্তরের নেতৃত্বে
অনেকসময় নির্বাচনি সাফল্যের নিরিখে অশিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তিবর্গ শাসকের পদে আসীন হন। এমন নিম্নমানের নেতৃত্ব সমগ্র জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়।
একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো।
একনায়কতন্ত্রের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-
(1) একনায়কের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা
এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে একজনমাত্র শাসকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর শাসনের পশ্চাতে অবশ্যই একটি বিশেষ দল বা শ্রেণির সক্রিয় সমর্থন বর্তমান থাকে। এই শাসনব্যবস্থা মূল মন্ত্রই হল, “একজাতি, একরাষ্ট্র এবং একনায়ক।”
(2) চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব
একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিবর্তে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে মুসোলিনি বলেছিলেন, “রাষ্ট্রের মধ্যেই সবকিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিংবা রাষ্ট্রের বাইরে কিছু হতে পারে না।”
(3) ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ
একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে চরম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার চরম। বিরোধী হল একনায়কতন্ত্র। কঠোর সামরিকীকরণের মাধ্যমে এই শাসনব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।
(4) বিভ্রান্তিমূলক প্রচারকার্য
বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা প্রচার একনায়কতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একনায়ক নিজের দমনপীড়ন, অত্যাচারকে সুষ্ঠু ও জনকল্যাণকর বলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করেন। অনেকসময় বিরোধী দল বা নেতার ভাবমূর্তিকে আঘাত করার মধ্য দিয়ে নিজ দল বা শ্রেণির প্রতি গণসমর্থক আদায় করার প্রচেষ্টা করে। সরকারি গণমাধ্যমকে আশ্রয় করে একনায়ক এরূপ মিথ্যা প্রচার চালিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জার্মানির আইনসভা রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের পর কমিউনিস্টদের উপর হিটলার মিথ্যা দোষারোপ করে কমিউনিস্টদের নির্মূল করতে তৎপর হলেও, জার্মানরা মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তার কোনোরূপ প্রতিবাদ করেনি।
(5) নির্বাচনি প্রহসন
অসাংবিধানিক উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করার পর একনায়ক নিজের কর্তৃত্বকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে।
(6) বিরোধীদের কণ্ঠরোধ
একনায়কতন্ত্রে একনায়কের দল ব্যাতীত অন্য সমস্ত দলের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রোধ করার জন্য একনায়ক যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। অনেকসময় দেশদ্রোহিতার মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয় বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিভিন্ন গুপ্তচরবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে অত্যাচারী শাসনকে নিরঙ্কুশ করার প্রচেষ্টা করেন একনায়ক।
(7) গুপ্তচর বাহিনীর অস্তিত্ব
একনায়কতন্ত্রে একনায়ক নিজের কর্তৃত্বকে কায়েম রাখার জন্য সুকৌশলে গুপ্তচরবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করে থাকেন। জনগণ কিংবা নিজ দলের কোনো প্রতিনিধি একনায়কের বিরোধিতা করছে কি না তা প্রত্যক্ষ করার জন্য গুপ্তচর বাহিনী গঠন করা হয়। এদের প্রধান কার্যই হল সংবাদ সংগ্রহ এবং তা একনায়কের নিকট সরবরাহ করা। এ প্রসঙ্গে হিটলারের ‘গেস্টাপো’ (Gestapo) এবং মুসোলিনির ‘কালো কুতা’ (Black Shirt) বাহিনীর কথা উল্লেখ্য।
(8) গোপনীয়তা রক্ষা
রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি যেমন-শাসন সংক্রান্ত। কার্যাদি, সাময়িক ক্রিয়াকলাপ, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়ে থাকে।
(9) যুদ্ধের সমর্থক
একনায়কতন্ত্র যুদ্ধের প্রশ্রয় দেয়। একনায়কতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা নিৎসে প্রচার করেন, ‘শান্তি পথ দুর্বলের পথ। পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিমানের বেঁচে থাকায় অধিকার রয়েছে।’ অর্থাৎ, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী এই একনায়কতন্ত্র। আবার, মুসোলিনি মনে করতেন, ‘আন্তর্জাতিক শান্তি কাপুরুষের স্বপ্ন।’ তিনি এও বলতেন “সাম্রাজ্যবাদ শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নিয়ম।”
(10) কঠোরভা
যে-কোনো সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ইত্যাদিকে কার্যকর ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় এরূপ শাসনব্যবস্থায়। এর মাধ্যমেই অত্যাচারী সরকার তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।
পরিশেষে একথা স্পষ্ট যে, একনায়কতন্ত্র হল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ছাড়াও বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক প্রগতি ইত্যাদিরও বিরোধী এই শাসনতন্ত্র। তাই অনেকেই একনায়কতন্ত্রকে ‘মানব সভ্যতার চরম শত্রু’ বলে মনে করেন।
কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার অসুবিধা বা ত্রুটি লেখো।
কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার একাধিক ত্রুটি বিদ্যমান। এগুলি হল-
(1) স্বাধীনতার অভাব
কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় জনগণ খুবই সীমিত পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি নাগরিকদের প্রায় থাকে না বললেই চলে। কেবল সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করা নয়, এরূপ শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিমাণ নাগরিকদের মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়। বিশেষত, বিরোধী নেতৃবর্গ, সাংবাদিক, রাজনৈতিক প্রতিবাদীরা বিভিন্ন প্রকার হয়রানি ও ভীতির সম্মুখীন হয়, যা ব্যক্তির জীবনের অধিকারকে (Right to Life) লঙ্ঘন করে।
(2) দুর্নীতি
কর্তৃত্ববাদে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কোনোরূপ স্থান নেই। একজন শাসক বা কতিপয় শাসকবর্গের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হওয়ায় এবং শাসন সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাবে কর্তৃত্ববাদী প্রশাসনে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় শাসকই যেহেতু সর্বেসর্বা, সেহেতু শাসকপক্ষকে তাদের কোনো কাজের জন্যই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, যা দুর্নীতির সুযোগকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এই দুর্নীতি জনজীবনকে কলুষিত করে এবং জাতীয় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।
(3) স্বৈরাচারের আশঙ্কা
কর্তৃত্ববাদে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একজন বা কয়েকজন শাসকের হাতে অথবা একটি দলের হাতে কুক্ষিগত থাকে বলে, তা স্বৈরাচারের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। যেহেতু কোনো বিরোধী দল বা বিরোধী শক্তি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না, সেহেতু এই ব্যবস্থায় শাসক যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বৈরাচারী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।
(4) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতার অভাব
কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত হওয়ার কারণে নাগরিকদের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা প্রকাশের ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটার সুযোগ খুবই কম। কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশকে দমিয়ে রাখা হয়। এর ফলে এক দমবন্ধ করা পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা সৃজনশীল নাগরিকদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতি বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করে।
(5) সামাজিক অস্থিরতা
কর্তৃত্ববাদে যেভাবে ভিন্নমতকে দমন করা হয়, তার ফলে জনগণের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় বলে অনেকে মনে করেন। শাসক নিজের মতকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার ফলে শিক্ষিত সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ববাদী শাসকের মতকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এগুলির ফলে সমাজে অসন্তোষ, বিরক্তি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে এবং জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা এবং প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে, যা সামাজিক অস্থিরতা, প্রতিবাদ এমনকি বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে। এই অস্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতিকেও ব্যাহত করতে পারে।
(6) গণতান্ত্রিক বৈধতার অভাব
কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সর্বদা বৈধতা লাভ করে না। অন্য ভাষায় বলা যায়, কর্তৃত্ববাদী শাসনে গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে, যা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন ও জনসার্বভৌমিতার নীতিগুলিকে ক্ষুণ্ণ করে। এই শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব থাকায় কর্তৃত্ববাদ এমন নীতি প্রণয়ন করে, যা জনকল্যাণ অপেক্ষা শাসন টিকিয়ে রাখাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।
(7) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দমন
কর্তৃত্ববাদী শাসনগুলি প্রায়ই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, ধর্মীয় অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত জীবনধারার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শৈল্পিক অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে দমন করে সাংস্কৃতিক সমসত্ত্বকরণ (Cultural Homogenization)-এর উপর গুরুত্ব দেয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর – নিষেধাজ্ঞার কারণে সাংস্কৃতিক স্থবিরতার জন্ম দেয়।
(8) সামাজিক মেরুকরণ
কর্তৃত্ববাদী শাসনে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব সামাজিক বিভাজনকে বাড়িয়ে তোলে এবং বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
(9) আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা
কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলি আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক আইনের অবহেলা এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করতে পারে। এমনকি এই কারণগুলির জন্য কর্তৃত্ববাদী দেশগুলি আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা ও নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে।
উপসংহার
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কর্তৃত্ববাদ এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যে ব্যবস্থাকে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, রাজনৈতিক বহুত্ববাদের সীমিতকরণ, ভিন্নমতের দমন ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক উদাহরণ এবং – সমসাময়িক কর্তৃত্ববাদী শাসনগুলি বিশ্লেষণ করলে এর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি এবং সমাজের উপর এই ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে চিত্রিত করা যায়। কর্তৃত্ববাদের অধ্যয়ন থেকে অনুধাবন করা যায় যে, স্বৈরী প্রবণতা বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ফলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বহুত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কর্তৃত্ববাদ যেভাবে ক্ষুণ্ণ করে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য কর্তৃত্ববাদকে বোঝা ও অধ্যয়ন করা আবশ্যক।
সর্বগ্রাসীবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো।
সর্বগ্রাসীবাদী সরকার বা শাসনব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বগ্রাসীবাদের স্বরূপ বা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-
(1) সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
সর্বগ্রাসীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সীমিত থাকে না, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের ব্যক্তিগত জীবন বা সমাজজীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্মাচরণ জীবনযাপন সবকিছুই ব্যাহত হয়। সর্বাত্মকবাদ অনুসারে, রাষ্ট্র হল জাতির বিবেকের মূর্ত রূপ, রাষ্ট্রই হল জনগণের বিবেকস্বরূপ। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে।
(2) আইনের অনুশাসনের অনুপস্থিতি
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে আইনি ব্যবস্থার কোনোরূপ অস্তিত্বই থাকে না, ফলে আইনের অনুশাসনের উপস্থিতি অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় শাসকের নির্দেশই আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইন জনগণকে সুরক্ষা প্রদান বা জনগণের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে না, বরং নাগরিকদের দমনপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
(3) রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি
সর্বগ্রাসীবাদে রাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্তির পূর্বে অর্থাৎ রাষ্ট্র আগে, ব্যক্তি পরে। এখানে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়। এজন্যই সর্বগ্রাসীবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিস্বাধীনতা অনুপস্থিত। এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে যেহেতু জনগণ তথা জাতির বিবেক হিসেবে মনে করা হয়, সেহেতু রাষ্ট্রই ব্যক্তির ভালো-মন্দের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে।
(4) একদলীয় শাসনব্যবস্থা
সর্বাত্মকবাদী শাসনব্যবস্থায় মূলত একদলীয় ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হয়। সর্বগ্রাসী মতাদর্শ বহুদলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় না। এজন্য এখানে শাসক দল ছাড়া অন্য কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের অথবা বিরোধী কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব থাকে না। যদি কোনো বিরোধী শক্তি বা ভিন্নমত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তবে তাকে সমূলে বিনাশ করা হয় এবং শাসকদলের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সমাজে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী নেতৃত্ব শাসকবিরোধী শক্তিকে মুছে ফেলতে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, গুপ্তহত্যা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ নাৎসি জার্মানির কথা বলা যায়। হিটলার জার্মানিতে নাৎসি দলের বিরোধী কোনো শক্তিকে গজিয়ে উঠতে দেননি।
(5) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি
সর্বাত্মকবাদ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কোনোরকম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয় না। এ কারণেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই জনগণ দেশের রাজনৈতিক কার্যে বা শাসনকার্যে অংশ নিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ন্যায় সর্বগ্রাসীবাদে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে জনগণ কোনোরূপ ভোটাধিকারের ক্ষমতা ভোগ করে না। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে জনগণের ভোটাধিকার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।
(6) নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম
সর্বগ্রাসীবাদে গণমাধ্যম অর্থাৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। পরিবর্তে এরূপ শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ গণমাধ্যম দেখা যায়। সর্বাত্মকবাদে গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হল শাসকের সপক্ষে মতপ্রচার করা। গণমাধ্যম বা মিডিয়া সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধীনে থেকে কাজ করে। ফলে রাষ্ট্রগুলিতে তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করে।
(7) পুলিশি নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ, ভীতি প্রদর্শন এবং নজরদারি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এখানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র নয়। সর্বাত্মকবাদ মূলত পুলিশি রাষ্ট্রগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এখানে সবকিছুকেই পুলিশি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় বিরোধীদের দমন এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, জনগণের উপর নজরদারি চালানোর জন্য গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করা হয় এবং গুপ্তচর বাহিনীর রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, নির্যাতন, দমনপীড়ন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালানো হয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েম করা হয়। এভাবে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।
(8) সহিংসতা
এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সহিংসতা (Violence)-কে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রাষ্ট্রপরিচালনা করতে গিয়ে স্বৈরাচারী শাসক ভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতামত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। উপরন্তু রাষ্ট্রের এই সহিংস ক্রিয়াকলাপকে ন্যায়সংগত ও বৈধ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। স্বৈরাচারী শাসক রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে হিংসার আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় দেখে না। যেমন-হিটলারের নাৎসি জার্মানিতে এবং স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নে যথাক্রমে ইহুদি এবং কুলাক (রাশিয়ান ধনী কৃষক)-দের উপর নির্বিচারে দমনপীড়ন চালানো হয় এবং তাদের হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং রাষ্ট্রের সংকটের জন্য তাদেরকেই দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়।
(9) অতিমানব তত্ত্ব
সর্বগ্রাসীবাদে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেখানে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনেতাকে অতিমানব বলে মহিমান্বিত করা হয়। অর্থাৎ সর্বগ্রাসীবাদ রাষ্ট্রনায়কের এমন এক ভাবমূর্তি তৈরি করা হয় যেন তিনি সাধারণ মানব নয়, একজন অতিমানব। তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না, তিনি সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। তিনিই সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা তাকে দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব এবং জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে চিত্রিত করা হয়। ইতালিতে মুসোলিনি, জার্মানিতে হিটলারের এমন অতিমানব ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছিল। সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র অনেকাংশেই নেতৃত্বের ‘Personality Cult’-এর উপর নির্ভর করে।
(10) আদর্শগত শুদ্ধতা
সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা একটি সর্বব্যাপী ও অনমনীয় মতাদর্শ গড়ে তোলা ও প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সামাজিক নিয়মের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নাগরিকদের মধ্যে আদর্শগত সামঞ্জস্যবিধান করতে, শক্তিশালী জনমত গঠন করতে এবং জনগণের আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার মাধ্যমে আদর্শকে প্রচার করা হয়।
(11) কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ
রাষ্ট্র বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিচার বিভাগ, সামরিক বাহিনী, শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম এবং অর্থনীতি-সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করে। প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষমতাসীন দল ও নেতার অধীনস্থ থাকে। এভাবে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র একীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং নীতির বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।
(12) গণসংহতি স্থাপন
সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়, শ্রমিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের মতো গণসংগঠনগুলিকে অনুগত করে রেখে গণসংহতি স্থাপনের ও আনুগত্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।
(13) অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ
অধিকাংশ সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কৃষির সমষ্টিকরণ, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে।
সর্বগ্রাসীবাদের সুবিধা বা গুণ গুলি লেখো।
সর্বাত্মকবাদ বা সর্বগ্রাসীবাদ, সরকারের এমন একটি রূপ, যেখানে রাষ্ট্র সমাজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং সরকারি ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিকের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এই শাসনব্যবস্থার সমর্থকরা এর কতকগুলি সুবিধা বা গুণকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল-
(1) দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রূপায়ণের উপযোগী
সর্বগ্রাসীবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে সরকারি নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার বিলম্ব হয় না। কারণ প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা, প্রশাসনিক সমস্যার নিষ্পত্তি, সংকট বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কোনোরূপ বিতর্ক বা সমঝোতার প্রয়োজন ছাড়াই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং সেই ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্তকে দ্রুত বাস্তবায়িত করা যায়।
(2) সংকটকালীন সময়ের উপযোগী
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ অথবা বৈদেশিক আক্রমণ ইত্যাদি সংকটকালীন বা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রনায়ক সমস্যা সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক রাষ্ট্রনায়কের একক সিদ্ধান্তই যেহেতু চূড়ান্ত, সেহেতু রাষ্ট্রনেতার সিদ্ধান্ত বা মতামতের উপরে কোনো মত থাকে না বলেই সিদ্ধান্তকে দ্রুত রূপায়িত করা সম্ভব হয়।
(3) আর্থিক বিকাশে সহায়ক
সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় শিল্পায়ন এবং আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত সাফল্য পাওয়া যায়। সারা দেশের জন্য একক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে সরকারি অফিসার বা আমলাদের প্রশাসন পরিচালনার সুযোগ থাকে না। এ কারণে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের শাসক এককভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক উন্নয়ন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, বলপূর্বক কৃষির সমষ্টিকরণের মাধ্যমে দ্রুত আর্থিক বিকাশের পথকে তরান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলা যায়। স্তালিন তাঁর রাষ্ট্র সর্বস্ববাদী শাসনে সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন।
(4) একক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের প্রশাসনে সমগ্র দেশে একক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বাসংস্থার অস্তিত্ব থাকে না বললেই চলে অথবা থাকলেও তার ক্ষীণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড রূপায়ণের পথ মসৃণ হয় ও সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন সম্ভব হয়।
(5) সামাজিক শৃঙ্খলা ও কঠোর অনুশাসন
সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ লক্ষ করা যায় বলে এরূপ সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। সারা দেশব্যাপী যে কঠোর অনুশাসন বলবৎ হয়, তার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হয়, তেমনি অপরাধ ও ভিন্নমতকে দমন করা সম্ভব হয়। এজন্যই সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় একটি স্থিতিশীল এবং অনুমানযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা যায়।
(6) জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উপযোগী
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে শুধুমাত্র যে রাষ্ট্রনায়ককে অতিমানব হিসেবে চিত্রিত করা হয় তাই নয়, রাষ্ট্রকেও শ্রেষ্ঠ ও সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরা হয়। সর্বাত্মকবাদে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী মতাদর্শ গড়ে তোলা হয়, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, দলাদলি এবং বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পথ সুগম করা যায়।
(7) জাতীয় নিরাপত্তার উপযোগী
জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মকবাদী শাসনব্যবস্থা সর্বাধিক উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ শাসক সহজেই জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় জনসমাজকে একত্রীকরণ এবং বিদ্রোহ ও গুপ্তচরবৃত্তিকে প্রতিরোধ করতে পারেন।
(8) সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিগ্রহণ
সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে রাষ্ট্র যেহেতু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সেহেতু রাষ্ট্র শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। একইসঙ্গে বাজারি গতিশীলতার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনকে সুনিশ্চিত করতে পারে।
সর্বগ্রাসীবাদের অসুবিধা বা ত্রুটি গুলি লেখো।
সর্বগ্রাসীবাদের বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও, এর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দোষ বা ত্রুটি রয়েছে। এগুলি হল-
(1) ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান খুবই সীমিত। রাষ্ট্রনেতা ব্যক্তিদের সার্বিক পৌর, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন ব্যক্তির বাক্ ও মতামত প্রকাশ, সমাবেশ, ধর্মাচরণ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-সহ জীবনের বেশিরভাগ দিক নিয়ন্ত্রণ করে।
(2) অগণতান্ত্রিক
সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতাদর্শ। গণতন্ত্রের মূল কথাই হল ‘Of the People, By the People, For the People’. গণতন্ত্র যেখানে জনগণের শাসনের উপর গুরুত্ব দেয়, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র শাসক স্বাধীন, এবং দেশের নাগরিকরা শাসকের অধীনস্ত। শাসকের কথাই এখানে শেষ কথা। জনগণের মতামতের কোনো গুরুত্ব সর্বগ্রাসীবাদে দেওয়া হয় না। উপরন্তু জনগণের ভিন্নমতকে দমন করা হয়। এক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও হিংসার ব্যবহারও করা হয়, ফলে নাগরিকরা প্রতিশোধের আতঙ্কে দিন কাটায়। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ নির্বাচন কমিশন, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, স্বাধীন গণমাধ্যমের অস্তিত্ব থাকে না। ফলে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।
(3) একদলীয় প্রাধান্য
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেমন বহুদলীয় ব্যবস্থা স্বীকৃত থাকে, সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে তেমন একদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে। একটি রাজনৈতিক দলই সার্বিকভাবে যাবতীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। শাসকদল ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখানে কল্পনাও করা যায় না। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে না। একক দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত জনগণকে বিনা বাধায় মেনে নিতে হয়।
(4) ব্যক্তি পরিসরে রাষ্ট্রের প্রবেশ
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের সবথেকে বড়ো ত্রুটি হল ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। এরূপ হস্তক্ষেপ একনায়কতন্ত্রেও পরিলক্ষিত হয় না। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র বলার প্রধানতম কারণই হল ব্যক্তির সবকিছুকেই রাষ্ট্র গ্রাস করতে চায়। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চিন্তা, উদ্যোগ, বিশ্বাস, মতামত, জীবনধারা সবকিছুকেই রাষ্ট্র গ্রাস করে, যা ব্যক্তির জন্য এক দমবন্ধ করা পরিবেশ গড়ে তোলে।
(5) সৃজনশীলসত্তার বিরোধী
সমালোচকগণ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকে নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার শত্রু বলে মনে করেন। এরূপ রাষ্ট্রে শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুই যেহেতু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই শিল্প সাহিত্যকেও রাষ্ট্রসর্বস্ব করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বহুত্ববাদের অভাব সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক স্থবিরতা, বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো ও স্তালিনের শাসনকালে এরকম সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর ফলে অনেক সৃজনশীল মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। বহু সময় সৃজনশীল ব্যক্তিরা ভিন্নমত পোষণ করায় তাদের কারাবাস এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয়েছে।
(6) নজরদারি ও সেন্সরশিপ
শাসক গণমাধ্যমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে এবং তথ্য প্রচারের উপর ক্রমাগত নজরদারি চালায়। শুধু তাই নয়, শাসক গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে বিরোধী বা ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করে এবং আত্মগৌরব প্রচার করার মাধ্যমে ক্ষমতাকে ধরে রাখতে চায়।
(7) দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অভাব
এই শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকার করা হয় না, ফলে প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধহীনতাও এই শাসনব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি। নাগরিকদের কাছে প্রশাসনিক তথ্য উপলব্ধ থাকে না, তথ্য লাভ করার বিষয় শাসকের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত থাকে।
(8) অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি
কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকসময় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু কৃষি, শিল্পায়ন সবটাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র অনুমোদিত হয়, সেহেতু উদ্ভাবনীমূলক অর্থনীতি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রায় থাকে না বললেই চলে, যা আর্থিক স্থবিরতার সৃষ্টি করতে পারে।
(9) মানবাধিকার লঙ্ঘন
সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য পরিচিত। কারণ এই শাসনব্যবস্থায় অত্যাচার, দমনপীড়ন, বিনা বিচারে কারাদণ্ডের পাশাপাশি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। বিশেষ করে ভিন্নমতাবলম্বী, সংখ্যালঘু এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এগুলির সম্মুখীন হয়।
(10) ক্ষমতার অপব্যবহার
সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য এখানে অনুপস্থিত। এ কারণে শাসক জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ছাড়াই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। শাসক এরূপ অবাধ ক্ষমতা অপব্যবহার করে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে।
(11) আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা
রাষ্ট্রশাসকের স্বৈরী ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিকে অধিকাংশ সময়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। অনেকসময় আবার দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতা হ্রাস করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বগ্রাসী দেশগুলি বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়।
(12) নৈতিকতা ও মূলবোধের প্রতি চ্যালেঞ্জ
সর্বগ্রাসীবাদ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা এবং অত্যাচারী শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে নৈতিক চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে।
উপসংহার
উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সর্বগ্রাসীতা সমাজের ও ব্যক্তির সমস্ত দিকের উপর নিরঙ্কুশ এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এজন্য অনেকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেননি। সামগ্রিকভাবে, সর্বগ্রাসীতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভীষণভাবে সীমিত করে। শুধু তাই নয়, এরূপ শাসনব্যবস্থা ভিন্নমতের দমন, ভীতিপ্রদর্শন, দমনপীড়ন, ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে উৎসাহিত করে। এটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের এক চরম রূপকে চিহ্নিত করে, যেখানে ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতাকে শাসকের স্বার্থের অধীনে রাখা হয়। যেহেতু সর্বগ্রাসীবাদ একটি সম্মোহনী নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, ফলে এরূপ ব্যবস্থায় সর্বদা একজন সর্বশক্তিমান জীবিত নেতার প্রয়োজন হয়।
সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক উদাহরণগুলি অনুধাবন করে সমাজের উপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলিকে চিহ্নিত করে বলা যায়, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ হল গণতন্ত্রের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক ধারণা। এটি ব্যক্তিমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তার অধিকারগুলিকে পদদলিত করে। বলাবাহুল্য, – এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না। সর্বক্ষণের আতঙ্ক, সন্দেহ ও বলপ্রয়োগ এই ব্যবস্থার ভিত্তি, যা একটি সুস্থ, স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পশ্চাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই পরিশেষে বলা যায়, সর্বগ্রাসীবাদ কেবল মানবতার শত্রু নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার শত্রুস্বরূপ।
আরও পড়ুন – নুন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর