আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : মূল ধারণা এবং রাজনৈতিক মতবাদসমূহ প্রশ্ন উত্তর | ক্লাস 12 চতুর্থ সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম অধ্যায় ছোটো প্রশ্ন উত্তর | International Relations short question answer | Class 12 4th Semester Political Science First Chapter Short question answer
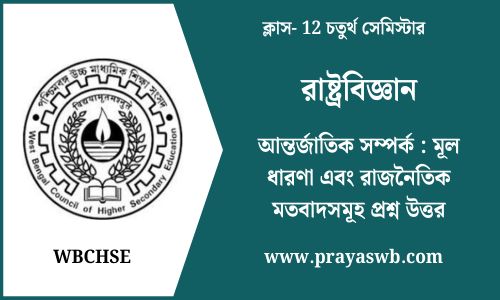
১। কত খ্রিস্টাব্দে এবং কার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস শুরু হয়?
উঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলস্-এর অ্যাবরিস্টউইথ (Aberystwyth) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভিড ডেভিসের উদ্যোগে উড্রো উইলসন চেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস শুরু হয়। স্যার অ্যালফ্রেড জিমার্ন ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রথম উড্রো উইলসন চেয়ারের অধ্যাপক।
২। International Relation’ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে?
উঃ ‘International Relation’ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেখাম। তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘Principle of Moral and Legislation’ রচনাটিতে এই কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।
৩। কোন্ কোন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতি এবং কেন?
উঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে: জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল, ন্যান ডি পামার, হাওয়ার্ড সি পারকিন্স প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।
কারণ: এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ কথাটির মধ্যে দিয়ে শুধু রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্কই নয়, রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের ভূমিকার উপরেও আলোকপাত করা হয়। তাছাড়া ‘আন্তর্জাতিক রাজনীতি’ বা বিশ্বরাজনীতি যেখানে রাজনৈতিক বিষয়াদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অরাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কেও আগ্রহী হয়।
৪। গ্রেসন কার্ক ও মরগেনথাউ-এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী?
উঃ গ্রেসন কার্ক-এর মত: গ্রেসন কার্ক-এর মতে, জাতীয় রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণকারী শক্তিসমূহের আলোচনাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলা হয়।
মরগেনথাউ-এর মত: মরগেনথাউ-এর মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে মূলত ক্ষমতার লড়াইকে বোঝায়।
৫। সিসিল ভি ক্র্যাব আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিতে কয়টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ও কী কী?
উঃ সিসিল ডি ক্র্যাব-এর মত: বিখ্যাত তাত্ত্বিক সিসিল ভি ক্র্যাব আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিতে সাতটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। যেমন- রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্ধারণের পদ্ধতি, রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব লক্ষ্যপূরণের জন্য গৃহীত পদ্ধতি, বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক লক্ষ্যপূরণের জন্য অনুসৃত কর্মসূচি, রাষ্ট্রের লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, সামাজিক লক্ষ্যপূরণে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা পালন, জাতীয় লক্ষ্যপূরণের স্বার্থে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিরোধিতা উভয় দিক থেকে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন।
৬। পামার ও পারকিন্স প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করো।
উঃ পামার ও পারকিন্স-এর মত: ‘Interna-tional Relations’ গ্রন্থে পামার ও পারকিন্স আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ‘বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার অধ্যয়ন’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা আরও বলেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সারা পৃথিবীর সব ধরনের মানুষ ও গোষ্ঠীর সবরকম সম্পর্ক, মানবজীবন, কার্যকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা, চাপ ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।
৭। স্ট্যানলি হফম্যান (Stanley Hoffmann) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা উল্লেখ করো।
উঃ স্ট্যানলি হফম্যান-এর মত: স্ট্যানলি এইচ হফম্যান তাঁর ‘Contending Theories of Interna-tional Relations’ গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামক শাস্ত্রটির প্রতিপাদ্য আলোচ্য বিষয় হল সেই সকল উপাদান ও কার্যকলাপ যা বিশ্বের মৌল এককগুলির বাহ্যিক নীতি এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।”
৮। ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স (International Encyclopedia of Social Science)-এ উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করো।
উঃ ‘ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোশ্যাল সায়েন্স’-এ উল্লেখ করা হয়েছে, “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি মানবীয় কার্যকলাপ যেখানে একাধিক জাতিরাষ্ট্রের মানুষ একাকী বা গোষ্ঠীগতভাবে মিথস্ক্রিয়া করে থাকে।”
৯। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করো।
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে জ্ঞানচর্চার এমন এক আন্তঃশাস্ত্রীয় বিষয়কে বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় এককসমূহের মধ্যে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত প্রভৃতি সকলপ্রকার সরকারি ও বেসরকারি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।
১০। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝো?
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: সাধারণত, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো মানুষ যেমন একা বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি আধুনিক পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলিও আন্তর্জাতিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এরূপ উপলব্ধির কারণে প্রতিটি রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক সমাজে মিলেমিশে থাকার ফলে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সাধারণভাবে তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা হয়।
১১। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবির্ভাব কখন ঘটে?
উঃ স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবির্ভাব সুসংবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব থেকেই। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশ লাভ করতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন শুরু হয়।
১২। বিংশ শতকের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার সীমাবদ্ধতা কী ছিল?
উঃ বিংশ শতকের পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত ছিল না। সেই সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার বিষয়বস্তুও ছিল অত্যন্ত সীমিত। কেবলমাত্র কূটনৈতিক ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ ছিল।
১৩। এমন কয়েকজন তাত্ত্বিকের নাম লেখো যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করেন এবং এমন কয়েকজন তাত্ত্বিকের নাম লেখো যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করেন না?
উঃ সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে কি না-এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র বিষয় : কুইন্সি রাইট, মর্টন কাপলান, কার্ল ডয়েশ্চ, বার্টন, হফম্যান প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পৃথক শাস্ত্র বলে মনে করেন।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র বিষয় নয়: জিমার্ন, পামার ও পারকিন্স প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলে গণ্য করেন না।
১৪। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করার পক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
উঃ পক্ষে যুক্তি: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র বিষয় কারণ-
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি স্বতন্ত্র আলোচ্যসূচি দেখতে পাওয়া যায়। যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছে।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিজস্ব বিশ্লেষণ ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।
১৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করার বিপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
উঃ বিপক্ষে যুক্তি: আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করার বিপক্ষে দুটি যুক্তি হল-
- পামার ও পারকিন্স-এর মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিজস্ব কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।
- আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সর্বদা পরিবর্তনশীল।। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা দীর্ঘমেয়াদি।
১৬। Politics Among Nations’-গ্রন্থটি কার লেখা? এটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উঃ ‘Politics Among Nations’ গ্রন্থটি হ্যানস্ জে মরগেনথাউ (Hans J Morgenthau)-এর লেখা।
এই গ্রন্থটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
১৭। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করো।
অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি বা আলোচনাক্ষেত্র উল্লেখ করো।
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি: একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু সদা পরিবর্তনশীল। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচ্য বিষয়গুলি হল-আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, জাতীয় শক্তি, জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক, বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির বিদেশনীতি, সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও ইতিহাস ইত্যাদি।
১৮। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের গুরুত্ব কী?
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের গুরুত্ব: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের ফলে একদিকে যেমন বিশ্বরাজনীতি, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বিষয়ে গভীর উপলব্ধি হয়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন পেশায় যথা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকতায়, বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাসে কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেয়।
১৯। সপ্তদশ শতকের কোন্ ঘটনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্মলগ্ন বলে চিহ্নিত করা হয়?
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কিছু বিশ্লেষকদের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্ম ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। কারণ ওই বছরই ‘ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি চুক্তি’ (Treaty of Westphalia) স্বাক্ষরিত হয়। মনে করা হয় যে ওই চুক্তির কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরবর্তী যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয়।
২০। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিটির সম্পর্ক কী?
উঃ ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তিরিশ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরে ইউরোপে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন।
এই চুক্তির পর থেকে প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি সঠিক রূপ পরিগ্রহ করে।
২১। প্রিন্সিপাল্স অফ ইন্টারন্যাশনাল ল এবং ‘দ্য গ্রেট ইলিউশন’ গ্রন্থদুটি কাদের লেখা?
উঃ ‘প্রিন্সিপাল্স অফ ইন্টারন্যাশনাল ল’ গ্রন্থটি জেরেমি বেথাম-এর লেখা।
‘দ্য গ্রেট ইলিউশন’ গ্রন্থটি নর্ম্যান অ্যাঞ্জেল-এর লেখা।
২২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে উড্রো উইলসনের ভূমিকা কী ছিল?
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে উড্রো উইলসনের ভূমিকা: ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮ জানুয়ারি স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পন্থা সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আদর্শবাদী উড্রো উইলসন মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে তাঁর ‘চোদ্দো দফা’ দাবি সম্বলিত বক্তব্য তুলে ধরেন। এই প্রস্তাবে সমস্ত প্রকারের গোপন কূটনীতির অবসান, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, এমনকি ভিন্ন মতাদর্শী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরাজিত জার্মান-সহ সকল দেশকে সমমর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়। এভাবে উড্রো উইলসন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় আদর্শবাদী ভাবধারার জন্ম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর চোদ্দো দফানীতির উপর ভিত্তি করে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৩। কবে, কেন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়?
উ: জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
২৪। কবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করে?
অথবা, কীভাবে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস শুরু হয়?
উঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড ডেভিস-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ওয়েলস্-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আন্তর্জাতিক রাজনীতি’-র উড্রো উইলসন প্রফেসর পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে।
২৫। কবে এবং কেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO)।
প্রতিষ্ঠার কারণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতির পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এবং বিশ্বজনীন বিষয়ে দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২৬। ইউনেস্কো-র সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে?
উঃ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) প্যারিসে সম্মেলন আহবান করে। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এখানে মূলত ৩টি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সেগুলি হল- আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইন।
২৭। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ধারার অবদান লেখো।
উঃ বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ধারা: ১৯৫০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবশ্যিকতাকে তুলে ধরেন। যেমন, অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা (Hypoth-esis Testing), সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার (Statistics), পরিমাপ (Quantification), তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Data Collection and Analysis), প্রতিরূপ নির্মাণ (Model Building) ইত্যাদি অনুসরণের উপর জোর দেন। এই তাত্ত্বিকদের মতে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সাবেকি চিন্তাবিদদের মতো অনুমান, উচিত-অনুচিত প্রশ্ন ইত্যাদি পরিহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই তত্ত্বের প্রধান তাত্ত্বিক হলেন ডেভিড ইস্টন, মর্টন কাপলান প্রমুখ।
২৮। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় প্রথম মহাবিতর্ক কী?
উঃ প্রথম মহাবিতর্ক: ১৯৩০-এর দশকে আদর্শবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বাস্তববাদী তত্ত্ব গড়ে উঠতে শুরু করে। এই সময় থেকে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় প্রথম মহাবিতর্ক বা বাস্তববাদী-আদর্শবাদী মহাবিতর্ক নামে পরিচিত। আদর্শবাদ যেখানে নীতিবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাস্তববাদ সেখানে নীতিবর্জিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক ধারণাকে তুলে ধরে যা বিরোধের সৃষ্টি করে।
২৯। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় দ্বিতীয় মহাবিতর্ক কী?
উঃ দ্বিতীয় মহাবিতর্ক: ১৯৫০-এর দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আচরণবাদীরা তীব্র বিরোধিতা গড়ে তোলেন। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিকরা মূলত উচিত-অনুচিত, অনুমাননির্ভর তত্ত্ব নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিতেন। অন্যদিকে আচরণবাদীরা অনুমানের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেন। কিন্তু সাবেকি তাত্ত্বিকগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিষয়ে জটিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ধারণা কাঠামোর ব্যবহার অর্থহীন। কারণ এই শাস্ত্রটি ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উপরে নির্ভরশীল এবং আন্তর্জাতিক সমাজে ক্ষমতা ও সহযোগিতা উভয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির বিতর্ক ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশক ধরে চলে, যাকে দ্বিতীয় মহাবিতর্ক বলা হয়।
৩০। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি সম্পর্কে ভিনসেন্ট বেকার-এর মত কী ছিল?
উঃ ভিনসেন্ট বেকার-এর মত: ভিনসেন্ট বেকার (Vincent Baker) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘The Introductory Course in International Relation’ গ্রন্থে যে বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধিভুক্ত করেছেন সেগুলি প্রধান শক্তিসমূহ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, শক্তির উপাদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহ, জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা, রাষ্ট্রসমূহের বিদেশনীতি এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিহাস। জাতীয় জাতীয় স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার, শক্তিধর সম্প্রতি
৩১। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি সম্পর্কে গ্রেসন কার্ক-এর অভিমত আলোচনা করো।
উঃ গ্রেসন কার্ক এর অভিমত: গ্রেসন কার্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধির মধ্যে ৫টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। যথা- রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা, রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী উপাদানসমূহ, বৃহৎ শক্তিগুলির অবস্থান ও বিদেশনীতি, সাম্প্রতিককালের স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, বিশ্বব্যবস্থা গঠন।
৩২। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি সম্পর্কে কুইন্সি রাইট-এর শ্রেণিবিভাজন উল্লেখ করো।
উঃ কুইন্সি রাইট এর শ্রেণিবিভাজন: ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘The Study of Internation-al Relations’ গ্রন্থে অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy wright) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুরূপে চিহ্নিত করেছেন। যথা- কূটনৈতিক ইতিহাস, সমরবিজ্ঞান ও যুদ্ধকৌশল, জাতীয় স্বার্থের হাতিয়াররূপে কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ঔপনিবেশিক সরকার এবং বিদেশনীতি পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ।
৩৩। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি হিসেবে কৌলৌম্বিস ও উল্ফ-এর মত লেখো।
উঃ কৌলৌম্বিস ও উল্ল্ফ-এর অভিমত: ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘Introduction to In-ternational Relations: Power and Jus-tice’ গ্রন্থে কৌলৌম্বিস ও উল্ফ (Theodore Couloumbis and James Wolfe) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন আলোচনা পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্ব, জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ, জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা, বিদেশনীতি, জাতীয় স্বার্থ, কূটনীতি, যুদ্ধ, শক্তির ভারসাম্য, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক কল্যাণকর কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, উন্নত ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকারী, সভ্যতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জসমূহ।
৩৪। জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?
উঃ জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল-এর অভিমত : জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল (Joseph Frankel) ‘আন্তর্জাতিক রাজনীতি’ তথা ‘বিশ্বরাজনীতি’ কথাটি বিশেষার্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি মনে করেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়গুলি হল- আন্তঃরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি।
৩৫। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু কী?
উঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। তবুও নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে এখানে উল্লেখ করা যায়- আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখা এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক, জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা, সন্ত্রাসবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ ও তার ব্যাপ্তি এবং শান্তি, রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির পররাষ্ট্রনীতি, শক্তির উত্থান-পতন ইত্যাদি।
৩৬। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন ইস্যুগুলি উল্লেখ করো।
উঃ উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারক ছিল জাতিরাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন, ব্যক্তি ইত্যাদি। কিন্তু ঠান্ডা লড়াইয়ের পর থেকে বিশ্বসমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বিশ্বায়নের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন-বহুজাতিক সংস্থা ও তার ভূমিকা, নারীর ভূমিকা, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুনভাবে আলোচ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে।
৩৭। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তনের পথে আদর্শবাদ (idealism) ধারাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি লেখো।
উঃ আদর্শবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: উদারনৈতিক আদর্শবাদী পণ্ডিতগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও ভয়ংকর পরিণাম দেখে উপলব্ধি করেন যে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করা যায়। এজন্য আদর্শবাদ রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র প্রসারের উপরে বেশি জোর দেয়।
৩৮। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় আদর্শবাদের উদ্ভব হয় কখন?
উঃ আদর্শবাদী তত্ত্বের উদ্ভব: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) ভয়াবহতার ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ যুদ্ধকে পরিহার করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্লেষণ শুরু করেন এবং উপযুক্ত নৈতিক জ্ঞানতত্ত্ব গঠনের প্রয়াস শুরু করেন। এই সময় (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) ইংল্যান্ডের ওয়েল্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টির আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। আবার অনেকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন-এর চিন্তাধারা বিশেষ করে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে তাঁর চোদ্দো দফা প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় আদর্শবাদের জন্ম হয়।
৩৯। উড্রো উইলসন-এর চোদ্দো দফা প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করো।
উঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চোদ্দো দফা প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলি হল-সমস্তরকম গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে প্রকাশ্য কূটনীতির সূচনা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, সমস্ত উপনিবেশ অঞ্চলের স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ স্থাপন, সমস্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।
৪০। আদর্শবাদী তত্ত্বের কয়েকজন তাত্ত্বিকের নাম লেখো।
উঃ আদর্শবাদের প্রধান তাত্ত্বিকগণ: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শবাদী তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। উড্রো উইলসন ছাড়া আদর্শবাদী ভাবনার অন্যান্য প্রবক্তারা ছিলেন-ন্যান অ্যাঞ্জেল, স্যার অ্যালফ্রেড জিমার্ন, বাটার ফিল্ড, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ।
৪১। আদর্শবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা লেখো।
উঃ আদর্শবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা: আদর্শবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে ১৯৩০-এর দশক থেকে বিভিন্ন সমালোচনা শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা হল-
① ক্ষমতার রাজনীতির উপেক্ষা: সমালোচকদের মতে নীতিবোধকে সামনে রেখে রাষ্ট্রগুলি চালিত হয় না বরং ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করা যায় না। কিন্তু আদর্শবাদে ক্ষমতার রাজনীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
② অবাস্তব ধারণা: সমালোচকরা আদর্শবাদকে কাল্পনিক মতবাদ হিসেবে সমালোচনা করেছেন। কারণ সংঘর্ষমুক্ত, সহযোগিতার আদর্শে উজ্জীবিত বিশ্বের যে ছবি তাঁরা তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই।
৪২। কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় বাস্তববাদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে?
উঃ বাস্তববাদী তত্ত্বের উদ্ভব: জাতিসংঘ বা লিগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠা করার পিছনে প্রধান কারণ ছিল বিশ্ব থেকে যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে নির্মূল করা। কিন্তু জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হওয়ার এক দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন অস্থিরতা দেখা দেয়। একদিকে ফ্যাসিবাদের উত্থান অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন নতুন করে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় বিদ্যমান আদর্শবাদী তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ই এইচ কার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Twenty Years’ Crisis, 1919-1939-এ আদর্শবাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে দেখান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার রাজনীতির উপর ভিত্তিশীল। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তথা ঠান্ডা লড়াই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় রাজনৈতিক বাস্তববাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।