শ্রীমদ্ভগবতগীতা – নিষ্কাম কর্মের ধারণা প্রশ্ন উত্তর
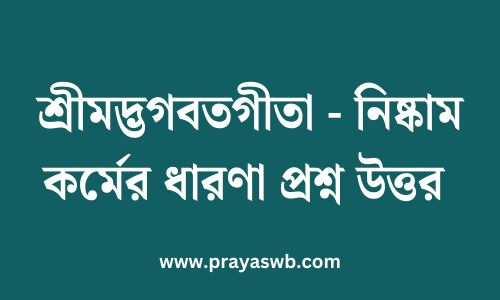
1. বিবেক বলতে কী বোঝায়?
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, শরীর এবং মন একটি অপরটির থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। শরীর অনিত্য, অসৎ একদেশীয় এবং বিনাশশীল এবং মন নিত্য, সৎ, সর্বব্যাপী এবং অবিনাশী। বিনাশশীল বস্তুর বিনাশ দেখে দুঃখী না হওয়া এবং অবিনাশী বস্তুর অবিনাশ্বত্ব দেখে তাকে ধরে রাখার প্রয়াস না করাকে ‘বিবেক’-বলা হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি যোগমার্গেই বিবেকের অত্যন্ত প্রয়োজন থাকে। ‘আমি শরীর থেকে সর্বতোভাবে পৃথক’- এই রকম বিবেকবোধ জাগলেই ব্যক্তির মুক্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়।
2. ‘বিবেক’ এবং ‘বুদ্ধি’ কি এক?
‘বিবেক’ এবং ‘বুদ্ধি’ দুটি শব্দ এক নয়। নিত্য এবং অনিত্য, সৎ এবং অসৎ, বিনাশী এবং অবিনাশী, শরীর এবং মনকে পৃথক ভাবে বোঝবার জন্য ‘বিবেকবোধ-এর প্রয়োজন হয়, ‘বুদ্ধি’-র প্রয়োজন হয় না। বিবেক হল ‘বুদ্ধি’-র থেকে শ্রেষ্ঠ। বিবেক বুদ্ধিতে প্রকটিত হয়। বুদ্ধি প্রধান জীব হওয়ায় মানুষের এই বিবেক বোধই বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়, তাই মানুষ তার ‘বিবেক’ দ্বারা জন্মমরণরূপ বন্ধন থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত হয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি লাভ করতে সমর্থ হয়। বিবেক জাগ্রত হলে অর্থাৎ শরীর এবং মনের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হলে মানুষ নিজের শক্তিতে অনুভূত শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ সমস্ত জগৎসংসারের সম্পর্ক থেকে চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়।
3. স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষণ কী?
স্থিতপ্রজ্ঞের প্রধান লক্ষণটি হল –
“প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।” (২/৫৫)
অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করেন। কারণ যতক্ষণ মন কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত হয়, ততক্ষণ মন আত্মাতে স্থির হতে পারে না। কামনাই মনকে চালিত করে। তাই বিষয়ের বাসনা দূর না হলে কোনো ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারে না। মানুষের বহুবিধ কামনা যেমন অর্থের কামনা, যশের কামনা, স্বর্গলাভের কামনা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। কামনা পূরণে যে সুখ তা অনিত্য, তুচ্ছ এবং দুঃখেরই নামান্তর। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে সুখ অনুভব করেন তার কাছে কামনা পূরণের সুখ মূল্যহীন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজের আত্মাতেই তৃপ্ত, বাইরের কোনো সুখ তিনি কামনা করেন না। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যখন যোগী বা সাধক তাঁর সমস্ত কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নিজেতেই নিজে তৃপ্ত থাকেন তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।
সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে যিনি নিষ্কাম কর্ম করেন তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ‘যোগস্থ’। অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাকে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে জ্ঞান করেন এবং সমস্ত প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কর্মফলকে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করেন।
4. স্থিতপ্রজ্ঞ হতে গেলে বিষয় কামনারহিত হওয়ার অতিরিক্ত কী কী মানসিক অবস্থা তাঁর মধ্যে থাকা দরকার?
স্থিতপ্রজ্ঞ হতে গেলে চিত্তকে কেবল বিষয় কামনারহিত করলেই হবে না। এইরূপ ব্যক্তি দুঃখে উদ্বিগ্ন হবেন না এমনকি দুঃখের আশঙ্কাতেও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। আবার সুখের প্রতিও তাঁর কোনো স্পৃহা নেই। দুঃখ এবং সুখ এই দুটিতেই তিনি সমানভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তিনি ভয় ও ক্রোধশূন্য। ‘বীতরাগ’ এই পদ্ধতির দ্বারা শুধু নিরাসক্তিকে বোঝায় না। ভয় এবং ক্রোধের অনুপস্থিতিকেও বোঝায়। যারা সাধারণ গৃহী মানুষ তারা প্রীতিদায়ক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন আবার বস্তুটিকে হারাবার ভয়ও তাদের মনের মধ্যে থাকে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মনে কোনো বস্তুর প্রতি কোনো অনুরাগ থাকে না। আবার বস্তুটিকে হারাবার ভয়ও থাকে না। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মনে দুঃখে উদ্বিগ্ন হওয়া বা সুখের প্রতি স্পৃহা, অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ কোনোটিই থাকে না।
5. স্থিতপ্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিস্পৃহভাবে, মমতাশূন্যভাবে, অহংকারশূন্যভাবে বিচরণ করে পরম শান্তি লাভ করেন। স্থিতপ্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-
- প্রথমত: স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী ব্যক্তি ভোগ্য পদার্থের প্রতি নিস্পৃহ থাকেন। বিষয়ের প্রতি স্পৃহা মানুষের চিত্তকে অস্থির করে, অশান্ত করে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্পৃহাশূন্য হওয়ায় তার চিত্ত স্থির ও শান্ত।
- দ্বিতীয়ত: স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নির্মম অর্থাৎ মমতাশূন্য, অনুরাগশূন্য। ‘আমার-আমার’ বোধই মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ মানুষের দুঃখের মূল কারণ। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির দুঃখবোধ নেই, কেন-না তার মমত্ববোধ নেই।
- তৃতীয়ত: স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিরহঙ্কারী। ‘আমি জ্ঞানী’, ‘আমি ধনী’, ‘আমি কর্তা’, ‘আমি ভোক্তা’, ‘আমি দাতা’ ইত্যাদি প্রকারের যে, ‘আমি-আমি’ বোধ তাই হল অহংকার। অহংকার মানুষকে অধঃপতিত করে এবং তা অশেষ দুঃখের কারণ হয়।
6. স্থিতপ্রজ্ঞ কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে লেখো। অথবা, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কী?
স্থিতপ্রজ্ঞের প্রকার
গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে অবস্থাভেদে দুই প্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ও অপরটি ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ।
(1) সমাধ্যি স্থিতপ্রজ্ঞ: যিনি বাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ধ্যান সমাধিতে মগ্ন থাকেন। অর্থাৎ যোগী যখন সকলপ্রকার কর্মবিহীন হয়ে থাকেন তখন তাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। সমাধি কথার অর্থ হল যার বুদ্ধি বাহ্যবিষয়ে স্থিত না হয়ে আত্মায় স্থিত হয়। এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সকলপ্রকার কামনা-বাসনাকে মনের ধর্মরূপে গ্রহণ করেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন এই কামনা-বাসনা আত্মাস্বরূপ নয়। তাই সেগুলিকে তারা খুব সহজেই পরিত্যাগ করতে পারেন।
(2) ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ: যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কথা-বার্তা, গতি, প্রকৃতি ইত্যাদি মোহগ্রস্থ ব্যক্তির স্বভাব থেকে স্বতন্ত্র তাকে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। কোনো স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সমাধি অবস্থা থেকে উন্নীত হলে তাকে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির শোক, তাপ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে না। গীতায় উল্লেখ আছে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না। এই অবস্থায় যোগীর ইন্দ্রিয়গুলি যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকলেও আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন। এর ফলে তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ে স্থিত নয়, বরং তার চিত্ত কেবলমাত্র ঈশ্বরে সমর্পিত।
7. ব্রাত্মীস্থিতি কী?
সমস্ত কামনা-বাসনা বর্জন করে, কাম্যবস্তুতে স্পৃহা ত্যাগ করে, মমত্ববুদ্ধি ও অহংকারশূন্য হয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্টচিত্ত হওয়াকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’ কথার অর্থ হল চিত্তে ব্রহ্মের স্থিতি বা অবস্থান। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে বিরাট ব্রহ্মসত্তায় বিরাজমান, যে ব্যক্তি জীবনে কখনও মোহের অধীন হন না, একমাত্র সেই স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী পুরুষই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেছেন মরণকালে তার ওই স্থিতির বিনাশ হয় না। তিনি ব্রহ্মতেই সমাহিত থাকেন, তাকে আর পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয় না। ব্রার্থীস্থিতির লক্ষণ হল নিস্পৃহতা, নির্মমতা ও নিরহঙ্কার। এই প্রকারের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি সংসারে বিচরণ করে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। চিত্তের সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থা ব্রাহ্মীস্থিতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই শান্তি লাভ করতে হলে কামনা, মমতা ও অহংকার ত্যাগ করতে হবে। কর্মের সঙ্গে যে কামনা- বাসনা ও অহংকার জড়িত থাকে তাতেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয়। সুতরাং গৃহী, সন্ন্যাসী বা যোগী যেই হোক না কেন, যিনি কামনা ও অহংকার ত্যাগ করে ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করতে পারেন তিনিই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের যোগ্য। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মোক্ষ লাভ করেন।
8. যজ্ঞার্থ কর্ম বলতে শ্রীকৃষ্ণ কী বুঝিয়েছেন?
নিষ্কাম কর্মকে গীতায় বলা হয়েছে ‘যজ্ঞার্থ কর্ম’। যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের ফল কোনো বন্ধন সৃষ্টি করে না। আমরা যদি কোনো উদ্দেশ্য পূরণের বা সিদ্ধির জন্য কর্ম করি তবে সেই কর্মকে বলা হবে ভোগার্থ কর্ম। কিন্তু যদি ত্যাগের জন্য কোনো যজ্ঞ করা হয় সেই কর্ম হবে যজ্ঞার্থ কর্ম। নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয় তা নিজের জন্য, কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয় জগতের হিতের জন্য করা হয়। গীতায় বলা হয়েছে, যে কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করা হয় তা হল যজ্ঞার্থ কর্ম। যন্ত্র যেমন যন্ত্রী দ্বারা চালিত হয়, যন্ত্রের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না, তেমনি মানুষও তার সমস্ত কর্মে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়। মানুষ যখন নিজেকে ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে গণ্য করে, তখন তার বোধ হয় যে সে তার সকল কর্মের নিমিত্তমাত্র। এই বোধের উন্মেষ হলে মানুষের সকল কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় এবং যখন আমরা ঈশ্বরকে সকল কর্মের নিয়ামক রূপে উপলব্ধি করি তখন সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকেই সমর্পণ করি।
9. স্থিতধী চেতনায় কোন্ ধরনের কর্ম দেখা যায়?
স্থিতধী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সাংখ্য অনুসৃত জ্ঞানমার্গ (বা নিবৃত্তিমার্গ) অথবা মীসাংসক অনুসৃত কর্মমার্গ বো প্রবৃত্তিমার্গ) অনুসরণ না করে তাদের সমন্বিত করে বুদ্ধিযোগে কর্মসম্পাদন করেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকে ‘আত্মজ্ঞান’-এর সঙ্গে যুক্ত করে বা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে, (কেন-না আত্মাই পরমাত্মা ঈশ্বর) ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্যজ্ঞানে কর্ম সম্পাদন করেন।
এই প্রকার বুদ্ধিযোগে একই সঙ্গে বলা হয়- ‘কর্ম করো’, ‘কর্ম পরিত্যাগ করো’। ‘কর্ম করো’ অর্থাৎ নিজবুদ্ধিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদন করো আর ‘কর্ম পরিত্যাগ করো’ অর্থাৎ নিজবুদ্ধিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে সংকীর্ণ কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করো।
10. মোক্ষমার্গ কী? গীতায় কি মোক্ষমার্গ স্বীকৃত হয়েছে?
মোক্ষমার্গ
‘মার্গ’ শব্দের অর্থ হল পথ। মোক্ষমার্গ মানে হল মুক্তিলাভের পথ। যে পথ দিয়ে গেলে জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব তাই হল মুক্তি মার্গ। ভারতীয় দর্শনে মুক্তিলাভের সহায়ক হিসাবে তিনটি মার্গ বা পথের কথা বলা হয়েছে- জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্মমার্গ। অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে এবং কর্মের মাধ্যমে জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব।
গীতায় স্বীকৃত মোক্ষমার্গ
গীতার অষ্টম অধ্যায়ের নাম হল মোক্ষযোগ অর্থাৎ যে পথ অবলম্বন করে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব সে কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মোহমুক্তি ঘটেছিল। তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনে তিনি সেই বিষাদ ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন।
11. নিষ্কাম কর্ম’ কীভাবে ব্যক্তিকে মোক্ষমার্গে উপনীত করতে সক্ষম হয়?
আসক্তিহীনভাবে কর্ম করলে তবেই মানুষ সেই কর্মের উর্ধ্বে গমন করতে পারে, পরম কাম্যবস্তুকে লাভ করতে পারে। যদি মানুষ আসক্তিহীনভাবে কর্ম করে তাহলে সেই মানুষ, সেই কর্মের ক্ষুদ্র পরিসরে বা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কর্মের গন্ডী ত্যাগ করে যেতে পারে না।
তাই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে, শুধুমাত্র অনাসক্ত হয়ে অর্থাৎ কর্ম ফলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, যদি কর্মানুষ্ঠান করা যায় তাহলে সেই কর্মের ফল ব্যক্তিকে আবদ্ধ করে না। অনাসক্ত চিত্তে কর্মানুষ্ঠান করলে চিত্তের সমস্ত মালিন্য নষ্ট হয় এবং সেই নির্মল চিত্তে পরম আনন্দের অনুভূতি হয়। তাই কর্মত্যাগ নয়, আসক্তিহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মই মানুষকে মোক্ষমার্গে উপনীত করতে সক্ষম।
12. ভারতীয় দর্শনে মোক্ষলাভের কী কী উপায় বা মোক্ষমার্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?
চার্বাক বাদে প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। কেন-না দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। অর্থাৎ আধিদেবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই সকল প্রকার দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়াকে বলা হয় মোক্ষ।
ভারতীয় দর্শনে মোক্ষলাভের মূলত তিনটি পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে – জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ।
(1) জ্ঞানমার্গ: জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। ন্যায়-বৈশেষিক, অদ্বৈত বেদান্তী এই মতের সমর্থক।
(2) কর্মমার্গ: এই মত অনুসারে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা সম্ভব। প্রাচীন মীসাংসক, স্বামী বিবেকানন্দ এই মতের সমর্থক।
(3) ভক্তিমার্গ : এই মত অনুসারে ভক্তিই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন আর ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য প্রয়োজন ভক্তি। রামানুজ এই মতের সমর্থক।
13. ত্রিগুণ কী? শ্রীকৃষ্ণ বেদকে কেন ত্রিগুণাত্মক বলেছেন?
ত্রিগুণ
সত্ত্ব, রজো তমো এই তিনটিকে একত্রে ত্রিগুণ বলা হয়েছে।
(1) সত্ত্বগুণ: সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক। সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে কারোর শরীরে অপবিত্রতা ও অলসভাব থাকে না অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি পবিত্র হয় ও আলস্য দূরীভূত হয়।
(2) রাজাগুণ: রজোগুণ শক্তি ও চাঞ্চল্যস্বরূপ। রজোগুণ মানুষকে শান্ত থাকতে দেয় না, সর্বদাই চঞ্চল করে রাখে।
(3) ভামাগুণ: তমোগুণের আধিক্য হলে শরীর ভারী বোধ হয় অর্থাৎ অলসতা বা আলস্য এসে কোনো কাজ করতে দেয় না, সবকিছুই যেন আবৃত করে রাখে। তাই তমোগুনকে বলা হয় গুরু ও আবরক বা অপ্রকাশক।
বেদ ত্রিগুণাত্মক
শ্রীকৃয় বেদকে ‘ত্রিগুণাত্মক’ বলেছেন। কেন-না বেদে যে সব কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে সেগুলির ফল হল ইহলোকে নানাবিধ সুখ ও ঐশ্বর্যভোগ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ। তাই বেদের কর্মকাণ্ড ত্রিগুণের অতীত নয়।
14. নির্দ্বন্দ্ব’, ‘নিত্যসত্ত্বস্থ ‘নির্যোগক্ষেম’ এই শব্দগুলির অর্থ কী কী?
নির্দ্বন্দ্ব
‘নির্দ্বন্দ্ব’ শব্দটির অর্থ হল সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র ইত্যাদির দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই সকলপ্রকার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে দ্বন্দ্বাতীত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।
নিত্যসত্ত্বস্থ
‘নিত্যসত্ত্বস্থ’ শব্দের অর্থ সর্বদা সত্ত্বগুণে অবস্থান থাকা। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজো এবং তমোগুণকে পরাভূত করলে ত্রিগুণের অবসান হয়। তখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। আত্মার এই অবস্থাকে নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা বলা হয়।
নির্যোগক্ষেম
‘নির্যোগক্ষেম’ শব্দের অর্থ হল যোগক্ষেম রহিত হওয়া। অলব্ধ বস্তুর লাভকে ‘যোগ’ এবং লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণকে বলে ‘ক্ষেম’। কাম্যবস্তুর লাভ ও তাকে সংরক্ষণ করা আত্মজ্ঞানীর লক্ষ্য নয়। কারণ আত্মজ্ঞানী জানেন যে পুরুষ বা আত্মা স্বরূপত নির্লিপ্ত, কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।
15. গীতা অনুসারে স্বধর্ম ও পরধর্ম আলোচনা করো।
গীতা অনুসারে প্রতিটি বর্ণের এবং আশ্রমের উদ্দেশ্যে যে নির্দিষ্ট কর্ম বিহিত আছে সেটিই হল তাদের স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি কখনোই কাম্য নয়। রাগ, ভয়, দুঃখের বশবর্তী হয়ে স্বধর্মপালন থেকে বিরত থাকা উচিৎ নয়। স্বধর্ম পালনে মৃত্যুবরণও শ্রেয়। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল অধ্যাপনা, দানগ্রহণ ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হল- রাজধর্ম রক্ষা, বৈশ্যের স্বধর্ম হল বাণিজ্য, কৃষিকাজ প্রভৃতি এবং শূদ্রদের স্বধর্ম হল অন্য বর্ণের মানুষদের পরিচর্যা করা।
স্বধর্মের বিপরীত হল পরধর্ম। বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্তব্য পালন না করে যদি অন্য বর্ণের জন্য নির্ধারিত ধর্ম পালন করে তবে তা সেই ব্যক্তির পরধর্ম। গীতায় পরধর্মকে ভয়াবহ বলা হয়েছে। স্বধর্ম পালনের তুলনায় পরধর্ম পালন সহজতর হলেও প্রত্যেকেরই স্বধর্ম পালন একান্ত কর্তব্য।
16. ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে?
ধর্মের জয় এবং অর্ধমের পরাজয়ের জন্য যে যুদ্ধ তাকে ধর্মযুদ্ধ বলে। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হল সত্ত্বমিশ্রিত রজোপ্রধান। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, দান প্রভৃতি গুণ দেখা যায়। এই সব গুণের অধিকারী বলে রাজ্যশাসন ও রক্ষা, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুতর কাজের ভার ক্ষত্রিয়ের উপর পড়ে। রাজ্যরক্ষা, দুষ্টের দমন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করতে হলে যুদ্ধ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধ ধর্মসঙ্গত হওয়া চাই। ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য নয়। দুষ্টের দমন, ধর্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, আত্মরক্ষা, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতি কার্যের জন্য যে যুদ্ধ করা হয়, তাকে ধর্মযুদ্ধ বলে।
শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেন, এই ধর্মযুদ্ধ না করলে অর্জুন স্বধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ করে পাপের ভাগী হবেন। সুতরাং ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া স্বধর্মচ্যুতি।
17. শ্রীকৃষ্ণ কেন বলেছেন যে কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম উন্নতমানের?
শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম যে উন্নততর তা বোঝাবার জন্য বলেছেন, যেসব ব্যক্তি মনে করেন, বেদে ঈশ্বর তত্ত্ব নেই এবং স্বর্গের অভিলাষী হয়ে কাম্যকর্ম সম্পাদন করেন, তারা বিচারবিহীন এবং মূঢ়। তারা বেদের বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ। স্বর্গলাভ করলে তারা নানারকম ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারবেন এই আশায় তারা বহু আয়াসসাধ্য কর্মকান্ড করে থাকেন। যেগুলি আড়ম্বরপূর্ণ এবং বাহুল্যবিশিষ্ট। এইসব ব্যক্তি যে কথাগুলি বলেন সেগুলি আপাত মধুর। ঠিক যেমন কিছু বৃক্ষ আছে সেগুলিতে সুন্দর ফুল ফোটে কিন্তু কোনো ফল ধরে না।
শ্রীকৃষ্ণ কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম যে উন্নতমানের তা দেখিয়েছেন। বেদের কর্মকান্ডে যেসব যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে সেগুলিও কাম্য কর্ম। কোনো যজ্ঞে পশুলাভ, কোনো যজ্ঞে বিত্তলাভ, কোনো যজ্ঞে স্বর্গলাভ নির্দিষ্ট আছে। তাহলে কাম্যকর্মকে নিকৃষ্ট আমরা কীভাবে বলবো?
এর উত্তরে বলা হয় যে, বেদের কর্মকান্ডে যেসব কাম্যকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে পশু, বিত্ত, স্বর্গ লাভ করা যায়। কিন্তু তার দ্বারা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ লাভ করা যায় না। এজন্য বেদের জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদের কথা বলা হয়েছে। এই কথাগুলি থেকে মনে হতে পারে যে বেদের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে বেদের নিন্দা করা হয়নি। যারা বেদবাক্যের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না, তাদের নিন্দা করা হয়েছে।
আরও পড়ুন – নুন কবিতার বড় প্রশ্ন উত্তর