তিমির হননের গান কবিতার প্রশ্ন উত্তর | জীবনানন্দ দাশ | ক্লাস ১২ চতুর্থ সেমিস্টার | Class 12 timir hononer gaan kobitar long question answer | WBCHSE
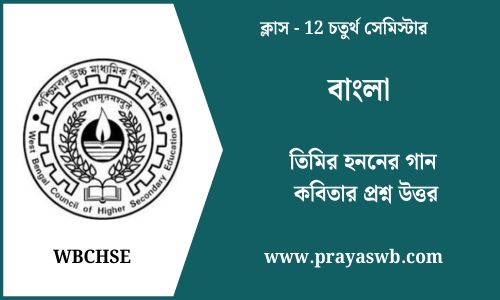
১। “হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।” -কার কথা বলা হয়েছে? কবির মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার উল্লিখিত অংশে প্রকৃতিলালিত মানবসভ্যতার আদিপর্বের মানুষদের কথা বলা হয়েছে।
পৃথিবীতে আদিপ্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল জলে। তারপর বিবর্তনের নানা জটিল পথ পেরিয়ে মানুষ এল। ইতিহাসের এক দীর্ঘ পরিসর জুড়ে মানুষের সভ্যতা ছিল প্রকৃতি-সংলগ্ন হয়ে। সমাজ সৃষ্টি হওয়ার পরে ‘সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে’ মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে সংযোগ তাও যেন ছিল সহজ, ‘জলের মতো’ অনায়াস। জীবনানন্দের অন্য কবিতার ভাষায় বলা যায়- “একদিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন এক আশ্চর্য আভা/ দেখা গিয়েছিল”। মানুষ সেই প্রকৃতির কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ অবাধ বিচরণ। জীবনের যা কিছু আলোড়ন সে আহরণ করেছিল প্রকৃতির কাছ থেকেই। প্রকৃতিই তাকে দিয়েছিল জীবনাচরণের শিক্ষা।
২। “সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো…” -কোন ‘সব রীতি’র কথা বলা হয়েছে? সেগুলি ‘মৃতের চোখের মতো’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২+৩
উত্তর: একদিন প্রকৃতির বুকে জীবন জেগে উঠেছিল। হ্রদে কিংবা নদীর ঢেউয়ে অথবা সমুদ্রের জলে মানুষ উপলব্ধি করেছিল জীবনের উচ্ছ্বাস, সংলগ্ন হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে। যখন মানবসমাজের সূচনা হয়েছিল সেই সময় থেকে প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ ‘অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে’ হাসি-খেলায় মেতে থেকেছে। প্রকৃতিলালিত সেই সভ্যতা তার জীবনধারার সন্ধান করেছিল প্রকৃতির মধ্যেই। তৈরি হয়েছিল ভালোবাসার ভিত্তিতে নিবিড় মানবিক সম্পর্ক। সেটাকে ‘তারা গ্রহণ করছিল স্মরণীয় গ্লানিহীন উত্তরাধিকার হিসেবে। ‘সেই সব রীতি’ বলতে এখানে মানুষের এই জীবনধারার কথা বলা হয়েছে।
প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, প্রকৃতির বুকে লালিত অমলিন জীবন নগরসভ্যতার যান্ত্রিকতায় ক্লান্ত অবসন্ন। নিরালোক মানুষদের জীবনে কোনো শান্তি সুস্থিতি নেই, আলো তার অন্বেষণে দূর নক্ষত্রের বিষয়। হেমন্তের প্রান্তরের মতো শূন্যতা বিরাজ করে যে নগর সভ্যতায়, সেখানে আলো কোনো নিকটবিষয় নয়। ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের ‘বিভিন্ন কোরাস’ কবিতাতে এই নির্বিকার নাগরিকদের বিষয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন- “বিকেলের বারান্দা থেকে সব জীর্ণ নরনারী/চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে;/খণ্ডহীন মন্ডলের মতো বেলোয়ারি।” নগরসভ্যতার এই যান্ত্রিকতায় ভেঙে পড়া পুরোনো মূল্যবোধ, বিপর্যস্ত পুরোনো জীবনধারাকেই কবি ‘মৃতের চোখের মতো’ বলেছেন।
৩। “সেই জের টেনে আজো খেলি।” -এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রোত্তর যুগের পুরোধা কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার উল্লিখিত অংশে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলা হয়েছে।
প্রকৃতির বুকে প্রাণের সৃষ্টি। প্রকৃতির কোলেই তার লালন। মানুষ এই প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল তার জীবনধারা। কোনো হ্রদে, নদীর ঢেউয়ে, কিংবা সমুদ্রের জলে সংলগ্ন থেকে তৈরি হয়েছিল মানুষের অনাবিল পারস্পরিক সম্পর্ক। তারপর মানুষ সমাজবদ্ধ হল, সেই সময়ে সেই সূচনা মুহূর্তেও শতাব্দীর সূর্যের নিকটে দাঁড়িয়ে তারা জীবনের আলোড়ন উপলব্ধি করেছিল, জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছিল। আকাশের কাছ থেকে উদারতা আর বিশালতার শিক্ষা নিয়ে নিজের দৃষ্টিকে করেছিল অন্য এক আকাশের মতো। এভাবেই জীবনের হাসি-খেলা-ভালোবাসায় তারা বহন করে এনেছিল গ্লানিহীন এক স্মরণীয় উত্তরাধিকার। কিন্তু যখন থেকে নগরজীবনের সূচনা হল, তখন থেকেই ধীরে ধীরে যান্ত্রিকতা গ্রাস করল মানুষের জীবনকে। সম্পর্কের অনাবিলতা, জীবনের স্বচ্ছন্দ পদচারণা বিনষ্ট হল। সেসব হয়ে উঠল ‘মৃতের চোখের মতো’। নিরালোক জীবন আলোর সন্ধান করল একমাত্র নক্ষত্রপথে। তবুও মানুষ কৃত্রিম হাসি, সম্পর্কের কৃত্রিম বুনোটে জীবনের উদ্যাপন করতে চাইল। সর্বরিক্ততার মধ্যে এইভাবে বিগত দিনের স্মৃতির অনুশীলন প্রসঙ্গেই কবি বলেছেন- ‘সেই জের টেনে আজো খেলি।’
৪। “সূর্যালোক নেই-তবুー/সূর্যালোক মনোরম মনে হ’লে হাসি।” -‘সূর্যালোক নেই’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২+৩
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘তিমিরহননের গান’ কবিতায় যান্ত্রিক নগরসভ্যতার অর্থহীন বেঁচে থাকার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে লালিত যে মানবজীবন একদিন অনাবিল এবং স্বচ্ছন্দ ছিল; সে জীবন বিগতপ্রায়। সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রথম পর্বে প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ শিখেছিল জীবনের সহজগতি। তাকে ভেবেছিল অনায়াস গ্লানিহীন স্মরণীয় উত্তরাধিকার। জীবনের হাসি-খেলা-ভালোবাসার মধ্যে ছিল তার অনায়াস উদ্যাপন। ‘সূর্যালোক নেই’ বলতে নাগরিক সভ্যতায় জীবনের এই সহজ উদ্ভাসনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ক্লান্ত অবসন্ন এবং আত্মিকভাবে রিক্ত নাগরিক মানুষ। যে প্রকৃতির সান্নিধ্য একদিন তার জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল করেছিল জীবনযাপনের সেই সব রীতি এখন ‘মৃতের চোখের মতো’। নিরালোক জীবন পারিপার্শ্বের সমাজে কোনো আলোর সন্ধান পায় না। তাই আলো খোঁজে দূরতম নক্ষত্রের পথে। যে জীবন হেমন্তের প্রান্তরের মতো সর্বরিক্ত সেখানে তারার আলোর খোঁজ চলে। আলোহীনতার অন্ধকারে জীর্ণ ক্লান্ত মানুষ অতীত থেকে আলো খোঁজে। সূর্যালোক না থাকলেও মনোরম সূর্যালোকের কথা ভেবে অবসন্ন মানুষ জীবনে হাসির সন্ধান করে।
৫। “স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্র সাধারণ/চেয়ে দ্যাখে….”-‘ভদ্র সাধারণ’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের বিমর্ষতার কারণ কী? তারা কী দেখে? ১+২+২
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার আলোচ্য পঙ্ক্তিতে ‘ভদ্র সাধারণ’ বলতে মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের কথা বলা হয়েছে।
নগরজীবনের জটিলতা এবং যান্ত্রিকতা নির্মল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। যে প্রকৃতির আশ্রয়ে একদা প্রাণ জেগে উঠেছিল, সমাজ গড়ে ওঠার পরে যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষকে, তার জীবনধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল-পরবর্তীতে নগরসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষদের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। জীবনের যে অনাবিলতা প্রকৃতির কাছ থেকে শিখে মানুষ হাসি-খেলা-ভালোবাসায় মেতে উঠেছিল, তার অভাবে আলোহীন হয়ে যায় মানুষের জীবন। কৃত্রিম জীবনে মানুষ আনন্দ খোঁজে কৃত্রিমভাবে। কিন্তু এর ফলেই এক সার্বিক বিষণ্ণতা এবং বিমর্ষতা ঘিরে রাখে মানবসমাজকে।
বিমর্ষ মধ্যবিত্ত আর-এক অশান্ত সময়ে যখন চোখ মেলে দেখতে পায় অধিকতর বিষণ্ণতার ছবি। “… সেই বিষাদের চেয়ে/আরো বেশি কালো-কালো ছায়া”। দুর্ভিক্ষের কারণে ছিন্নমূল গ্রামের মানুষেরা শহরে ভিড় করে। লঙ্গরখানায় খাবারের জন্য লাইন দেয়। নর্দমা থেকে ওভারব্রিজ-এইসব স্থান মানুষগুলোর ঠিকানা হয়। ‘ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে’ ছিন্নমূল এইসব মানুষেরা তারাভরা আকাশের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা মরে যায়। এই অপার বিষণ্ণতা অতিক্রম করে যায় মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনা ও নৈরাশ্যের সমস্ত হিসাব।
৬। “নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম’রে যেতে জানে।” -কাদের কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ২+৩
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার উদ্ধৃত অংশে দুর্ভিক্ষের কারণে ছিন্নমূল শহরে ভিড় করে আসা গ্রামের মানুষদের কথা বলা হয়েছে।
১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর বাংলার সমাজজীবনে নারকীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে ভিখারিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে নাগরিক বাঙালিসমাজ বিপর্যস্ত হয়েছিল মূল্যবোধের অভাব, জীবনযাপনের যান্ত্রিকতা, ক্লান্তি এবং অবসন্নতায়। ব্যক্তিমানুষের এই সংকটের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ যুক্ত করল সামাজিক সংকটের এক মর্মান্তিক ছবি। মধ্যবিত্তের ব্যক্তিসংকটের থেকেও, তার জীবনের ব্যাপ্ত বিষণ্ণতার থেকেও ‘আরো বেশি কালো-কালো ছায়া’ ভিড় করে শহরের রাজপথে। সেই ভিড়কে দেখা যায় খাদ্যের সন্ধানে লঙ্গরখানায়। নর্দমা থেকে ওভারব্রিজ-হয়ে থাকে এইসব অপাঙ্ক্তেয় মানুষদের আশ্রয় এবং বিচরণক্ষেত্র। ‘নিরুত্তর ফুটপাত’, যা দিতে পারে না অনিশ্চিত বেঁচে থাকার কোনো সমাধান। সেখানেই তারাভরা আকাশের তলায় তারা ঘুমিয়ে পরে কিংবা মারা যায়। এভাবেই তৈরি হয় ইতিহাসের ‘অন্তহীন বেদনার’ পথ।
৭। “আমরা বেদনাহীন-অন্তহীন বেদনার পথে।” -‘আমরা’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? কেন তারা ‘বেদনাহীন-অন্তহীন বেদনার পথে’? ২+৩
উত্তর: জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার উল্লিখিত অংশে ‘আমরা’ বলতে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলা হয়েছে।
নগরসভ্যতার পত্তনের পর থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ক্রমিক বিচ্ছেদ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আসে ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা। মূল্যবোধের ভাঙন, যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি অবসন্নতায় বিপন্ন মানুষদের কাছে নির্মল মানবিক সম্পর্ক, প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস ইত্যাদি বিগত দিনের স্মৃতি হয়ে যায়। “সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু-” এরই মধ্যে মিথ্যা সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চায় অবসন্ন মধ্যবিত্ত। শূন্য হেমন্তের প্রান্তরে কোনো আলো না পেয়ে তারার আলোর সন্ধান করে মানুষ। সময়ের সংকট তীব্রতর হয় দুর্ভিক্ষের তাড়নায়। কিন্তু লঙ্গরখানায় খাবারের সন্ধানে লাইন দেওয়া কিংবা ফুটপাতে বেঘোরে মরে যাওয়ার দৃশ্যও বিচলিত করতে পারে না আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজকে। সীমাহীন নেতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হেসে যায় ‘সূর্যালোক প্রজ্ঞাময়’ মনে করে। ‘অন্তহীন বেদনার পথে’-ও এই ‘মধ্যবিত্তমদির জগতে’ নাগরিক মানুষ বেদনাহীন হয়ে থাকে, যা আসলে তার আত্মপ্রতারণা, সত্যবিমুখতা এবং সমাজবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন হয়ে থাকে।
৮। “মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।” কারা এ কথা বলেছে? এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর: রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার আলোচ্য পঙ্ক্তিতে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।
নগরজীবনের জটিলতা এবং যান্ত্রিকতায় মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে একদিন প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে অর্জিত জীবনের সহজ অনাবিলতা। নিরালোক জীবনে বিমর্ষতাই একমাত্র সত্য। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত বিষণ্ণতাকে ছাপিয়ে যায় ঘনিয়ে আসা সামাজিক অন্ধকার। দুর্ভিক্ষের প্রবল অভিঘাতে ছিন্নমূল মানুষেরা ভিড় করে শহরের রাজপথে। লঙ্গরখানায় খাবারের জন্য তারা লাইন দেয়। নর্দমা থেকে শূন্য ওভারব্রিজ হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয়স্থল। ‘নিরুত্তর ফুটপাতে’ তারা ঘুমায় এবং একসময় মরে যায়। কিন্তু জীবনের এই ‘অন্তহীন বেদনার পথ’ মধ্যবিত্তকে ছুঁতে পারে না। তারা নিজেদের ভালো থাকার জন্য তৈরি করে নেয় আত্মপ্রবঞ্চনার এক বৃত্ত। সেখানে কোনো সূর্যালোক না থাকলেও তাকে প্রজ্ঞাময় মনে করে হেসে যায়। মহানগরী তাদের কাছে ‘জীবিত বা মৃত রমণী’ যেভাবেই প্রতীয়মান হোক-না-কেন, তার থেকে সুগন্ধ খুঁজে নিতেই সক্রিয় থাকে এইসব মানুষেরা। এক ভয়ংকর আত্মরতি ঘিরে থাকে তাদের জীবনকে।
৯। “তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ’য়ে/আমরা কি তিমিরবিলাসী?” -কবির মনে এই সংশয়ের কারণ কী? এবিষয়ে কবির অভিমত আলোচনা করো। ২+৩
উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপনের যান্ত্রিকতা এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা জীবনানন্দ দাশের ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার অন্যতম প্রেক্ষাপট। যে মানুষ একদিন প্রকৃতির বুকে আশ্রয় নিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল তার স্বচ্ছন্দ সহজ অনাবিল জীবনধারা; নাগরিক জীবনে সে সেই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে প্রসারণশীলতা ছিল তার জীবনধর্ম, তার পরিবর্তে আসে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং তা এতটাই তীব্র যে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিরাশ্রয়তা, লঙ্গরখানায় খাদ্যের জন্য লাইন, ফুটপাতে বেঘোরে মৃত্যু ইত্যাদি কোনোকিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারে না। এমন এক মদির জগতে মধ্যবিত্তের বিচরণ, যেখানে ‘অন্তহীন বেদনার পথে’ দাঁড়িয়েও তারা বেদনাহীন থাকে। তাৎপর্যহীন জীবনে একদা ছিল যে অনাবিল সুন্দর জীবন, যা বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে, তার জের টেনে সে হেসে যায়। কিন্তু এই আত্মপ্রবঞ্চনা কবির কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, সভ্যতা মানুষের কাছে প্রথমত এবং প্রধানত প্রত্যাশা করে মনুষ্যত্ব। তা না দেখতে পেয়েই কবির মনে প্রশ্নোল্লিখিত সংশয় তৈরি হয়েছে।
সমস্ত যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারে চলতে চলতে জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত স্থিত হতে চেয়েছেন অমলিন আশাবাদের। গভীর প্রত্যয়ে অন্তর্দীপ্ত কবি তাই ভরসা করেছেন মানুষের অন্তর্গত বোধ এবং প্রত্যয়ে। -“আমরা তো তিমিরবিনাশী/হ’তে চাই।/আমরা তো তিমিরবিনাশী।” লক্ষণীয় প্রথমে তিমিরবিনাশী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও অন্তিম পঙ্ক্তিতে তা প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কবি জানিয়ে দিয়েছেন “আমরা তো তিমিরবিনাশী।” কোনো সংশয় অথবা প্রশ্ন নেই। সর্বমানবের হয়ে কবির এই উচ্চারণ। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এই উচ্চারণ আসলে মনুষ্যত্বের দৃপ্ত অঙ্গীকার।
১০। ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার নামকরণের মধ্যে যে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করো।
উত্তর: জীবনানন্দের ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এক অমলিন আশাবাদ। কবিতার বিষয়বস্তুর চূড়ান্তে এই আশাবাদেরই প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়।
সুদূর অতীতের এক জীবনচর্যার ছবি দিয়ে কবিতার সূচনা। সে জীবন কোনো হ্রদে, নদীর ঢেউয়ে বা সমুদ্রের জলে জেগে ওঠার। প্রকৃতির কোলে জেগে ওঠা সে জীবন যখন সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার বৃত্তে এল তার প্রাথমিক পর্যায়ে সে একইভাবে প্রকৃতির থেকে অর্জিত সহজ অনাবিল জীবনধারার গ্লানিহীন উত্তরাধিকার বহন করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের সেই সহজ বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। একদিকে যান্ত্রিকতা, অন্যদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয় জীবনকে ধূসর বিবর্ণ করে তুলল। আনন্দ-হাসি বিবর্জিত জীবনে মানুষ ভালো না থাকলেও কৃত্রিম ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে থাকে। আত্মপ্রসারণের বদলে তৈরি হয় আত্মপ্রবঞ্চনার চিত্রনাট্য এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় মধ্যবিত্তের শ্রেণি ও ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতা। যে কারণে দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিন্নমূল মানুষদের লঙ্গরখানায় লাইন দিতে দেখে কিংবা ফুটপাতে মরে যেতে দেখেও তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। ‘অন্তহীন বেদনার পথে’-ও নার্সিসিস্ট বা আত্মমুগ্ধ মধ্যবিত্ত তাই নিজেকে ‘বেদনাহীন’ ভাবে। মানবতার এই অবক্ষয় কবির মনে সংশয় তৈরি করে। প্রকৃতির কোলে জেগে ওঠা সে জীবন যখন সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার বৃত্তে এল তখন তার প্রাথমিক পর্যায়ে সে একইভাবে প্রকৃতির থেকে অর্জিত সহজ অনাবিল জীবনধারার গ্লানিহীন উত্তরাধিকার বহন করেছিল। “তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ’য়ে/আমরা কি তিমিরবিলাসী?” শেষপর্যন্ত নিজেই সমস্ত মানুষের হয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন-“আমরা তো তিমিরবিনাশী/হ’তে চাই।” কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে এই ইচ্ছা ঘোষণায় রূপান্তরিত হয়-“আমরা তো তিমিরবিনাশী।” এভাবেই সমস্ত সংশয়কে অতিক্রম করে কবি মনুষ্যত্বকে ভরসা করেছেন। কারণ সেটাই তিমিরহননের একমাত্র শক্তি। এভাবেই জীবনানন্দের পঠিত কবিতায় আশাবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
১১। তিমিরহননের পথেই মানুষ বাববার কেন ফিরে আসে ‘তিমিরহননের গান’ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
উত্তর : জীবনানন্দের ‘তিমিরহননের গান’ কবিতার বিষয়বস্তুর চূড়ান্ত উপসংহারে এক অমলিন আশাবাদেরই প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়।
সুদূর অতীতের যে জীবনচর্যার ছবি কবিতার সূচনায় কবি এঁকেছেন তা জীবনের জাগরণের। কোনো হ্রদে, নদীর ঢেউয়ে বা সমুদ্রের জলে, এককথায় প্রকৃতির কোলে জেগে ওঠে সে জীবন। মানবসমাজ গঠনের সূচনাতেও মানুষ সেই অনাবিল জীবনধারার গ্লানিহীন উত্তরাধিকার বহন করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একদিকে যান্ত্রিকতা, অন্যদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয় সেই সহজ বেঁচে থাকাকে অসম্ভব করে তুলল। আনন্দ-হাসি বিবর্জিত সেই ধূসর বিবর্ণ জীবনে মানুষকে ভালো না থেকেও ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে দেখা গেল। তার সঙ্গে যুক্ত হল মধ্যবিত্তের শ্রেণি ও ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিকতা। তাই দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিন্নমূল মানুষদের লঙ্গরখানায় লাইন দিতে দেখে কিংবা ফুটপাতে মরে যেতে দেখেও তারা অনায়াসে প্রতিক্রিয়াহীন থাকত। ‘অন্তহীন বেদনার পথে’-ও সে মধ্যবিত্ত নিজেকে ‘বেদনাহীন’ ভাবে।
যে মানুষের অন্ধকার দূর করার কথা ছিল অন্ধকারের কাছেই তার আত্মসমর্পণ কবিকে সংশয়ী করে তোলে। “তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ’য়ে/আমরা কি তিমিরবিলাসী?” শেষপর্যন্ত নিজেই সমস্ত মানুষের হয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন-“আমরা তো তিমিরবিনাশী/হ’তে চাই।” সমস্ত সংশয়কে অতিক্রম করে কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে কবির ইচ্ছা ঘোষণায় রূপান্তরিত হয়- “আমরা তো তিমিরবিনাশী।” সংশয়হীন প্রত্যয়ে এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই।
১২। ‘তিমিরহননের গান’ কবিতাটি কোন্ প্রেক্ষাপটে লেখা? কবি কেন ‘তিমিরবিলাসী’ নয়, ‘তিমিরবিনাশী’ হতে চেয়েছেন? ২+৩
উত্তর: ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর বাংলার সমাজজীবনে নারকীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে ভিখারিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে নাগরিক বাঙালিসমাজ বিপর্যস্ত হয়েছিল মূল্যবোধের অভাব, জীবনযাপনের যান্ত্রিকতা, ক্লান্তি এবং অবসন্নতায়। ব্যক্তিমানুষের এই সংকটের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ যুক্ত করল সামাজিক সংকটের এক মর্মান্তিক ছবি। মধ্যবিত্তের ব্যক্তিসংকটের থেকেও, তার জীবনের ব্যাপ্ত বিষণ্ণতার থেকেও ‘আরো বেশি কালো-কালো ছায়া’ ভিড় করে শহরের রাজপথে। এই প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দ দাশ রচনা করেছেন ‘তিমিরহননের গান’ কবিতাটি।
সমস্ত যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারে চলতে চলতে জীবনানন্দ শেষপর্যন্ত স্থিত হতে চেয়েছেন অমলিন আশাবাদের। গভীর প্রত্যয়ে অন্তর্দীপ্ত কবি তাই ভরসা করেছেন মানুষের অন্তর্গত বোধ এবং প্রত্যয়ে। “আমরা তো তিমিরবিনাশী/হ’তে চাই।/আমরা তো তিমিরবিনাশী।” লক্ষণীয় প্রথমে তিমিরবিনাশী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও অন্তিম পঙ্ক্তিতে তা প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কবি জানিয়ে দিয়েছেন “আমরা তো তিমিরবিনাশী।” কোনো সংশয় অথবা প্রশ্ন নেই। সর্বমানবের হয়ে কবির এই উচ্চারণ। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এই উচ্চারণ আসলে মনুষ্যত্বের দৃপ্ত অঙ্গীকার।