Holud Pora Golper Question answer (Manik Bandyopadhyay) Class 12 Semester 4th | হলুদ পোড়া গল্পের বড়ো প্রশ্ন উত্তর ক্লাস 12 বাংলা চতুর্থ সেমিস্টার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
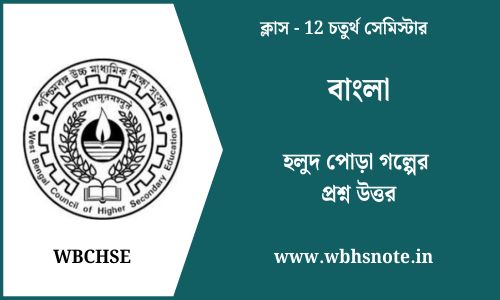
১। “মানুষের মত কি যেন একটা নড়াচড়া করছে।” -কে কোথায় দৃশ্যটি দেখেছিল? প্রকৃত ঘটনাটি কী ছিল?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে পড়ন্ত বিকেলে ধীরেন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এল, ডোবার ধারে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় সে মানুষের মতো কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখেছিল।
সমস্ত দুপুর ঘরের মধ্যে কাটিয়ে শেষবিকেলে ধীরেন যখন উঠোনে বেরিয়ে এসেছিল সেই সময়ে তার স্ত্রী শান্তি মাজা বাসন হাতে নিয়ে ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় মানুষের মতো কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখে ধীরেন আর্তনাদ করে ওঠে এবং সেখানে কে তা জানতে চায়। বোঝা যায় যে তার অবচেতনে কাজ করে যায় ওই ডোবার ঘাটে শুভ্রার খুন হওয়ার ঘটনা। শান্তির হাত থেকে সেই চিৎকারে বাসন পড়ে যায়। বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে কোনো চেনা কণ্ঠস্বর উত্তর দেয় যে সে বাঁশ কাটছে। শান্তি জানায় যে, বাঁশ কাটার নির্দেশ সে-ই দিয়েছে। কারণ, ক্ষেন্তিপিসি বলেছে যে, নতুন একটা বাঁশ কেটে তার আগা-মাথা পুড়িয়ে ঘাটের পথে সন্ধ্যার আগে ফেলে রাখতে। অশরীরী শক্তির অনুপ্রবেশ ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠোনে উঠে আসতে চায় সেই ‘বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে’। শান্তি ধীরেনকে সতর্ক করে সে যাতে ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে না যায়।
২। ধীরেনের বাড়িতে শুভ্রার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যা যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর:: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে শুভ্রার মৃত্যু খুব স্বাভাবিকভাবেই সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল ধীরেনকে। সাত মাসের গর্ভবতী বোনের জন্য সে পুকুরে ঘাট বানিয়ে দিয়েছিল, আর সেখানেই খুন হয়েছিল শুভ্রা। খুনী কে, কীভাবে সেখানে এল, তার উদ্দেশ্য কী ছিল-এইসব নিয়ে ধীরেন যথেষ্ট ভাবিত ছিল। অন্যদিকে আর-এক খুন হওয়া চরিত্র বলাই চক্রবর্তীর সঙ্গে শুভ্রাকে জড়িয়ে যে কলঙ্কিত কাহিনি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গ্রামবাসীদের তরফ থেকে চলছিল তা ধীরেনের মানসিক শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে দেয়। সে নিজেকে তার কর্মক্ষেত্র এবং সমাজ-পারিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে শুরু করে।
ধীরেনের স্ত্রী শান্তি ভয়ে বাঁশ কেটে তার দু-প্রান্ত পুড়িয়ে ঘাটের পথে ফেলে রাখার পরিকল্পনা করেছিল যাতে তা ডিঙিয়ে অশরীরী আত্মা অনুপ্রবেশ না করতে পারে। সন্ধ্যার আগেই সে ইদানীংকালে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরে ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড়ো ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে।
তাদের ছেলেমেয়েরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, -“ছোটোপিসি ভূত হয়েছে।” তাদেরই মধ্যে কেউ সংশোধন করে দেয় যে ভূত নয়, পেত্নী হয়েছে। এভাবে পরিবারের সকলের ভাবনাচিন্তার কেন্দ্রে থেকে যায় অকালে খুন হয়ে যাওয়া শুভ্রা।
৩। “আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।” -কার, কখন এ কথা মনে হয়েছিল? এজন্য তাকে কী করতে দেখা গিয়েছিল?
ত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে শুভ্রার দাদা ধীরেনের উল্লিখিত ভাবনাটি হয়েছিল। দিনের অবসানে তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু তখনও মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা আকাশে স্পষ্ট দৃশ্যমান। রাত্রি অপেক্ষমান। এরকম সময়েই ধীরেনের মনে হয় যে, জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগস্থাপনের সবথেকে প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যা। এরপরে রাত্রি নেমে এলে শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তাই দেরি না করে শুভ্রাকে সুযোগ করে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে ধীরেন।
শুভ্রার সঙ্গে কথা বলার জন্য চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। কিছু পরে এক অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে ধীরেনের স্ত্রী শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দেখে যে, বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তার গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা আর রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ধীরেন শান্তিকে বাঁশ সরিয়ে নিতে বলে কারণ সে সেই বাঁশ ডিঙোতে পারছিল না।
৪। “শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না।” -কোন্ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না? এর প্রতিক্রিয়া কী ঘটেছিল?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে ধীরেনকে দেখে তার স্ত্রী শান্তির সন্দেহ ছিল না যে, কোনো অশরীরী আত্মা তাকে ভর করেছে।
গোপনে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীরেন চলে গিয়েছিল ডোবার দিকে। উদ্দেশ্য ছিল তার অকালে খুন হয়ে যাওয়া বোন শুভ্রার সঙ্গে কথা বলা। যখন সে ফিরে আসে তার গেঞ্জি আর কাপড় কাদায় রক্তে মাখামাখি। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ধীরেন শান্তিকে বাঁশ সরিয়ে নিতে বলে কারণ সে সেই বাঁশ ডিঙোতে পারছিল না। এই বাঁশ শান্তিই দুই প্রান্ত আগুনে পুড়িয়ে পেতে রেখেছিল যাতে কোনো অশরীরী অনুপ্রবেশ করতে না পারে। ধীরেন তা পেরোতে না পারায় শান্তি নিশ্চিত হয়ে যায় যে অশরীরী আত্মা তাকে ভর করেছে। প্রচণ্ড ভয়ে সে তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে। প্রতিবেশী এবং গ্রামের লোকেরা ছুটে আসে। কুঞ্জও চলে আসে। তিন-চার কলশি জল ঢেলে তাকে স্নান করিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়। ঠিক যেমন এর আগে দামিনীর সঙ্গে করা হয়েছিল সেরকমই মন্ত্র পড়া, জলছিটানো, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়োনো ইত্যাদির মাধ্যমে ধীরেনকে নিস্তেজ করে ফেলা হয়। তারপরে মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে কুঞ্জ বজ্রকণ্ঠে তার পরিচয় জানতে চায়। এবং ধীরেনের তরফ থেকে উত্তর আসে যে সে বলাই চক্রবর্তী, সে-ই শুভ্রাকে খুন করেছে।
৫। হলুদ পোড়া’ গল্পে ধীরেন চরিত্রের যে রূপান্তর লক্ষ করা যায় তা আলোচনা করো।
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটিতে অন্ধবিশ্বাস এবং সংস্কারকে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া ভৌতিক আবহে অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ধীরেন চরিত্রের বিবর্তন।
ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাস করা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শুভ্রার দাদা ধীরেন পাস করা না হলেও বিনামূল্যে ডাক্তারিও করত। অর্থাৎ তার মানসিক ঝোঁক ছিল বিজ্ঞানের প্রতি। লাইব্রেরি তৈরি, তরুণ সমিতি গঠন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চা ও মুক্তভাবনার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। আর সে কারণেই অসুস্থ দামিনীর চিকিৎসার জন্য তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলে ধীরেন নিজে দায়িত্ব না নিলেও কৈলাশ ডাক্তারকে ডাকার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় সে কুঞ্জ গুনিনকে ডেকে আনার প্রস্তাবেরও তীব্র বিরোধিতা করে। নবীনকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, লেখাপড়া শিখে, জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হয়ে কুঞ্জকে ডেকে পাঠানো ‘দুর্বুদ্ধি’ ছাড়া আর কিছুই নয়।
ভূত তাড়ানোর নামে যখন দামিনীকে অত্যাচার করা হচ্ছিল ধীরেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এহেন ধীরেনকে সম্পূর্ণ অন্য রূপে দেখা যায় কাহিনির শেষ অংশে। বোন শুভ্রার খুন হয়ে যাওয়া তার মনে প্রবল চাপ তৈরি করে। আবার গ্রামের লোকদের কথাবার্তা তাতে ইন্ধন জোগায়। চারপাশের পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সে। সন্ধ্যা নামলেই শুভ্রার সঙ্গে কথা বলার জন্য ধীরেন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। নীরবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। যখন ফিরে আসে তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম চেহারা তার। গেঞ্জি আর কাপড় রক্তমাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। প্রায় জান্তব চিৎকারে সে নিজের নাম ধরে ডাকতে থাকে। আর গুনিন কুঞ্জর মন্ত্র ও ক্রিয়াকর্ম প্রয়োগের পরে সে জানিয়ে দেয় যে সে-ই বলাই চক্রবর্তী এবং সে শুভ্রাকে খুন করেছে। ধীরেনের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অন্ধবিশ্বাসের অভিঘাতে আগ্রাসী সমাজমানসিকতার কাছে আত্মিক-সংকটের সূত্র ধরে অসহায় আত্মসমর্পণ।
৬। ‘হলুদ পোড়া’ গল্পের কুন্তু চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখাও।
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটিতে মানুষের আদিম বিশ্বাস এবং অন্ধসংস্কারের যে সর্বব্যাপ্ত চেহারাকে তুলে ধরা হয়েছে কুঞ্জ সেই ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে।
অন্ধবিশ্বাসের ভরকেন্দ্র: নবীনের স্ত্রী দামিনী অসুস্থ হলে বৃদ্ধ পঙ্কজ ঘোষাল ডাক্তার ডাকার বদলে কুঞ্জকে ডাকার পরামর্শ দেন। সেখানে উপস্থিত গ্রামের সকলেই তাতে সম্মতি দেয়। ধীরেন তীব্র আপত্তি করলেও কুঞ্জ উত্তর দেয়-” এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয়।” বোঝা যায় নিজেদের অন্ধবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশে কুঞ্জকে আশ্রয় করতে চেয়েছে সকলে।
পেশাগত তৎপরতা: কুঞ্জর পেশাগত তৎপরতা স্পষ্ট করে দেয় যে কেন তার প্রতি মানুষের আস্থা। দামিনীকে দেখেই কুঞ্জ বলেছিল যে ভরসন্ধ্যায় তাকে অশরীরী ভর করেছে। সেই সঙ্গেই অশরীরীকে প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কুঞ্জ বলে যে, তাকে ছেড়ে যেতেই হবে, “কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।” কুঞ্জর মন্ত্র পড়া, দামিনীর চুল খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, নাকে হলুদ পোড়া শোঁকানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কুঞ্জ গ্রামসমাজে অন্ধ-সংস্কারের বহমানতার অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে এবং তার প্রভাবেই দামিনীর মুখ দিয়ে অশরীরী শুভ্রা নিজের উপস্থিতির স্বীকারোক্তি করে, সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেয় যে, বলাই চক্রবর্তী তাকে খুন করেছে। একইভাবে পরে ধীরেনও জানিয়ে দেয় যে সে বলাই চক্রবর্তী এবং সে-ই শুভ্রাকে খুন করেছে।
উপসংহার: কৈলাস ডাক্তার নবীনের বাড়িতে কুসংস্কারের প্রতীক কুঞ্জকে গালাগালি দিয়েছে, তার আগুনের মালসা লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষের কুঞ্জর প্রতি আস্থাকে টলাতে পারেনি। এবং কাহিনির শেষে ধীরেন যখন নিজেকে বলাই চক্রবর্তী বলে আর সেখানেও হলুদ পোড়া শোঁকায় কুঞ্জ, তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় গণমানসের অন্ধকারের পুরোহিত কুঞ্জ। তার সমালোচনা যেমন অনিবার্য, উপস্থিতি তেমনই অনস্বীকার্য।
৭। ” ‘হলুদ পোড়া’ একটি সংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীসমাজের ভৌতিক বিশ্বাসের গল্প।”-‘হলুদ পোড়া’ গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি ঘটনা ও চরিত্রের আপাতবিন্যাসে গ্রামজীবনে মানুষের মনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিনিধিত্ব করে, যার পটভূমি নিঃসন্দেহে ভৌতিক।
মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে দুটি খুন এবং তাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজের সংস্কারগ্রস্ত গণমানসের নিবিড় উন্মোচন ঘটেছে এই গল্পে। বলাই চক্রবর্তী খুন হওয়ার তিন দিন পরে খুন হয় গ্রামের মেয়ে ষোলো-সতেরো বছরের শুভ্রা। বিবাহিতা শুভ্রা বাবার বাড়িতে এসেছিল তার সন্তান হবে বলে। বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যু গ্রামের লোকদের কাছে বিস্ময়ের না হলেও শুভ্রার মৃত্যু তাদের বিচলিত ও বিস্মিত করে। কাহিনিতে ভৌতিক আবহের সূচনা হয় প্রথম যখন বলাই চক্রবর্তীর উত্তরাধিকারী তার ভাইপো নবীনের স্ত্রী দামিনীর গায়ে সন্ধ্যাবেলা বাতাস লাগে। তেঁতুলগাছ থেকে বাহিত মৃদু অথচ দমকা বাতাস গায়ে লেগে ভীত দামিনী অচেতন হয়ে যায়। সেই সূত্র ধরে কাহিনিতে প্রবীণ পঙ্কজ ঘোষালের পরামর্শমত এবং গ্রামের মানুষদের সোৎসাহ সমর্থনে কুঞ্জ গুনিনের আবির্ভাব ঘটে। ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষক এবং ডিগ্রিহীন চিকিৎসক ধীরেনের আপত্তি গ্রাহ্য হয় না। মন্ত্রতন্ত্র, আচার-আচরণের যে প্রয়োগ দামিনীর উপরে ঘটে, উপস্থিত দর্শকরা যেভাবে সে দৃশ্য উপভোগ করে তার মধ্যে সমাজে সর্বব্যাপ্ত অন্ধসংস্কারই প্রতিফলিত হয়। দামিনী যখন বলে যে সে শুভ্রা এবং বলাই চক্রবর্তী তাকে খুন করেছে তখন যেন গণমানসের প্রত্যাশাই মান্যতা পেয়ে যায়। পঙ্কজ ঘোষাল কিংবা কুঞ্জ তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে দেয়। কিন্তু এই ভৌতিক আবহ তীব্রতম রূপ পায় যখন গল্প শেষে ধীরেন বলাই চক্রবর্তীর আত্মার বাহক হয়ে যায়। এবং জানায় যে, সে শুভ্রাকে খুন করেছে। ব্যক্তিমনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাস একসময়ে সামাজিক অন্ধত্বের সামনে নিজেকে উন্মোচিত করে দিতে বাধ্য হয়।
৮। “হলুদ পোড়া’-সংস্কারের আবর্তে মনসত্ত্বের জয়ধ্বজা।” -কাহিনি বিশ্লেষণ করে মন্তব্যটির যথার্থতা আলোচনা করো।
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি আপাতভাবে এক ভৌতিক আবহকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তিন দিনের ব্যবধানে দুটি মৃত্যু। শুভ্রা চাটুজ্জে আর বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুতে গ্রামের লোকেরা যখন বিচলিত, বিশেষভাবে শুভ্রার মৃত্যুতে, সেইসময় একদিন নবীনের স্ত্রী দামিনীর গায়ে বাতাস লাগে এবং কুঞ্জ গুনিন সিদ্ধান্তে যায় যে, তাকে অশরীরী আত্মা ভর করেছে। মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ, কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে শোঁকানোর পরে দামিনীর মুখ থেকে শোনা গেল সেই অশরীরীর কণ্ঠস্বর, যে সে শুভ্রা আর বলাই চক্রবর্তী তাকে খুন করেছে। ঠিক একইভাবে কাহিনির শেষ অংশে ধীরেনের মুখে শোনা যায় আর-এক অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর তা হল সে বলাই চক্রবর্তী এবং সেই শুভ্রাকে খুন করেছে। অসম্ভবের এইটুকু বিন্যাস ছাড়া বাকি সবটাই চরিত্রদের মনোলোকের উন্মোচন এবং টানাপোড়েন। আর তার পরতে পরতে থাকে অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারের আদিম অন্ধকারে ডুবে থাকা ব্যক্তিমন এবং সমাজমন।
ধীরেন চাটুজ্জে যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মসমর্পণ করে এই অন্ধবিশ্বাসের কাছে। সমাজমনের প্রবল চাপ হয়তো কার্যকর থাকে তার অবচেতন থেকে উঠে আসা আদিম কণ্ঠস্বরে, সে বলে আমি বলাই চক্রবর্তী, আমি শুভ্রাকে খুন করেছি। পঙ্কজ ঘোষালের অন্ধবিশ্বাস, ক্ষেন্তি পিসির ভূত আটকানোর দাওয়াই, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক থেকে ছাত্রদের আচরণের পালটে যাওয়া আসলে সংস্কারে আটকে যাওয়া সমাজমনের বহিঃপ্রকাশ। এই মানসিকতার পৌরোহিত্য করে কুঞ্জ। তাই চূড়ান্ত বিচারে হলুদ পোড়া কোনো ভূতের গল্প নয়। অবচেতনের অন্ধকার থেকে উঠে আসা সংস্কার-নির্ভর মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ।
৯। ছোটোগল্প হিসেবে ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি কতদূর সার্থক তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ ছোটোগল্পটি তার আয়তনে আপাতভাবে ছোটোগল্পের প্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ততার শর্তকে কিছুটা হলেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু তার সূচনা ছোটোগল্পের প্রত্যাশিত আকস্মিকতা দিয়ে। “সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দু’দুটো খুন হয়ে গেল।” এই ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমেই পাঠক চমকে ওঠে। কাহিনির সমাপ্তিতেও থাকে একই রকম আকস্মিকতা। ধীরেন বলে, “আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” ধীরেন চরিত্রের পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু পাঠক যখন এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে তখনই কাহিনি শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, ঘটনাক্রম-এই সমস্ত কিছুর জন্য উৎকণ্ঠা জারি রেখে গল্পের সমাপ্তি ঘটে।
ছোটোগল্পে চরিত্র সংখ্যা কম থাকে। ‘হলুদ পোড়া’ গল্পেও দেখা যায় মূল চরিত্র মূলত ধীরেন, কুঞ্জ, এবং কিছুটা নবীন, দামিনী, কিংবা কুঞ্জর স্ত্রী শান্তি। বিচ্ছিন্নভাবে আরও কিছু চরিত্র থাকলেও তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত ক্ষণ পরিসরে। তবে ‘হলুদ পোড়া’ গল্পের মূল স্বাতন্ত্র্য তার কাহিনি বিন্যাসে। যেভাবে একটা আপাত ভৌতিক গল্পের কাঠামো নির্মাণ করে এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মুছে দিয়ে দুটি চরিত্রের অতিপ্রাকৃত রূপান্তর ঘটিয়েছেন লেখক, সেখানে নিশ্চয়ই আপাত ভৌতিক গল্পের কাঠামোর মধ্য দিয়ে সমাজ মনস্তত্বের তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামের মানুষদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের প্রত্যাশা, কুসংস্কারকেন্দ্রিক সমাজের বিনির্মাণ সেখানে লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেনের অতিপ্রাকৃত রূপান্তর কিংবা কৈলাস ডাক্তারের প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত কুঞ্জ গুনির কাছে হেরে যাওয়া আসলে একটা গোটা সমাজের মানসিকতারই প্রতিফলন। লেখক এখানে কোনো লোকশিক্ষার দায়িত্ব নেননি, শুধু সমাজমনস্তত্ত্বের রূপদান করায় তার লক্ষ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে ‘হলুদ পোড়া’ ছোটোগল্প হিসেবে নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে।
আরো পড়ুন : স্বাধীনতার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কমিশনসমূহ MCQ প্রশ্ন উত্তর
আরো পড়ুন : মহান শিক্ষকগণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অবদানসমূহ MCQ প্রশ্ন উত্তর