আঞ্চলিক শক্তির উত্থান | অষ্টম শ্রেণি ইতিহাস প্রথম অধ্যায়
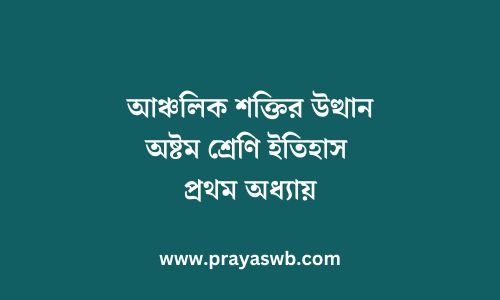
‘ব্রিটিশ রেসিডেন্স’ ব্যবস্থা কী? রেসিডেন্টদের ভূমিকা বা কাজ কী ছিল?
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলেও ক্রমে তা একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তখন থেকেই রেসিডেন্স ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ভারতে কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারে রেসিডেন্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রেসিডেন্স ব্যবস্থা
রেসিডেন্ট বলতে বোঝায় প্রতিনিধি ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধিরা যে স্থানে থাকতেন সেই স্থান বা বাসভবনকে বলা হত রেসিডেন্সি। কোম্পানি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে বিভিন্ন দেশীয় শাসকদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইসব শাসকদের দরবারে একজন করে কোম্পানির প্রতিনিধি থাকতেন। এরাই হলেন রেসিডেন্ট। আর কোম্পানির স্বার্থরক্ষার জন্য গড়ে তোলা এই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ রেসিডেন্স ব্যবস্থা।
রেসিডেন্টদের ভূমিকা বা কাজ
বক্সারের যুদ্ধের পর বিজয়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাবের দরবার মুর্শিদাবাদ ও অযোধ্যার নবাবের দরবার লখনউতে রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। এই রাজ্যগুলিতে কোম্পানি ও ইংরেজদের সঙ্গে নবাবদের কাজকর্মের উপর নজরদারি চালাত এই রেসিডেন্টরা। ফলে স্বাধীনভাবে কাজ করা নবাবদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।
লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি চালু করলে রেসিডেন্সি ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। এই নীতি অনুযায়ী মিত্ররাজ্যে রেসিডেন্ট নিয়োগ বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে হায়দরাবাদ, পেশোয়া এবং সিন্ধিয়ার দরবারে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।
এইসব রেসিডেন্টরা দেশীয় শাসকদের আর্থিক ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কোম্পানিকে তথ্য সরবরাহ করত। প্রতিবেশী শাসক বা বিদেশি শক্তি (বিশেষত ফরাসি) সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যটিকে সরাসরি দখল করা উচিত না কি পরোক্ষ শাসন বজায় রাখা উচিত তা নিয়ে কোম্পানিকে পরামর্শ দিত। বস্তুত রেসিডেন্টদের মাধ্যমেই ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে কোম্পানির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সূত্র ধরেই লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা ভারতের বহু দেশীয় রাজ্য গ্রাস করেন।
ভারতে কোম্পানির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার ছিল রেসিডেন্স ব্যবস্থা। দেশীয় শাসকদের খরচে পালিত এই রেসিডেন্টরাই দেশীয় রাজ্যগ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের বর্ণনা দাও।
বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক রাজ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও বাণিজ্যিক প্রভুত্বের প্রশ্নে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ শুরু হয়।
ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ
(i) প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ: ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং কর্ণাটকের নবাব নিয়োগের প্রশ্নে ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পন্ডিচেরির ফরাসি গভর্নর দুপ্লে আনোয়ার উদ-দিনকে সেন্ট থোম-এর যুদ্ধে পরাজিত করে চাঁদাসাহেবকে নবাব পদে অভিষিক্ত করেন (১৭৪৬ খ্রি.) এবং ইংরেজ ঘাঁটি মাদ্রাজ দখল করেন। ইউরোপে আই-লা-শ্যাপলের সন্ধিতে (১৭৪৮ খ্রি.) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দু বা প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের অবসান ঘটে।
(ii) দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ: ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ ঝা মারা গেলে তার পুত্র নাসির জঙ্ এবং দৌহিত্র মুজাফ্ফর জঙ্-এর মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দু শুরু হয়। কর্ণাটকের সিংহাসন নিয়ে আনোয়ার উদ-দিন ও চাঁদাসাহেবের মধ্যে দ্বন্দু বাধে। ফরাসি গভর্নর দুপ্লে মুজাফ্ফর জঙ্ ও চাঁদাসাহেবকে সমর্থন করেন। তিনি অম্বরের যুদ্ধে (১৭৪১ খ্রি.) আনোয়ার উদ-দিনকে পরাজিত ও নিহত করে চাঁদাসাহেবকে নিষ্কণ্টক করেন। তারপর কুদাপ্পার নবাবের সাহায্যে নাসির জঙ্কে হত্যা করে হায়দরাবাদে মুজাফ্ফর জঙ্কে নিজাম করেন। ফরাসি সেনাপতি বুসি তার অভিভাবক নিযুক্ত হন।
এই অবস্থায় ইংরেজরা কর্ণাটকে চাঁদাসাহেবকে হত্যা করে মৃত আনোয়ার উদ-দিনের পুত্র মহম্মদ আলিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠা করে। হায়দরাবাদে নাসির জঙ্-এর ভাই সালাবৎ জঙ্কে তারা সমর্থন জানায়। শেষে নতুন ফরাসি গভর্নর গডেছু এক সন্ধির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৫৫ খ্রি.)। হায়দরাবাদে ফরাসি প্রাধান্য বজায় থাকে।
(iii) তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ: ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রি.) সূত্র ধরে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাংলার ফরাসি ঘাঁটি চন্দননগর ইংরেজরা দখল করে। ফরাসি সেনাপতি বুসি ও লালি ইংরেজ ঘাঁটি মাদ্রাজ ও সেন্ট ডেভিড দুর্গ দখল করে। ইংরেজরা উত্তর সরকার উপকূল, পন্ডিচেরি দখল করে বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসি দের পরাজিত করে (১৭৬০ খ্রি.)। প্যারিস চুক্তিতে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ভারতেও যুদ্ধের অবসান ঘটে। স্থির হয় ফরাসি ঘাঁটিগুলি কেবল বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
ভারতে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ ফরাসিদের ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।
লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্ত কী ছিল? কোন্ দেশীয় রাজ্য এই নীতি প্রথম গ্রহণ করেছিল? এর গুরুত্ব কী ছিল?
১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি এই নীতির শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য দেশীয় রাজাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্ত
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্তগুলি ছিল-
- এই নীতি গ্রহণকারী রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিপদ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রক্ষা করবে।
- কোম্পানির বিনা অনুমতিতে মিত্রতায় আবদ্ধ রাজ্য অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বা মিত্রতা করতে পারবে না।
- রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য ও একজন ইংরেজ প্রতিনিধি থাকবে।
- ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মিত্রতা নীতি গ্রহণকারী রাজ্যকেই বহন করতে হবে।
- রাজ্য থেকে ইংরেজ বাদে সব ইউরোপীয়দের বিতাড়িত করতে হবে।
মিত্রতা নীতি গ্রহণকারী রাজ্য
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রথম গ্রহণ করেছিল নিজাম শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্য (১৭৯৮ খ্রি.)। তারপর যথাক্রমে অযোধ্যা (১৮০১ খ্রি.), পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও (১৮০২ খ্রি.), ভোঁসলে (১৮০৩ খ্রি.), সিন্ধিয়া (১৮০৩ খ্রি.) প্রমুখ এই নীতি গ্রহণ করেন।
গুরুত্ব: এই নীতি প্রয়োগের ফলে-
- ইংরেজ কোম্পানির শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
- ইংরেজরা ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।
- ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মিত্রতা নীতি গ্রহণকারী রাজ্য বহন করায় ইংরেজদের সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকুচিত হয়।
- এই নীতির শর্ত অমান্যকারী রাজ্যগুলিকে গ্রাস করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পায়।
মূল্যায়ন
এইভাবে বিনা ব্যয়ে এবং বিনা রক্তপাতে ভারতের বিশাল অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।
লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার কীভাবে হয়েছিল?
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে বড়োলাট লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার বলেছেন, লর্ড ওয়েলেসলির রাজত্বকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল।
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য
(i) সুশাসন প্রতিষ্ঠা: লর্ড ওয়েলেসলি মনে করতেন, ইংরেজদের সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা হল শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় রাজারা অত্যাচারী ও নীতিহীন। তাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।
(ii) ভারতে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর বাজার প্রতিষ্ঠা: ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বিক্রির বাজার তৈরি করতে চেয়েছিলেন।
(iii) ফরাসি আধিপত্যের বিনাশ: এ ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে ফরাসি আধিপত্যের সমূলে বিনাশ ঘটানোও ওয়েলেসলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।
ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি
লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যথা-
① যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয়, ② ছলনার মাধ্যমে রাজ্যজয় এবং ③ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে রাজ্যজয়।
যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয়
(i) চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ: লর্ড ওয়েলেসলি যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে মহীশূর সাম্রাজ্য দখল করেন। তিনি মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতায় স্বাক্ষর করতে বললে টিপু সুলতান তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধে টিপু সুলতান পরাজিত ও নিহত হন। মহীশূরে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।
(ii) ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: মারাঠা দলপতি সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ইংরেজ মিত্ররাজ্য হায়দরাবাদ আক্রমণ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেয়। ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলের উপর ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
ছলনার মাধ্যমে রাজ্যজয়
লর্ড ওয়েলেসলি ছলনার আশ্রয় নিয়ে তিনটি রাজ্য দখল করেন। সেগুলি হল- তাঞ্জোর, সুরাট ও কর্ণাটক।
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে রাজ্যজয়
লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতি অনুযায়ী-① কোনো দেশীয় রাজ্য ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হলে সেই রাজ্যের নিরাপত্তার ভার ব্রিটিশরা নেবে, ② ওই রাজ্যটিতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকবেন এবং ③ রাজ্যটির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে হবে। এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি অনেক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করেন। এই রাজ্যগুলি হল- হায়দরাবাদ (১৭৯৮ খ্রি.), অযোধ্যা এবং (১৮০১ খ্রি.), সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের (১৮০২ খ্রি.) রাজ্য প্রভৃতি।
এইভাবে লর্ড ওয়েলেসলি কূটনীতির দ্বারা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর ব্রিটিশ শাসন কায়েম করেছিলেন।
দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি স্বত্ববিলোপ নীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্য দখলের প্রক্রিয়া ও কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতি এবং লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ভূমিকা
সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরাসরি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশীয় শক্তিগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিতে বাধ্য করেন। এই নীতির প্রধান শর্ত হিসেবে বলা হয়-
- অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।
- মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলি কোনো তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে তার রক্ষার দায়িত্ব নেবে কোম্পানি।
- এই মিত্রতা নীতি গ্রহণের পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিজেদের ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে।
প্রয়োগ: দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হায়দরাবাদের নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। এ ছাড়া এই নীতি প্রয়োগ করে মহীশূর রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে কোম্পানি পেশোয়ার সকল অঞ্চল দখল করে নিলে মারাঠা শক্তি এই নীতি মেনে নেয়।
লর্ড ওয়েলেসলি তার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে বহু দেশীয় রাজন্যবর্গকে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোম্পানির অখণ্ড কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এ ছাড়া একজন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।
দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগে স্বত্ববিলোপ নীতির ভূমিকা
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তার তথা দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি ভারতে এসে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতির মূল বক্তব্যগুলি হল-
- ইংরেজ আশ্রিত কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্যের রাজন্যবর্গ দত্তক নিতে পারবেন না এবং উক্ত রাজ্যটি সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে।
- এই নীতির মধ্য দিয়ে বলা হয় যে, ইংরেজদের আশ্রিত কোনো রাজ্য যদি দত্তক নিতে চায় তবে তার আগে সেই রাজ্যকে কোম্পানির অনুমতি নিতে হবে এবং তা না হলে ওই রাজ্যটি সরাসরি কোম্পানির শাসনাধীনে চলে আসবে।
- স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় ষাট ভাগেরও বেশি অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রয়োগ
দেশীয় রাজ্য দখলের উদ্যোগে স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে লর্ড ডালহৌসি সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন।
মূল্যায়ন
লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত এই নীতি দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। ফলস্বরূপ দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে ব্রিটিশ বিরোধিতার সৃষ্টি হয়।
এইভাবে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও স্বত্ববিলোপ নীতি দেশীয় রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলা যেতে পারে।
হায়দর আলির নেতৃত্বে কীভাবে মহীশূর রাজ্যের উত্থান হয়েছিল? হায়দর আলির সময়ে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক কীরকম ছিল?
মহীশূর সাম্রাজ্যে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে হায়দর আলি একজন সাধারণ সৈনিক থেকে মহীশূরের সর্বেসর্বা হন। এইসময় ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হলে তাদের সঙ্গে হায়দার আলি ও তার পুত্র টিপু সুলতানের সংঘর্ষ বাঁধে।
হায়দর আলির নেতৃত্বে মহীশূরের উত্থান
পূর্ব জীবন
১৭২১ খ্রিস্টাব্দে বুদিকোটে হায়দর আলি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ফতে মহম্মদ একজন ভাড়াটে সৈনিক ছিলেন। হায়দর আলি মহীশূরের শাসক নঞ্জরাজের অধীনে এক সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরের শাসক নঞ্জুরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে মহীশূর সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হন।
রাজ্যবিস্তার
সিংহাসনে আরোহণের পর হায়দর আলি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিদনুর, গুটি, সেরা প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে নিজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেন। তার রাজ্যবিস্তারের ফলে ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
হায়দর আলির সময়ে ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক
প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
এমতাবস্থায় হায়দর আলিকে দমন করার জন্য ইংরেজরা মারাঠা ও নিজামকে নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করে। ক্ষুব্ধ হায়দর আলি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। হায়দর আলি ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিতে মাদ্রাজ আক্রমণ করলে ইংরেজরা হায়দারের সঙ্গে মাদ্রাজের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
মাদ্রাজের সন্ধির শর্ত
মাদ্রাজের সন্ধির শর্ত অনুসারে স্থির হয় যে, হায়দর আলি ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে কোনো এক পক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অন্যকে সাহায্য করবে।
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
মূলত দুটি কারণে দ্বিতীয় ইঙ্গ- মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। যথা-
- মারাঠারা ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মহীশূর আক্রমণ করলে মাদ্রাজের সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা মহীশূরকে সাহায্য করেনি।
- ইংরেজরা মহীশূরের বিনা অনুমতিতে মহীশূরের অন্তর্গত ফরাসি উপনিবেশ মাহে আক্রমণ করে। ফলে হায়দর আলি ক্ষুব্ধ হন। হায়দর আলি ইংরেজ আশ্রিত কর্ণাটক আক্রমণ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। কিন্তু এর মধ্যে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কর্কট (ক্যানসার) রোগে আক্রান্ত হয়ে হায়দর আলি মারা যান।
টিপু সুলতানের সময় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ ও মহীশূর রাজ্যের পতন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
টিপু সুলতানের নেতৃত্বে মহীশূরের যুদ্ধ
টিপু সুলতান ছিলেন মহীশূর রাজ্যের একজন অন্যতম শাসক। পিতা হায়দর আলির মৃত্যুর পর তিনি মহীশূর সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। উভয়পক্ষের ইচ্ছানুসারে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মহীশূর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।
ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির শর্ত
ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকৃত অঞ্চল ফেরত দেয়। এই সন্ধির ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে।
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
যুদ্ধের কারণ
টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে যোগসাজশ করেন। অপরদিকে ইংরেজ বড়োলাট কর্নওয়ালিস ইচ্ছাকৃতভাবে মহীশূরের নাম বাদ দিয়ে মিত্ররাজ্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে টিপু ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। দু-বছর বীরবিক্রমে যুদ্ধ করার পর টিপু সুলতান পরাজিত হন এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।
শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্ত
শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্ত অনুসারে-
- টিপুকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও অর্ধেক রাজ্য ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হয়,
- ক্ষতিপূরণের টাকার জামিনস্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজরা আটক রাখে।
চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
কিছুকাল পর টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে আবার ফরাসিদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন। এদিকে বড়োলাট লর্ড ওয়েলেসলি টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে স্বাক্ষর করতে বললে টিপু তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।।
মহীশূরের পতন
এই যুদ্ধে টিপু ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে মহীশূর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।
কীভাবে ইংরেজরা মারাঠা শক্তির পতন ঘটায়?
ভূমিকা
পানিপতের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রি.) মারাঠারা পরাজিত হলেও পেশোয়া মাধব রাও মারাঠা সাম্রাজ্যকে আবার শক্তিশালী করেন। কিন্তু তার মৃত্যু ও পরবর্তী পেশোয়ার হত্যাকাণ্ডের ফলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়। কোম্পানির বোম্বাই কাউন্সিল এই গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়। তিনটি যুদ্ধের ফলে শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ও পেশোয়া পদের অবসান ঘটে।
পেশোয়া
মারাঠি ভাষায় ‘পেশোয়া’ বলতে বোঝায় প্রধানমন্ত্রীকে।
ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক
মারাঠা সাম্রাজ্য এবং কোম্পানির বোম্বাই কাউন্সিল নিকটে অবস্থান করায় মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকটে বোম্বাই কাউন্সিল প্রভাবিত হয়, ফলে তার থেকে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হয়।
প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২ খ্রি.): ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তার ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও তাকে হত্যা করে নিজে পেশোয়া হন। মারাঠা নেতারা তখন নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে। আত্মরক্ষার জন্য রঘুনাথ রাও সলসেট, বেসিন ইংরেজদের দিয়ে সুরাট-এর চুক্তি করেন (১৭৭৫ খ্রি.)। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস শিশু পেশোয়ার সঙ্গে পুরন্দর-এর চুক্তি করেন (১৭৭৬ খ্রি.)। কিন্তু লন্ডনের ডাইরেক্টর সভা সুরাট চুক্তি সমর্থন করলে কোম্পানি রঘুনাথ রাও-এর সমর্থনে সৈন্য পাঠায়। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। শেষে সলবাই-এর সন্ধিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৭৮২ খ্রি.)। শিশু মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া হিসেবে স্বীকৃত হন। রঘুনাথ রাওকে বৃত্তি দেওয়া হয় এবং সলসেট ও বেসিন ইংরেজদের হাতে থাকে।
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-০৫ খ্রি.): মারাঠা নেতা নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হলে মারাঠা সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মারাঠা নেতা সিন্ধিয়া ও হোলকার দুর্বল পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে সরিয়ে নিজেরা পেশোয়া পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বাজিরাও ইংরেজদের সঙ্গে বেসিনের সন্ধি করেন (১৮০২ খ্রি.)। পরে তিনি সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়।
এই যুদ্ধে পরাজিত ভোঁসলে দেওগাঁও সন্ধি দ্বারা (১৮০৩ খ্রি.) কটক ও বালেশ্বর এবং সিন্ধিয়া সুরজি অঞ্জনগাঁও সন্ধি (১৮০৩ খ্রি.) দ্বারা শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ অঞ্চল, উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে জয়পুর, যোধপুর, আহমেদনগর ও ব্রোচ ইংরেজদের ছেড়ে দিয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হন।
তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮ খ্রি.): ইংরেজ অনুগত
গাইকোয়াড়-এর দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যা, অপমানজনক পুনা সন্ধির (১৮১৭ খ্রি.) প্রতিক্রিয়ায় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ইংরেজ রেসিডেন্সি আক্রমণ করলে এই যুদ্ধ শুরু হয়। মারাঠা নেতারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত হয়। ইংরেজরা সমগ্র মহারাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে এবং পেশোয়া নির্বাসিত হন।
মূল্যায়ন: এইভাবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়াতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। মারাঠা শক্তির পতন ঘটে এবং কোম্পানি ভারতে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হয়।
অযোধ্যা ও পাঞ্জাব কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাংলাদেশে এবং পরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করে। অযোধ্যা ও পাঞ্জাব দখল ছিল তার মধ্যে অন্যতম।
অযোধ্যা
১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয় হলে অযোধ্যার নবাব সুজা উদ-দৌলা কারা ও এলাহাবাদ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অযোধ্যার নবাব ভাড়াটিয়া ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে প্রতিবেশী রোহিলাখণ্ড জয় করেন। এইসময় থেকে অযোধ্যায় ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয় এবং একদল ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন থাকে। অযোধ্যার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন অঞ্চল ইংরেজরা দখল করে নেয়। শেষে বড়োলাট লর্ড ডালহৌসি কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা রাজ্য দখল করে নেন।
পঞ্জাব
১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে সুরজি অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি দ্বারা সিন্ধিয়ার কাছ থেকে পাওয়া পূর্ব পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রণজিৎ সিংহ তা স্বীকার করে নেন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঘটে (১৮৪৫-৪৬ খ্রি.)। যুদ্ধে পরাজিত শিখরা লাহোর সন্ধির দ্বারা (১৮৪৫-৪৬ খ্রি.) শতদ্রু নদীর দক্ষিণ অঞ্চল জলন্ধর দোয়াব ব্রিটিশদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শিখ দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট ও পঞ্জাবে ব্রিটিশবাহিনী মোতায়েন থাকে।
এই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের জন্য দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঘটে (১৮৪৯ খ্রি.)। এই যুদ্ধেও শিখরা পরাজিত হলে সমগ্র পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৮৪৯ খ্রি.)।
এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ফলপ্রসূ হয়। উত্তর ভারতের উর্বর দোয়াব সমভূমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং আফগানিস্তান পর্যন্ত ব্রিটিশ আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়।